
২০১৮ সালে শুরু হওয়া এক দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষার পরে, গত কয়েক মাসে বাংলাদেশে রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থায় এমন একটি পর্যায় আসছে যেখানে ‘সংস্কার’ এক কার্যকর রাজনৈতিক দাবিতে রূপ নেয়। ২০২৪ সালের জুলাই‐আগস্টে শিক্ষার্থী, শ্রমিক ও জনতার আন্দোলন, আন্দোলনের ওপর রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের ঘন জোরাজুরি শেষে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। সেই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস অনুসন্ধান কমিটি ও সংস্কার‐কমিশন গঠন করেন: নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতিবোধ ও তথ্য অধিকার ইত্যাদির মতো বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে।
ঐকমত্য কমিশন, যা এমন একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিভিন্ন পার্টি, গোষ্ঠী ও অভ্যাগত নাগরিক অংশগ্রহণ করছিল, তারা “জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫” নামে একটি খসড়া তৈরি করেছে। এই সনদে অন্তত ৮৪টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, এবং দ্বিতীয় দফার আলোচনায় আরও ১১টি মৌলিক সংস্কার‐প্রস্তাব তৈরি হয়েছে যেখানে পার্টিগুলো ভিন্নমতের নোটসহ একমত হয়েছে।
এই সংস্কার‐প্রস্তাবগুলোর মধ্যে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা সাধারণভাবে দৃষ্টিগোচর: স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ন্যায্যতা, রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক স্বচ্ছতা, নির্বাচন কমিশনের গঠন, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি, দ্রব্যমূল্য‐নিয়ন্ত্রণ নয়, তবুও জনপরিসেবায় নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর নিরপেক্ষতা, দুর্নীতি দমন ব্যবস্থায় আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী পদক্ষেপ, তথ্য অধিকার আইন সংশোধন, নাগরিক মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ ইত্যাদি।
একই সঙ্গে, “জুলাই সনদে” কিছু বিষয় আছে যেখানে পার্টিগুলোর মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। যেমন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও নির্বাচন পদ্ধতি, প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের মেয়াদ, বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ, জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান, এবং জনস্বার্থে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদিতে পার্টিগুলো এক‐স্থান নাও আসতে পারছে।
এই প্রেক্ষাপটে, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস বুধবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে বলেছিলেন, “ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচনের কোনো বিকল্প আমাদের হাতে নেই।” অর্থাৎ, সনদ‐সংস্কার ও নির্বাচন—এই দুইটিই সরকারের মূল ম্যান্ডেট, এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে মৌলিক সংস্কারগুলো শেষ করা একান্ত জরুরি।
তবে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিশ্লেষণ বলছে, শুধু খসড়ার ওপর একমত হওয়া যথেষ্ট নয়; সনদ বাস্তবায়নের কাঠামো, আইনগত ও সংবিধানগত বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। ঐকমত্য কমিশন নিজেই বলেছে যে, তাদের ক্ষমতা “শুধু সুপারিশ” করার—কোনো কিছু জোর করে বাস্তবায়ন করতে পারবে না। অর্থাৎ, সরকার ও আইন-নিয়ন্ত্রক সংস্থার রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আইনগত প্রস্তুতি অপরিহার্য।
বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা ও কার্যকর অগ্রগতি নির্ধারণে, রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ ও স্বাক্ষর প্রক্রিয়া চলছে। উদাহরণস্বরূপ, “জুলাই জাতীয় সনদ হত্যের চূড়ান্ত ভাষ্য” রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে, এবং দলগুলোর পক্ষ থেকে দু’জন প্রতিনিধির নাম জানাতে বলা হয়েছে সাক্ষর করার জন্য।
এই রূপান্তরের ধাপগুলো দেশের প্রেক্ষাপটে নতুন ধাঁচের গণতন্ত্র বিল্ডিংয়ের ইঙ্গিত বহন করছে—যেখানে শুধু নির্বাচনের দিন নয়, নির্বাচন প্রক্রিয়া, স্বাধীনতা ও সংবিধান, বিচার বিভাগ, প্রশাসন ও দুর্নীতি‐নিয়ন্ত্রণ—সবকিছু একটি জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্মিত হবে। তবে বিপুল কাজ রয়েছে: রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও পার্থক্য মেটানো, সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়া চালানো, স্বতন্ত্র তদন্ত ব্যবস্থা গঠন, আদালত ও প্রশাসনকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা ইত্যাদি।
বর্তমানে সময়ের দাবী হল যে এই সংস্কারগুলো শুধু কথার স্তরে থেমে যাবে না; নির্বাচনের আগে এই গুছানো সংস্কারগুলোর আইনগত বাধ্যবাধকতা, স্বচ্ছতা ও সময়সীমা নির্ধারণ করে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ফেব্রুয়ারি আসছে, এবং নির্বাচনকে একটি ‘ফাউন্ডেশনাল ইলেকশন’ বলা হচ্ছে—যে নির্বাচন শুধু আসন্ন নির্বাচন নয়, ভবিষ্যতের বাংলাদেশের রূপরেখা নির্ধারণ করবে। জনতা অপেক্ষায় আছে: শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব পরিবর্তন।



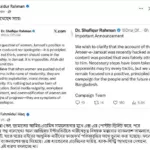


আপনার মতামত জানানঃ