 ঢাকা বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র। এই শহর শুধু দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক রাজধানী নয়, অর্থনীতিরও মূল চালিকাশক্তি। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সেবা খাত—সবকিছুতেই ঢাকার প্রভাব এত বেশি যে, পুরো দেশের অর্থনৈতিক চিত্র অনেকাংশে এই একটি শহরের ওপর নির্ভরশীল। সদ্য প্রকাশিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) অর্থনৈতিক অবস্থান সূচক বা ইপিআই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ঢাকার মানুষের মাথাপিছু আয় এখন ৫ হাজার ১৬৩ মার্কিন ডলার। দেশের গড় আয় যেখানে ২ হাজার ৮২০ ডলার, সেখানে ঢাকার আয় প্রায় দ্বিগুণ। এটি শুধু পরিসংখ্যান নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে।
ঢাকা বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র। এই শহর শুধু দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক রাজধানী নয়, অর্থনীতিরও মূল চালিকাশক্তি। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সেবা খাত—সবকিছুতেই ঢাকার প্রভাব এত বেশি যে, পুরো দেশের অর্থনৈতিক চিত্র অনেকাংশে এই একটি শহরের ওপর নির্ভরশীল। সদ্য প্রকাশিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) অর্থনৈতিক অবস্থান সূচক বা ইপিআই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ঢাকার মানুষের মাথাপিছু আয় এখন ৫ হাজার ১৬৩ মার্কিন ডলার। দেশের গড় আয় যেখানে ২ হাজার ৮২০ ডলার, সেখানে ঢাকার আয় প্রায় দ্বিগুণ। এটি শুধু পরিসংখ্যান নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে।
এই গবেষণার পেছনে রয়েছে বেশ বিস্তারিত বিশ্লেষণ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১১ সালের জেলা ভিত্তিক জিডিপির তথ্যকে ভিত্তি ধরে, বিনিয়োগ, ভোগ, ব্যয়, আমদানি-রফতানি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভূমির আয়তনসহ নানা উপাদান মিলিয়ে ঢাকা জেলার মাথাপিছু আয়ের হিসাব অনুমান করেছে ডিসিসিআই। গবেষণাটি পরিচালিত হয় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে, যেখানে ৬৫৪ জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়—তাদের মধ্যে ৩৬৫ জন ছিলেন উৎপাদন খাত থেকে এবং ২৮৯ জন সেবা খাত থেকে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকার অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি—৫৬ শতাংশ। সেবা খাতের অবদান ৪৪ শতাংশ। উৎপাদন খাতের মধ্যে খাদ্যপণ্য ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ, টেক্সটাইল ৯ দশমিক ৩ শতাংশ, রাবার ও প্লাস্টিক পণ্য ৭ দশমিক ৭ শতাংশ, মৌলিক ধাতু ৩ দশমিক ৩ শতাংশ, ওষুধ ও রাসায়নিক ২ দশমিক ৭ শতাংশ, চামড়া ২ দশমিক ৭ শতাংশ এবং অ-ধাতব খনিজ ২ দশমিক ২ শতাংশ অবদান রাখে। অন্যদিকে সেবা খাতে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্যের অংশীদারিত্ব সবচেয়ে বেশি—৬০ দশমিক ২ শতাংশ। এরপর রয়েছে রিয়েল এস্টেট ২০ দশমিক ৮ শতাংশ এবং পরিবহন খাত ১৯ শতাংশ।
ডিসিসিআইয়ের এই গবেষণা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নতুনভাবে দেখার একটি জানালা খুলে দিয়েছে। সংস্থাটির সভাপতি তাসকীন আহমেদ জানিয়েছেন, দেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ নিয়ে অনেক সূচক থাকলেও সেগুলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আসল পরিবর্তন কতটা ধরতে পারে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তাই প্রথমবারের মতো দেশীয় বাস্তবতার ভিত্তিতে ‘অর্থনৈতিক অবস্থান সূচক’ প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুরুতে এটি ঢাকাকেন্দ্রিক হলেও, ধীরে ধীরে সারা দেশে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।
তাসকীন আহমেদ বলেন, এই সূচক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকাশ করা হবে এবং এতে শিল্পখাতের উৎপাদন, বিক্রি, রফতানি, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ প্রবণতা এবং ব্যবসায়িক আস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। বর্তমানে সূচকে তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, আবাসন, পরিবহন ও ব্যাংক খাতের তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআইয়ের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ড. একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী। তিনি জানান, এই গবেষণার লক্ষ্য ছিল ঢাকার অর্থনীতির প্রকৃত শক্তি ও সীমাবদ্ধতা নিরূপণ করা। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয় যে, ঢাকার অর্থনীতির মেরুদণ্ড এখনো শিল্প উৎপাদনেই নির্ভরশীল। তবে সেবা খাতও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে খুচরা বাণিজ্য ও রিয়েল এস্টেট খাত শহরের মানুষের জীবনধারা ও কর্মসংস্থানের সাথে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে।
গবেষণার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঢাকার সাবেক চেম্বার সভাপতি আবুল কাসেম খান বলেন, তৈরি পোশাক খাত অনেক ধরনের প্রণোদনা ও সুবিধা পাচ্ছে, তাই অন্য খাতের সঙ্গে এর সরাসরি তুলনা ঠিক ন্যায্য নয়। তবে তিনি সতর্ক করেন, তথ্য বিশ্লেষণ শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না; বরং প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ জরুরি। তাঁর মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সংস্কারের গতি ধীর, এবং সরকার প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত গতিতে এগোচ্ছে না।
এসএসজিপির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ নেসার আহমেদ উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) মর্যাদার অনেক সুবিধা ব্যবহার করে ফেলেছে। এখন এলডিসি উত্তরণের পর নতুন বাস্তবতায় প্রতিযোগিতা আরও কঠিন হবে। তাই এখনই নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি নিতে হবে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক ড. সৈয়দ মুনতাসির মামুন বলেন, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনই টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। সরকারি ও বেসরকারি খাত যদি যৌথভাবে ব্যবসায়িক স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বাড়ায়, তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরও মজবুত হবে। তিনি পরামর্শ দেন, ভবিষ্যতে এই গবেষণায় কৃষি খাতকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, কারণ কৃষি এখনো দেশের একটি মৌলিক অর্থনৈতিক ভিত্তি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক নওশাদ মোস্তফা বলেন, এসএমই খাতে ঋণপ্রাপ্তি সহজ করতে ইতোমধ্যেই নীতিমালা শিথিল করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে উদ্যোক্তারা কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছেন, সেই তথ্য আরও গভীরভাবে জানা দরকার। এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারবে।
অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা র্যাপিডের গবেষণা পরিচালক ড. মো. দীন ইসলাম বলেন, অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থা জানতে গবেষণার পদ্ধতিতে আরও পরিমার্জন প্রয়োজন। একইসঙ্গে বিএফটিআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. সাইফ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার তথ্য একত্রিত করে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ তৈরি করা গেলে ফলাফল আরও নির্ভরযোগ্য হবে।
ঢাকার মানুষের মাথাপিছু আয় দেশের গড় আয়ের প্রায় দ্বিগুণ হওয়াটা যেমন একটি সাফল্যের প্রতীক, তেমনি এটি আঞ্চলিক বৈষম্যেরও ইঙ্গিত দেয়। ঢাকার বাইরে শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে ধীর, যার ফলে রাজধানীতে সম্পদ ও সুযোগের ঘনত্ব বেড়ে চলেছে। একদিকে উন্নত অবকাঠামো, আর্থিক সেবা, আন্তর্জাতিক সংযোগ ও প্রযুক্তিগত সুযোগ ঢাকাকে এগিয়ে নিচ্ছে; অন্যদিকে, এই কেন্দ্রীকরণ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিনিয়োগে অনীহা তৈরি করছে।
এই প্রেক্ষাপটে ইপিআই সূচক শুধু একটি গবেষণা নয়, বরং এটি হতে পারে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের একটি দিকনির্দেশক। ত্রৈমাসিকভাবে প্রকাশিত হলে এটি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াবে, নীতি নির্ধারকদের সঠিক তথ্য দেবে এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা দেবে।
সবশেষে বলা যায়, ঢাকার অর্থনীতির এই উল্লম্ফন বাংলাদেশের জন্য একদিকে গর্বের বিষয়, অন্যদিকে একটি সতর্কবার্তা। কারণ, টেকসই উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন প্রবৃদ্ধি শুধু একটি শহর বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। ঢাকার মাথাপিছু আয় ৫১৬৩ ডলার—এই সংখ্যা তাই একদিকে অর্জনের প্রতীক, অন্যদিকে সমতার চ্যালেঞ্জের প্রতিফলনও। এখন সময় এসেছে এই সাফল্যের ছায়া ছড়িয়ে দেওয়ার, যাতে দেশের প্রত্যেক অঞ্চল, প্রত্যেক নাগরিক উন্নয়নের সুফল পেতে পারে সমানভাবে।

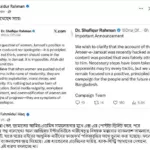




আপনার মতামত জানানঃ