 ভারতের ঝাড়খণ্ডের গড্ডায় নির্মিত আদানি পাওয়ারের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি এখন বাংলাদেশের জন্য এক অস্বস্তির নাম। এক সময় যেই প্রকল্পকে দুই দেশের বন্ধুত্বের প্রতীক বলা হয়েছিল, আজ সেটি হয়ে উঠেছে জটিলতা, অর্থনৈতিক চাপ ও আইনি ঝামেলার কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও আদানি গ্রুপের মধ্যে কয়লার দাম, বিদ্যুতের মূল্য এবং বকেয়া পরিশোধ নিয়ে বিরোধ এখন এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে, যেখানে আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে দুই পক্ষই।
ভারতের ঝাড়খণ্ডের গড্ডায় নির্মিত আদানি পাওয়ারের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি এখন বাংলাদেশের জন্য এক অস্বস্তির নাম। এক সময় যেই প্রকল্পকে দুই দেশের বন্ধুত্বের প্রতীক বলা হয়েছিল, আজ সেটি হয়ে উঠেছে জটিলতা, অর্থনৈতিক চাপ ও আইনি ঝামেলার কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও আদানি গ্রুপের মধ্যে কয়লার দাম, বিদ্যুতের মূল্য এবং বকেয়া পরিশোধ নিয়ে বিরোধ এখন এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে, যেখানে আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে দুই পক্ষই।
আদানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয় ২০২৩ সালের শুরুর দিকে। ২৫ বছরের জন্য স্বাক্ষরিত এই চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ নির্দিষ্ট দামে বিদ্যুৎ নেবে এবং আদানি সরবরাহ করবে কয়লাভিত্তিক উৎপাদন থেকে। কিন্তু শুরু থেকেই দেখা দেয় দাম নিয়ে মতবিরোধ। পিডিবির হিসাব বলছে, আদানির কেন্দ্রের কয়লার দাম প্রতি টনে গড়ে ১৫ থেকে ২০ ডলার বেশি পড়ে, যা বাংলাদেশের অন্য কয়লাভিত্তিক কেন্দ্রগুলোর তুলনায় অস্বাভাবিক। যেমন, পায়রা বা বাঁশখালী বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যেখানে প্রতি টন কয়লার দাম ৬৫ থেকে ৭০ ডলারের মধ্যে, সেখানে আদানি ৮০ ডলার পর্যন্ত দাবি করছে।
এই বাড়তি দামের প্রভাব পড়েছে সরাসরি বিদ্যুতের দামে। পিডিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আদানির কেন্দ্র থেকে কেনা প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের খরচ হয়েছে ১৪ টাকা ৮৭ পয়সা, যেখানে ভারতের অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আমদানির গড় খরচ ছিল ৮ টাকা ৪০ পয়সা। এত বিশাল পার্থক্য কেবল অর্থনৈতিক চাপই তৈরি করেনি, বরং প্রশ্ন তুলেছে চুক্তির ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিয়েও।
এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে। সেই সময় আদানির পাওয়ার প্রজেক্টকে ‘দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা’র বড় উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব চিত্র উল্টো। চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই দাম ও বকেয়া নিয়ে বিরোধ বাড়তে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বকেয়ার অঙ্ক দাঁড়ায় প্রায় ৭০ কোটি ডলার, অর্থাৎ ৮ হাজার ৬০০ কোটি টাকারও বেশি। যদিও পিডিবি বলছে, গত জুন পর্যন্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে, তবে কয়লার বাড়তি দাম ধরে আদানির দাবি করা বকেয়া এখনো রয়েছে প্রায় ২০ কোটি ডলার বা আড়াই হাজার কোটি টাকার মতো।
এই জটিলতার মাঝেই আদানি গ্রুপ ২৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টাকে চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে চেয়ারম্যান গৌতম আদানি অভিযোগ করেছেন, জুন মাসে পিডিবির কর্মকর্তারা তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সব বকেয়া ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে, কিন্তু তা হয়নি। এমনকি আদানি পাওয়ার ইতিমধ্যে ৩৩৬ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত পরিশোধ পেয়েছে বলেও উল্লেখ আছে।
বিষয়টিকে আরও জটিল করেছে ভারতের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ। ভারতের সরকার গড্ডা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ দেশটির জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করার অনুমোদন দিয়েছে। অর্থাৎ, এখন থেকে আদানি শুধু বাংলাদেশ নয়, চাইলে ভারতের বাজারেও বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারবে। অথচ এই কেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছিল মূলত বাংলাদেশের জন্য—২৫ বছরের বিদ্যুৎ রপ্তানি চুক্তি সাপেক্ষে।
এ অনুমোদন মেলে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর ধারা ১৬৪-এর অধীনে। ভারতের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় ২৯ সেপ্টেম্বর এই নির্দেশনা জারি করেছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আদানির সামনে নতুন বাজার উন্মুক্ত হয়েছে, আর বাংলাদেশে তার প্রভাব পড়েছে অনিশ্চয়তা হিসেবে। কারণ, চুক্তি অনুসারে আদানির উৎপাদন ক্ষমতার একটি বড় অংশ বাংলাদেশের জন্য সংরক্ষিত থাকার কথা।
বাংলাদেশ এখন আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পিডিবি জানিয়েছে, তারা এক মাস সময় চেয়েছে আইনি পরামর্শক নিয়োগের জন্য। ইতিমধ্যে আদানি গ্রুপ নিয়োগ দিয়েছে সিঙ্গাপুরভিত্তিক দুটি আইনি প্রতিষ্ঠান—ডাক্সটন হিল চেম্বারস ও দি আরবিট্রেশন চেম্বারস। এসবই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বিরোধ আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতে গড়াতে যাচ্ছে।
পিডিবি চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম বলেছেন, “আমরা আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান চাই। আদানি যদি প্রমাণ করতে পারে যে কয়লার দাম সত্যিই বেশি, আমরা তা পরিশোধ করব। কিন্তু একই সূচকে আমরা অন্য জায়গা থেকেও কয়লা কিনছি, সেখানে এমন দাম নেই।” তাঁর বক্তব্যে বোঝা যায়, বাংলাদেশ পক্ষ সরাসরি সংঘাতে যেতে চায় না, কিন্তু প্রস্তুতি নিচ্ছে যেন প্রয়োজনে আদালতে নিজেদের অবস্থান শক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়।
জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. ম. তামিম এই চুক্তিকে শুরু থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ বলেছেন। তাঁর মতে, “এটি আন্তর্জাতিক দক্ষ আইনজীবীর কাছে নেওয়া দরকার। চুক্তির শর্তগুলো পর্যালোচনা করে দেখতে হবে, কয়লার মূল্য নির্ধারণে আদানিকে অস্বাভাবিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে কি না। পৃথিবীর অন্য কয়লাভিত্তিক কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে এ চুক্তির অস্বচ্ছতা স্পষ্ট।” তিনি আরও বলেন, “যেহেতু এটি ২৫ বছরের দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি, এখনই উদ্যোগ না নিলে ভবিষ্যতে বড় আর্থিক ঝুঁকিতে পড়বে বাংলাদেশ।”
আদানির চুক্তি পর্যালোচনায় অন্তর্বর্তী সরকারের একটি কমিটি কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে তারা জানিয়েছে, চুক্তিটি ‘অসম’। এতে আদানির পক্ষে অনেক সুবিধা রাখা হয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ মূল্যের নির্ধারণে কয়লার দামকে প্রধান উপাদান ধরা হলেও সেখানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দর কষাকষির সুযোগ রাখা হয়নি। ফলে আদানি একতরফাভাবে দাম বাড়ানোর পথ পেয়ে গেছে।
বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের নীতিনির্ধারকরা এখন বিব্রত অবস্থায়। একদিকে আদানির চাপ, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি ও ঋণের বোঝা—সব মিলিয়ে বিদ্যুৎ খাতে সংকট দিন দিন গভীর হচ্ছে। দেশীয় কেন্দ্রগুলোতেও উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে, কারণ ডলারের দাম বৃদ্ধি ও আমদানিনির্ভর জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা। এই অবস্থায় বিদেশি চুক্তির উচ্চমূল্য বাংলাদেশে বিদ্যুতের ট্যারিফ বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা ভোক্তার ঘাড়েই পড়ছে।
আদানির প্রকল্পটি একসময় রাজনৈতিক সাফল্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। শেখ হাসিনার সরকার দাবি করেছিল, এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সেই ‘উন্নয়ন প্রকল্প’ পরিণত হয়েছে দায়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল বিদ্যুৎ নয়, বরং কয়লা বিক্রির মাধ্যমে বাণিজ্যিক লাভ। বাংলাদেশের পক্ষে কয়লার মূল্য নির্ধারণের শর্ত এতটাই দুর্বল যে, বাস্তবে আদানির মুনাফা অনেক বেশি এবং ঝুঁকির ভার পুরোপুরি বাংলাদেশের ঘাড়ে এসে পড়েছে।
এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে—চুক্তি পর্যালোচনার পর কী করা উচিত? বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন, চুক্তি সম্পূর্ণ বাতিল করা কঠিন, কারণ এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। কিন্তু শর্ত সংশোধনের সুযোগ আছে। আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও দরকার, যাতে ভারত সরকার মধ্যস্থতা করে ন্যায্য সমাধানে আসতে পারে।
অর্থনীতিবিদদের মতে, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে যে সংকট এখন দেখা দিচ্ছে, তা শুধু আদানি কেন্দ্রের কারণ নয়, বরং অদূরদর্শী পরিকল্পনার ফল। বিদেশি বিনিয়োগের নামে অনেক প্রকল্প এমনভাবে গঠিত হয়েছে যেখানে রাষ্ট্রের লাভ কম, দায় বেশি। আদানি প্রকল্প সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। এখন যদি দ্রুত সমাধান না আসে, তাহলে এর বোঝা পড়বে দেশের অর্থনীতিতে, বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বিদ্যুৎ ভর্তুকির ওপর।
আদানির সঙ্গে বাংলাদেশের এই বিরোধ তাই শুধু একটি বাণিজ্যিক বা আইনি ইস্যু নয়, বরং এটি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক নীতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরছে। একদিকে দেশের জনগণ বাড়তি দামে বিদ্যুৎ কিনছে, অন্যদিকে একটি বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে খেলছে।
বাংলাদেশ এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—সে কি আগের মতো অস্বচ্ছ চুক্তিতে আটকে থাকবে, নাকি ভবিষ্যতের জন্য স্বচ্ছ, ন্যায্য ও কৌশলগত জ্বালানি নীতির পথে এগোবে। আদানির বিদ্যুৎ কেন্দ্র তাই শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের নীতিনির্ধারণের পরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।


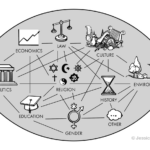



আপনার মতামত জানানঃ