
ভারতের নারী সুরক্ষা সূচক (NARI) ২০২৫-এর প্রতিবেদন দেশের নারীর নিরাপত্তার বাস্তব চিত্রকে নতুনভাবে সামনে এনেছে। ৩১টি শহরে ১২,৭৭০ জন নারীকে নিয়ে করা এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা, নিরাপত্তা ব্যবস্থার শক্তি ও দুর্বলতা, এবং নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রতিবেদনটি শুধু নারীর শারীরিক নিরাপত্তাই নয়, বরং তাদের মানসিক, আর্থিক এবং ডিজিটাল সুরক্ষাকেও আলোচনায় এনেছে। এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নারীর নিরাপত্তা কোনো একক মাত্রার বিষয় নয়; বরং এটি নারী জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে।
কোহিমা, বিশাখাপত্তনম, ভুবনেশ্বর, আইজল, গ্যাংটক, ইটানগর এবং মুম্বাই ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ শহর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অন্যদিকে, পাটনা, জয়পুর, ফরিদাবাদ, দিল্লি, কলকাতা, শ্রীনগর এবং রাঁচি তালিকার সর্বনিম্নে রয়েছে। এই বিভাজন কেবল ভৌগোলিক পার্থক্যের কারণে নয়, বরং প্রতিটি শহরের সামাজিক কাঠামো, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, নাগরিক সচেতনতা ও লিঙ্গসমতার অবস্থার প্রতিফলন।
শীর্ষস্থানীয় শহরগুলোকে নিরাপদ হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে শক্তিশালী পুলিশি ব্যবস্থা, নাগরিকদের লিঙ্গবিষয়ক সচেতনতা, নারী-বন্ধব পরিকাঠামো এবং সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ। কোহিমার নারীরা মনে করেন, স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি সম্প্রদায়ের দায়বদ্ধতা নারীদের নিরাপদ চলাফেরায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অপরদিকে, পাটনা বা জয়পুরের নারীরা তুলে ধরেছেন দুর্বল সরকারি ব্যবস্থা, দায়িত্ববোধের অভাব এবং পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে তারা ভীত ও অসহায় বোধ করেন।
প্রতিবেদনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো সময়ভিত্তিক নিরাপত্তার পার্থক্য। দিনের বেলায় নারীরা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ বোধ করেন, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৮৬ শতাংশ শিক্ষার্থী মেয়েরা দিনের বেলা ক্যাম্পাসে নিরাপদ মনে করেন। কিন্তু রাত নামতেই এই নিরাপত্তা ধারণা বদলে যায়। স্কুল-কলেজ হোস্টেলের বাইরে, গণপরিবহন কিংবা বিনোদনমূলক স্থানে নিরাপত্তাহীনতার অভিজ্ঞতা প্রবল হয়ে ওঠে। এর ফলে নারীরা তাদের চলাফেরা সীমিত করে আনতে বাধ্য হচ্ছেন, যা শিক্ষা ও কর্মজীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলছে।
প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি ও অপমানের ঘটনাও উদ্বেগজনক। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ৭ শতাংশ স্বীকার করেছেন যে, ২০২৪ সালে তারা রাস্তায় বা গণস্থানে যৌন হেনস্তার শিকার হয়েছেন। বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২৪ বছরের নিচে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা দ্বিগুণ। ঘটনাস্থল হিসেবে বেশি উল্লেখ এসেছে পাড়া-মহল্লা (৩৮ শতাংশ) এবং বাস-ট্রেন (২৯ শতাংশ)। যদিও তিনজনের মধ্যে একজন মাত্র পুলিশে অভিযোগ করেছেন। এর অর্থ হলো অধিকাংশ নারী নীরব থেকে যান, যার ফলে এই ধরনের অপরাধের বড় অংশ ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হয় না। এই নীরবতা আসলে আইনের প্রতি আস্থার ঘাটতি এবং সামাজিক চাপে লুকিয়ে থাকার প্রবণতার প্রতিফলন।
এই বাস্তবতায় ন্যাশনাল উইমেন্স কমিশনের (এনসিডব্লিউ) চেয়ারপারসন বিজয়া রাহাতকর মন্তব্য করেছেন, নারীর নিরাপত্তাকে শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন হিসেবে দেখা উচিত নয়। এটি নারী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে—তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ এবং চলাফেরার স্বাধীনতা সবকিছুর সঙ্গেই নিরাপত্তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিনি চারটি মাত্রাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন—শারীরিক, মানসিক, আর্থিক এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা। অর্থাৎ, নারীকে শুধু রাস্তায় অপরাধ থেকে রক্ষা করলেই চলবে না; সাইবার অপরাধ, আর্থিক বৈষম্য এবং মানসিক হয়রানি থেকেও সুরক্ষা দিতে হবে।
নারী সুরক্ষার এই বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আসলে একটি উন্নত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারতের জন্য অপরিহার্য। নারীরা যদি নিরাপদ না হন, তবে তারা তাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। শিক্ষা থেকে শুরু করে কর্মজীবন পর্যন্ত, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের পদক্ষেপ আটকে যাবে। একটি দেশের উন্নয়ন তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তার নারীরা সমানভাবে সুযোগ পান এবং নিরাপদে এগিয়ে যেতে পারেন।
প্রতিবেদনটি আরও এক বাস্তবতা সামনে এনেছে—নারীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ নিরাপদ বোধ করেন, কিন্তু বাকিরা নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলেছেন। এর অর্থ হলো এখনও একটি বড় অংশের নারীর জীবনে ভয় ও অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। এই নিরাপত্তাহীনতার কারণ শুধুই অপরাধ নয়, বরং পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব, সামাজিক কুসংস্কার এবং প্রশাসনিক অদক্ষতা। নারীকে ‘দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক’ হিসেবে দেখার মানসিকতা এখনও সমাজের গভীরে প্রোথিত।
এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে এই চিত্র পাল্টানো সম্ভব? প্রথমত, নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অপরিহার্য। ছোটবেলা থেকেই ছেলে-মেয়েদের সমানভাবে মূল্যবোধ শেখানো দরকার। দ্বিতীয়ত, শক্তিশালী আইন এবং তার কার্যকর প্রয়োগ জরুরি। অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে না পারলে নারীরা আস্থাহীন হয়ে পড়বেন। তৃতীয়ত, নারীবান্ধব পরিকাঠামো যেমন নিরাপদ গণপরিবহন, আলোকিত রাস্তা, সিসিটিভি ব্যবস্থা এবং জরুরি হেল্পলাইন আরও কার্যকর করতে হবে। পাশাপাশি, সাইবার অপরাধ মোকাবেলায় আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবল নিয়োগেরও বিকল্প নেই।
সর্বোপরি, নারীর নিরাপত্তা কোনো ‘নারী বিষয়ক’ সমস্যা নয়, বরং এটি গোটা সমাজের উন্নয়নের পূর্বশর্ত। একটি শহর তখনই সত্যিকারের উন্নত বলা যাবে, যখন সেখানকার নারী রাত-বিরাতেও নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবেন। নারীর নিরাপত্তা মানে কেবল অপরাধ থেকে রক্ষা নয়, বরং স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা।
এই রিপোর্ট আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, কোথায় আমরা সফল হয়েছি, আর কোথায় ভয়াবহভাবে পিছিয়ে রয়েছি। নিরাপদ শহরের তালিকায় কোহিমা, গ্যাংটক কিংবা আইজলের মতো শহর উঠে আসা আমাদের শেখায় যে নিরাপত্তা কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর নয়; এটি মূলত সামাজিক মানসিকতা ও প্রশাসনিক কার্যকারিতার ফল। অন্যদিকে, পাটনা বা দিল্লির মতো শহরের নিম্ন স্থান প্রমাণ করে যে কেবল অবকাঠামো উন্নয়ন যথেষ্ট নয়, মনোভাবের পরিবর্তন জরুরি।
একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে নারীর নিরাপত্তা নিয়ে এত অনিশ্চয়তা ভারতের জন্য লজ্জাজনক। তবে ইতিবাচক দিক হলো, এই ধরনের জাতীয় প্রতিবেদনগুলো বিষয়টিকে জনসমক্ষে আনে, বিতর্ক তৈরি করে এবং নীতিনির্ধারকদের চাপের মুখে ফেলে। ভারতের উন্নত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এটাই যে, সে তার নারীদের কতটা নিরাপদ, সম্মানজনক এবং স্বাধীন জীবন দিতে পারছে।

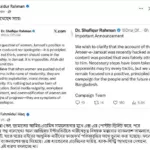




আপনার মতামত জানানঃ