
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের এবং তার স্ত্রী শেরীফা কাদেরের বিদেশ গমনে আদালতের নিষেধাজ্ঞা সাম্প্রতিক সময়ের রাজনীতিতে বড় আলোচনার জন্ম দিয়েছে। দুদক জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অনুসন্ধান চলছে, এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে তারা দেশ ত্যাগ করে সম্পদ হস্তান্তর করতে পারেন। এই প্রেক্ষাপটে আদালতের সিদ্ধান্ত মূলত রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষার অংশ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। তবে এর পেছনে রাজনৈতিক প্রভাবও অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের রাজনীতি বরাবরই বহুমাত্রিক, এবং এখানে দুর্নীতি, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ক্ষমতার লড়াই ও রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়।
বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জাতীয় পার্টির অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দ্বি-মেরু রাজনীতির মধ্যে জাপা প্রায়শই ক্ষমতাসীনদের সহযোগী কিংবা বিকল্প শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু দলের নেতৃত্ব নিয়ে অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন বহুবার সামনে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে জিএম কাদেরের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র একটি আইনি সিদ্ধান্ত নয়, বরং এর মাধ্যমে রাজনৈতিক মেসেজও দেওয়া হচ্ছে। দলকে চাপের মধ্যে রাখার পাশাপাশি এটি দেখায় যে শাসকশক্তি চাইলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।
শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়টিও এই বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ। ছাত্ররাজনীতি বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে—স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে গণআন্দোলন পর্যন্ত। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্রসংগঠনগুলো অনেকাংশেই মূল দলের স্বার্থ রক্ষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যকার সংঘর্ষ এখন আর মতাদর্শগত নয়, বরং ক্ষমতা, প্রভাব ও সুবিধা বণ্টনকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। যখন বড় দলগুলো নিজেদের মধ্যে বা সহযোগী দলগুলোর সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ায়, তার প্রতিফলন বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাম্পাসেও দেখা দেয়। জাতীয় পার্টির নেতাদের আইনি ও রাজনৈতিক চাপ শিক্ষার্থীদের মধ্যকার বিভাজনকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে, কারণ দলীয় আনুগত্যের প্রশ্নে ছাত্রসংগঠনগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়।
এই ধরনের সংঘর্ষের কারণ অনেকগুলো। প্রথমত, বড় রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যখন কেন্দ্রীয় নেতারা নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে বা প্রতিপক্ষকে দুর্বল করতে লড়াই করেন, তখন তার প্রতিচ্ছবি ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব। অনেক সময় দেখা যায়, নির্দিষ্ট একটি দলকে প্রভাবশালী রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নীরব থাকে বা একপক্ষকে সুবিধা দেয়। তৃতীয়ত, আর্থিক স্বার্থ। ছাত্রসংগঠনগুলোর একটি বড় অংশ বিভিন্ন আর্থিক সুযোগ-সুবিধার নিয়ন্ত্রণে যুক্ত থাকে—হোক তা হল দখল, টেন্ডার ব্যবসা, বা নিয়োগ বাণিজ্য। এই স্বার্থসংশ্লিষ্টতা সংঘর্ষকে আরও সহিংস করে তোলে।
এই সংঘর্ষের ফলাফল বহুমাত্রিক। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় শিক্ষা পরিবেশের। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হয়, শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং একাডেমিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব শিক্ষার্থীদের মানসিকতা ও সামাজিক বিকাশেও পড়ে। তারা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি শেখার পরিবর্তে হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেখে। এর ফলে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দুর্নীতিগ্রস্ত, সহিংসতাপ্রবণ এবং অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।
জাতীয় পার্টির বর্তমান সঙ্কট ও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের মধ্যে একটি মিল পাওয়া যায়—দুটোই রাজনীতির অস্বচ্ছতা ও অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফল। একদিকে আইনের শাসনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে জনগণের আস্থা কমে যায়, অন্যদিকে ছাত্ররাজনীতি যখন গণতন্ত্রের পরিবর্তে ক্ষমতার দখল নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন তা শিক্ষা ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এর থেকে উত্তরণের পথ কোথায়? প্রথমত, রাজনীতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। আইনি প্রক্রিয়া যেন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার হাতিয়ার না হয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি। দ্বিতীয়ত, ছাত্ররাজনীতিকে মূল রাজনৈতিক দলের হাত থেকে বের করে শিক্ষার্থীদের কল্যাণ ও জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগাতে হবে। তৃতীয়ত, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও আইনের শাসন শক্তিশালী করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী বা নেতা—কেউ আইনের ঊর্ধ্বে থাকতে না পারে।
সবশেষে বলা যায়, জাতীয় পার্টির নেতাদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা বর্তমান রাজনীতির অস্থির চিত্রকে আরও উন্মোচন করেছে। এ ধরনের পদক্ষেপ যেমন দুর্নীতি দমন প্রক্রিয়ায় সহায়ক হতে পারে, তেমনি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশও হতে পারে। আর শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ এই অস্বচ্ছ রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বহিঃপ্রকাশ। যদি রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভাবতে না শেখে, তবে এর ফল ভয়াবহ হবে—শিক্ষা, গণতন্ত্র, সমাজ সবকিছুই দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।


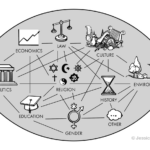



আপনার মতামত জানানঃ