
গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রায় ঘিরে রাজধানী ঢাকায় এক ধরনের অদৃশ্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তায় বের হলে স্বাভাবিক কোলাহলই চোখে পড়ে, যানজটে আটকে থাকা মানুষের বিরক্তি, অফিসপাড়ার ভিড়—সবই যেন আগের মতোই। কিন্তু এই স্বাভাবিকতার আড়ালে অদেখা এক তীব্র অস্থিরতা কাজ করছে; কারণ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে টানা কয়েকদিন ধরে ঘটছে ককটেল বিস্ফোরণ আর বাসে অগ্নিসংযোগের মতো চোরাগোপ্তা হামলা।
এই হামলাগুলো এখনো পর্যন্ত বড় কোনো প্রাণহানি ঘটায়নি। কোথাও কেউ নিহত হয়নি, গুরুতর আহত হওয়ার খবরও পাওয়া যায়নি। কিন্তু মানুষ বুঝে গেছে—বিষয়টা সংখ্যা বা হতাহতের পরিসংখ্যান নয়, মূল ভয়টি কাজ করছে ‘কখন, কোথায়, কীভাবে’—এই অনিশ্চয়তাকে ঘিরে। যে শহরে আপনি প্রতিদিন বাসে উঠে অফিসে যান, যে হাসপাতালের সামনে দিয়ে আপনি হেঁটে যান, যে স্কুলে আপনাদের সন্তান পড়ে—সেইসব চেনাজানা জায়গার নাম এখন হামলার তালিকায় উঠে আসছে। এটাই আতঙ্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে, তারা সর্বোচ্চ সতর্ক আছে, রাজধানীজুড়ে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। থানায় থানায় কড়া নির্দেশ গেছে, চেকপোস্ট বসানো হয়েছে, রাতের টহল বাড়ানো হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নজরদারি চলছে। কিন্তু এই সব ব্যবস্থার মাঝেও একের পর এক ককটেল বিস্ফোরণ আর আগুনের ঘটনা দেখাচ্ছে—দুর্বৃত্তরা এখনো পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতে পারছে। যে শহরে হাজার হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, যেখানে ছোটখাটো সড়ক দুর্ঘটনার ফুটেজও পরে হাতে চলে আসে, সেই শহরেই বারবার ঘটে যাচ্ছে এসব হামলা, অথচ পরিকল্পনাকারীদের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না।
সোমবার ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অন্তত ১২টি ককটেল বিস্ফোরণ এবং তিনটি অগ্নিসংযোগের ঘটনা এভাবে ছড়িয়ে থাকে রাজধানীজুড়ে। ধানমণ্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে শান্ত মারিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখায় থমকে যায় আশপাশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাত-আটজন তরুণ হেঁটে যাচ্ছিলেন বাসটির পাশ দিয়ে; কিছুক্ষণের মধ্যে বাসে আগুন ধরে যায়। ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট দৌড়ে এসে আগুন নেভালেও তারা বলতে পারেনি, কীভাবে আগুন লাগল—মল্টভ? দাহ্য পদার্থ? নাকি আগে থেকে রেখে যাওয়া কোনো জ্বালানি?
একই সন্ধ্যায় আগারগাঁও রেডিও স্টেশনের সামনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। অল্প সময়ের মধ্যে মিরপুরের শাহ আলী মার্কেটের সামনে তিনটি, সবুজবাগ এলাকায় আরও কয়েকটি বিস্ফোরণ হয়। কোথাও কাঁচ ভেঙে যায়, কোথাও মানুষ আতঙ্কে দৌড়ায়, কিন্তু হামলাকারীরা কখন আসে আর কখন অদৃশ্য হয়ে যায়—সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের কথাও অস্পষ্ট। যেন কয়েক সেকেন্ডের জন্য হাজির হয়ে, শব্দ আর ধোঁয়ার রেখা রেখে তারা মিলিয়ে যায় শহরের অগণিত গলির ভিড়ে।
এদিন ভোরে মেরুল বাড্ডা আর শাহজাদপুরে ভিক্টর পরিবহনের দুইটি বাসে অগ্নিসংযোগ ঘটে। ফজরের আজানেরও আগে, ঘুমন্ত শহরের প্রান্তিক এলাকাগুলোয় আগুন জ্বলে ওঠে বাসের শরীরে। ফায়ার সার্ভিস জানায়, তারা খবর পেয়ে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও কীভাবে আগুন লাগানো হলো, সে বিষয়ে কোনো পরিষ্কার তথ্য নেই। দুটো আগুন, দুটোই প্রায় একই ধরনের পরিবহনে, একই ভোরে—এ যেন হালকা একটা বার্তা, “আমরা যেখানে খুশি, যখন খুশি আঘাত করতে পারি।”
আরেকটি আলাদা ধারায় দেখা যাচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থাপনায় ককটেল হামলা। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপদেষ্টা ফরিদা আক্তারের ধানমণ্ডির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ‘প্রবর্তনা’কে লক্ষ্য করে সকালে দুটি ককটেল নিক্ষেপ করে দুই মোটরসাইকেল আরোহী। স্যার সৈয়দ রোডের একটি বাড়ির সামনে দুইটি মোটরসাইকেলে করে তারা আসে, কয়েক সেকেন্ডের ভেতর একটি ককটেল প্রতিষ্ঠানের ভেতরে, আরেকটি রাস্তায় ছুড়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলে যায়। আশপাশের মানুষ ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। অনেকে জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখে শুধু ধোঁয়া আর আতঙ্ক, হামলাকারীরা ততক্ষণে দূরে।
ধানমণ্ডি এলাকার আরেক প্রান্তে একই সকাল সাতটার দিকে ইবনে সিনা হাসপাতাল ও রাপা প্লাজার বিপরীতে মাইডাস সেন্টারের সামনে ধারাবাহিক চারটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন—আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা চলছে। কিন্তু শহরের সাধারণ বাসিন্দার কাছে এই ধরনের আশ্বাস এখন আর ততটা সান্ত্বনাদায়ক শোনায় না। তাদের প্রশ্ন, “আজ সেখানে, কাল কোথায়?”
এর দুদিন আগেই মিরপুরের গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে রাত ২টা ৪৩ মিনিটে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, একটি মোটরসাইকেলে করে মুখে গামছা বাঁধা দুই ব্যক্তি আসে, দ্রুতগতিতে পরপর দুটি ককটেল নিক্ষেপ করে আবার মোটরসাইকেল চেপে পালিয়ে যায়। পুরো ঘটনা কয়েক সেকেন্ডের—এই অল্প সময়ে আশেপাশে কোনো মানুষের প্রতিক্রিয়া, পুলিশের উপস্থিতি, কেউ ধরার চেষ্টা—কিছুই নেই। শুধু একটা ভয় থেকে যায়: শহরের যে কোনো মোড়ে, যে কোনো সময় এমন কয়েক সেকেন্ডের জন্যই হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসতে পারে।
শুধু রাস্তাঘাট নয়, নিরাপদ ভেবে নেওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গির্জাও টার্গেটে এসেছে। শনিবার রাতে মোহাম্মদপুরের সেন্ট যোসেফ স্কুলের ভেতরে ককটেল বিস্ফোরণের পর স্কুল কর্তৃপক্ষ থানায় জিডি করেছে। তারও আগে রমনার কাকরাইলে সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রাল গির্জায় দু’টি ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে, যার একটি বিস্ফোরিত হয়, অন্যটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। সেন্ট যোসেফের নাম শুনলেই অনেকের মনে ভেসে ওঠে ফলাফলের গর্ব, সহপাঠীদের স্মৃতি, আর গির্জা মানেই অনেকের কাছে প্রার্থনা আর শান্তির জায়গা। সেই জায়গাগুলোর নাম এখন বিস্ফোরণের খবরের সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ায় একটা গভীর মানসিক চাপ তৈরি হচ্ছে।
এই প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা সতর্ক করছেন, চোরাগোপ্তা এই ধারাবাহিক হামলার আলামত মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়। তাদের কথায়, অতীতের অভিজ্ঞতা বলে, দুর্বৃত্তরা অনেক সময় আগে ছোট ছোট হামলা চালিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা ‘পরিমাপ’ করে। কোথায় কত দ্রুত পুলিশ পৌঁছায়, কোথায় কতটা নজরদারি আছে, কোন কোন জায়গায় নজরদারির ফাঁক আছে—এসব তথ্য সংগ্রহের জন্যই যেন এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বিস্ফোরণ ও অগ্নিসংযোগ সাজানো হয়। পরে সেই ছবি মাথায় রেখেই বড় হামলা বা নাশকতার পরিকল্পনা আঁকা হয়।
এই প্রেক্ষাপটে বড় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করা যায় না। জুলাই মাসের গণ-অভ্যুত্থানের সময়কার হত্যাকাণ্ড ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার রায় ঘোষণার দিন ঘনিয়ে এসেছে। রায়কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা, গুজব, সামাজিক মাধ্যমে তর্ক-বিতর্ক—সব মিলিয়ে রাজনৈতিক তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই চড়া। এমন অবস্থায় সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন নিরাপত্তার স্বার্থে জাতীয় ঈদগাহ মাঠে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে, সুপ্রিম কোর্ট, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় ও সুপ্রিম কোর্ট বার ভবনে বিশেষ নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ঢাকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাতেও বাড়তি নিরাপত্তা বলয় তৈরি হয়েছে।
এ নিরাপত্তা বলয়ের আরেকটি অদৃশ্য দিক হলো রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর নজরদারি ও অভিযান। প্রতিটি থানাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের তালিকা ধরে ধরে ‘অভিযান’ চালানোর জন্য। ফলে রাতের আঁধারে অনেকেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের কড়া নক শোনেন বাড়ির দরজায়। কারো কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র, বিস্ফোরক বা নাশকতামূলক পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হচ্ছে, আবার অনেকেই দাবি করছেন—তাদের শুধু ‘সন্দেহের বশবর্তী’ হয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই টানাপোড়েন শহরের রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও ঘনীভূত করে তুলছে।
একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বাড়ছে তদারকি। বিভিন্ন পোস্ট, মন্তব্য, শেয়ার করা খবর নজরে রাখছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠী কী বলছে, কেউ নাশকতার ইঙ্গিত দিচ্ছে কি না, গোপন সমন্বয় হচ্ছে কি না—এসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিন্তু এই নজরদারি আবার অন্য এক আতঙ্কের জন্ম দিচ্ছে সাধারণ ব্যবহারকারীদের মাঝে—কোন বক্তব্য কোথায় ভুল ব্যাখ্যা হয়ে তার জন্য হয়তো কোনোদিন জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হতে পারে।
পুলিশের একটি অংশ স্বীকার করছে, নাশকতা করতে কেউ যদি প্রাণপণ চেষ্টা করে, তাকে সব সময় থামিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। ঢাকার মতো জনবহুল, জটিল শহরে প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি গলিতে সব সময় পুলিশের উপস্থিতি রাখা বাস্তবসম্মত নয়। দুর্বৃত্তরা আগে থেকেই ‘রেকি’ করে—অর্থাৎ কোন সময়ে কোথায় পুলিশের উপস্থিতি কম, কোন গলিতে ক্যামেরা নেই, কোথায় অন্ধকার বেশি—এসব দেখে টার্গেট নির্ধারণ করে। ককটেল ফাটাতে লাগে কয়েক সেকেন্ড, গান পাউডার ছিটিয়ে বাসে আগুন ধরাতে লাগে এক মিনিটও না। এই অল্প সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সব সময় ধরাশায়ী করা যায় না, এটাও এক বাস্তবতা।
তবু প্রশ্ন থেকেই যায়, রাজধানীর মানুষ কতদিন এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাবে? অফিসগামী কোনো বাবা যখন সকালে সন্তানকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়, তার মনের এক কোণে এখন আর শুধুই পড়াশোনার চিন্তা থাকে না; জড়িয়ে থাকে নিরাপত্তার প্রশ্নও। রাত এলে শহরের অনেক এলাকায় হালকা শব্দ হলেই বুক ধড়ফড় করে ওঠে—এটা কি তালাবদ্ধ দোকানের শাটার পড়ার শব্দ, নাকি দূরের কোনো বিস্ফোরণ? ছুটে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি গেলে কেউ কেউ ঘড়ি দেখে, কেউ পরিচিতদের ফোন করে জানতে চায়—“কোথায় আগুন লেগেছে?”
অন্যদিকে, এই পরিস্থিতি রাজনৈতিক বিভাজনকেও আরও উসকে দিচ্ছে। কেউ বলছে, এটা সুপরিকল্পিত ‘নাশকতা’, যার লক্ষ্য রায়ের আগে রাষ্ট্রকে দুর্বল দেখানো, অস্থিরতা তৈরি করা। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করে, এসব হামলা ক্ষমতাসীনদেরই কোনো ‘অভ্যন্তরীণ খেলা’, যাতে বিরোধী পক্ষকে দায়ী করে কঠোর দমন-পীড়নের যৌক্তিকতা দাঁড় করানো যায়। প্রমাণ-অপ্রমাণের এই বিতর্কের মধ্যে আটকে থাকে সাধারণ মানুষ, যার কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছায় খুবই সীমিতভাবে, আর পৌঁছানো তথ্যগুলোও প্রায়ই রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় রঙিন।
এমন পটভূমিতে ঢাকার প্রতিটি ছোট ঘটনা এখন বড় শঙ্কার ইঙ্গিত হয়ে দেখা দিচ্ছে। গির্জা, স্কুল, বাস, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান—দুর্বৃত্তদের এই বহুমুখী লক্ষ্যবস্তুর তালিকা দেখেই বোঝা যায়, তারা শুধু ভয় দেখাতে নয়, বরং নিজেদের ‘উপস্থিতি’ জানান দিতে চাইছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা তাই স্পষ্ট করেই বলছেন—এটি হয়তো ‘পরীক্ষামূলক ধাপ’, এর পরের ধাপ কী হতে পারে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা।
এই উদ্বেগের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঢাকাবাসীর দৈনন্দিন জীবন চলছেই। কেউ অফিসে যায়, কেউ দোকান খোলে, কেউ রিকশা নিয়ে বের হয়, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে যায়। সন্ধ্যায় কেউ আবার রেস্টুরেন্টে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। বাহ্যিকভাবে সবই স্বাভাবিক, কিন্তু অন্তর্গত সুরটা বদলে গেছে। রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া উৎসুক চোখ এখন একটু বেশিই সশঙ্ক, রাস্তা থেকে ভেসে আসা হালকা ধোঁয়া দেখলেও মনে পড়ে যায় খবরের কাগজে দেখা আগুনের ছবি।
অবশেষে প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়—এই শহর কি আবারও আগের মতো নির্ভার হবে? বাসে উঠে কি আবার কেউ নিশ্চিন্তে জানালার পাশে বসে বই পড়তে পারবে, কোনো বাবা-মা কি শিশু সন্তানকে নির্ভয়ে গির্জা বা স্কুলে পাঠাতে পারবেন, ব্যবসায়ী কি সকালবেলা দোকানের তালা খুলে আরেকবার চিন্তায় পড়বেন না? নাকি এই চোরাগোপ্তা বিস্ফোরণ আর আগুনের শিখা ঢাকাবাসীর সামষ্টিক স্মৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে এক অন্ধকার রেখা এঁকে রেখে যাবে? উত্তরটা আজই হয়তো জানা যাবে না, কিন্তু যে ভয় আর অনিশ্চয়তার সঙ্গে মানুষ এখন প্রতিদিন বাঁচছে, সেটাই এই সময়ের সবচেয়ে বড় সত্য।


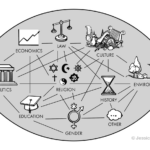



আপনার মতামত জানানঃ