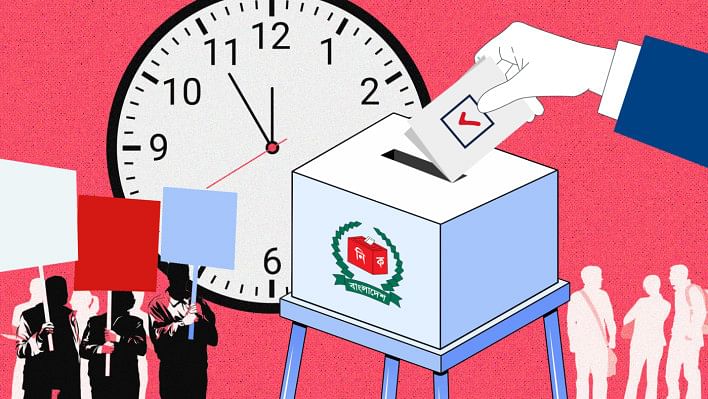 বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন (ইসি) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধনের মাধ্যমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, ভোটার অংশগ্রহণ, প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন এবং নির্বাচন-পরবর্তী স্বচ্ছতা—সব ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। এ পরিবর্তনগুলো মূলত নির্বাচনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে বাঁচানো, দলীয় স্বকীয়তা রক্ষা, অনিয়ম রোধ, প্রযুক্তির অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং ফলাফল ঘোষণার পদ্ধতিকে নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য করার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে।
বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন (ইসি) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধনের মাধ্যমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, ভোটার অংশগ্রহণ, প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন এবং নির্বাচন-পরবর্তী স্বচ্ছতা—সব ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। এ পরিবর্তনগুলো মূলত নির্বাচনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে বাঁচানো, দলীয় স্বকীয়তা রক্ষা, অনিয়ম রোধ, প্রযুক্তির অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং ফলাফল ঘোষণার পদ্ধতিকে নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য করার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে।
প্রথমত, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে একটি বড় বিতর্কের বিষয় ছিল যে, কোনো আসনে কেবল একজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিলে বা অন্য প্রার্থীরা সরে দাঁড়ালে তিনি বিনা ভোটেই নির্বাচিত হয়ে যেতেন। এই প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে ভোটারদের অংশগ্রহণের সুযোগ কেড়ে নিয়েছে এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমিয়ে দিয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কোনো আসনে একজন মাত্র প্রার্থী থাকলেও তাকে ‘না’ ভোটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। ‘না’ ভোট যদি জয়ী হয়, তবে প্রার্থী নির্বাচিত হবেন না এবং পুনরায় নির্বাচন হবে না। এ পদক্ষেপ মূলত ২০০৮ সালের সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কার এটিএম শামসুল হুদার কমিশনের প্রবর্তিত ‘না’ ভোট পদ্ধতির আংশিক পুনঃপ্রবর্তন। যদিও আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে ‘না’ ভোট বাতিল করেছিল, বর্তমান কমিশন আবার এটি ফিরিয়ে আনছে—তবে এবার সব আসনে নয়, শুধু একক প্রার্থী থাকলেই এর প্রয়োগ হবে।
দ্বিতীয়ত, জোটবদ্ধ নির্বাচনে অন্য দলের প্রতীক ব্যবহারের সুযোগ বিলোপ করা হয়েছে। অতীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছোট রাজনৈতিক দলগুলো বড় দলের সঙ্গে জোট বেঁধে শরীক দলের প্রতীকে নির্বাচন করত, যা অনেক ক্ষেত্রে ভোটারের কাছে প্রার্থীর প্রকৃত রাজনৈতিক পরিচয় অস্পষ্ট করে দিত। এখন থেকে জোটে থাকলেও প্রতিটি দলকে নিজ নিজ সংরক্ষিত প্রতীকেই নির্বাচনে অংশ নিতে হবে। নির্বাচন কমিশনের মতে, এটি রাজনৈতিক স্বকীয়তা বজায় রাখবে এবং ভোটারদের কাছে প্রতিটি দলের স্বতন্ত্র অবস্থান স্পষ্ট করবে।
তৃতীয়ত, ইভিএম বা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহারের বিধান সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে। বর্তমান ইসি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ইভিএম ব্যবহার না করার অবস্থান জানিয়েছিল এবং এবার আরপিও থেকেও এটি আনুষ্ঠানিকভাবে বাদ দিয়েছে। ফলে আগামী নির্বাচন পুরোপুরি ব্যালটের মাধ্যমে হবে। ইভিএমকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক ছিল—বিশেষ করে এর স্বচ্ছতা, প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং হ্যাকিংয়ের ঝুঁকি নিয়ে—যা এ সিদ্ধান্তের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে।
চতুর্থত, সমসংখ্যক ভোট পাওয়া প্রার্থীর মধ্যে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারণের বিধান বাতিল করা হয়েছে। আগে কোনো আসনে দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমান ভোট পেলে লটারির মাধ্যমে জয়ী নির্ধারণ করা হতো। এই পদ্ধতিকে অনেকেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে অসঙ্গত বলে সমালোচনা করেছেন, কারণ ভাগ্যের উপর নির্ভর করে সংসদ সদস্য নির্বাচন করা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন নয়। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
পঞ্চমত, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা পুনঃস্থাপন ও বিস্তৃত করা হয়েছে। আগে অনিয়ম প্রমাণিত হলে পুরো আসনের ভোট বাতিল করার ক্ষমতা সীমিত ছিল, কিন্তু এবার আবার সেই পূর্ণ ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইসি এখন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে এক বা একাধিক আসনের নির্বাচন বাতিল করতে পারবে। এছাড়া কোনো প্রার্থী নির্বাচনি হলফনামায় ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিলে—even যদি তিনি বিজয়ী হন—তার প্রার্থিতা বাতিল করার ক্ষমতাও থাকবে কমিশনের হাতে। এই পরিবর্তন নির্বাচনে সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।
ষষ্ঠত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে অপতথ্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান যোগ করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের যুগে এআই-ভিত্তিক প্রচারণা ও অপতথ্য ছড়ানোর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে। এ কারণে এআই অপব্যবহার রোধে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ।
সপ্তমত, ভোট গণনার সময় স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের গণনা কক্ষে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সাংবাদিকরা সরাসরি ভোট গণনা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন, যা অনিয়মের সুযোগ কমাবে এবং জনগণের আস্থা বাড়াবে।
অষ্টমত, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় সশস্ত্র বাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মানে, নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনীও আনুষ্ঠানিকভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মোতায়েন করা যাবে। এটি নির্বাচনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক হতে পারে, যদিও অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সেনা মোতায়েনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে।
সবশেষে বলা যায়, এসব পরিবর্তন নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে পারে। তবে এর কার্যকারিতা মূলত নির্ভর করবে রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা, নির্বাচনী আচরণবিধির কঠোর প্রয়োগ, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা এবং জনগণের আস্থার উপর। কারণ শুধু আইন বা বিধান পরিবর্তন করলেই সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত হয় না—বাস্তবায়নই এর আসল চ্যালেঞ্জ। যদি এই সংস্কারগুলো নিরপেক্ষভাবে এবং সঠিকভাবে কার্যকর করা যায়, তবে এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য একটি ইতিবাচক অগ্রগতি হয়ে উঠতে পারে।






আপনার মতামত জানানঃ