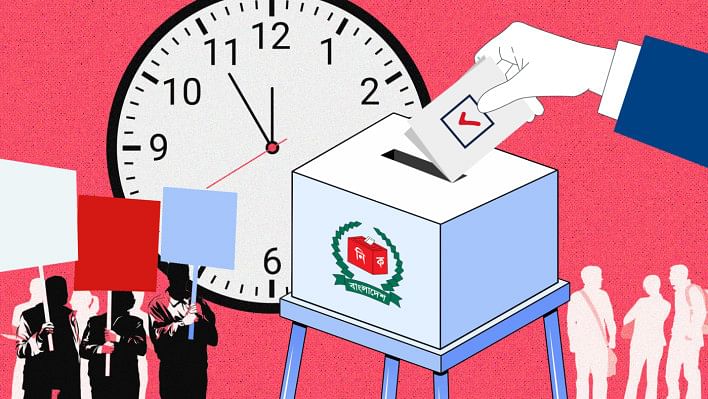 বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রতীক–ভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহু দশক ধরে চালু থাকলেও সাম্প্রতিক গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন দেশটির দলীয় সমীকরণে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এত দিন জোটের শরিক ছোট দলগুলো বড় দলের জনপ্রিয় প্রতীক ব্যবহার করে ভোট করত এবং সংসদে টিকে থাকার মতো শক্তি অর্জন করত। কিন্তু নতুন বিধানে বলা হয়েছে, কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অন্য দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। এই পরিবর্তন জোট রাজনীতির পুরোনো কাঠামোকে নষ্ট করে দিচ্ছে, আর তার ফলে প্রশ্ন উঠছে—ধানের শীষ এবং দাঁড়িপাল্লার মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতীকের বাইরে দাঁড়িয়ে কোনো দল কি বাস্তবিকভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে?
বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রতীক–ভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহু দশক ধরে চালু থাকলেও সাম্প্রতিক গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন দেশটির দলীয় সমীকরণে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এত দিন জোটের শরিক ছোট দলগুলো বড় দলের জনপ্রিয় প্রতীক ব্যবহার করে ভোট করত এবং সংসদে টিকে থাকার মতো শক্তি অর্জন করত। কিন্তু নতুন বিধানে বলা হয়েছে, কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অন্য দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। এই পরিবর্তন জোট রাজনীতির পুরোনো কাঠামোকে নষ্ট করে দিচ্ছে, আর তার ফলে প্রশ্ন উঠছে—ধানের শীষ এবং দাঁড়িপাল্লার মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতীকের বাইরে দাঁড়িয়ে কোনো দল কি বাস্তবিকভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে?
বাংলাদেশের রাজনীতির দীর্ঘ ইতিহাসে নৌকা ও ধানের শীষ ছিল কেন্দ্রীয় প্রতীক। আওয়ামী লীগের নৌকা ও বিএনপির ধানের শীষের দ্বৈরথে দেশ তার বহু গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন দেখেছে। জাতীয় পার্টির লাঙল এবং জামায়াতে ইসলামের দাঁড়িপাল্লা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের সীমিত পরিসরে জায়গা রেখেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরের সংকট, জুলাইয়ের অভ্যুত্থান এবং পরবর্তী নিবন্ধন স্থগিতাদেশ আওয়ামী লীগকে আগামী নির্বাচনের মাঠ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এর ফলে নৌকা প্রতীক অনুপস্থিত থাকায় নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে—এবার ভোটের প্রতিযোগিতা মূলত ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লা ঘিরেই আবর্তিত হবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন।
এখনকার বাস্তবতায় বিএনপি কার্যত সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মাঠে রয়েছে। দলটি প্রাথমিকভাবে যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে, তাতে ৩৭টি আসন ফাঁকা রাখা হয়েছে শরিক দল বা মিত্রদের জন্য। জামায়াত ইতিমধ্যে সারা দেশে প্রার্থী ঘোষণা করেছে এবং ইসলামী সাতটি দলকে সঙ্গে নিয়ে জোটধর্মী সমঝোতার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এনসিপি—যারা জুলাইয়ের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের ঘিরে আলোচনায় উঠে এসেছে—তাদের প্রতীক শাপলা কলি। যদিও তারা আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো জোটে যুক্ত হতে দৃশ্যত অনীহা দেখালেও বিএনপির সঙ্গে নির্বাচনকালীন সমন্বয় হতে পারে বলে আভাস মিলেছে। জাতীয় পার্টি এখনো মাঠে নামেনি, আর ১৪ দলের শরিকদের অনেক নেতা গ্রেপ্তার বা পলাতক থাকায় তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা ন্যূনতম।
গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধনের মাধ্যমে জোটভুক্ত দলগুলোকে বাধ্য করা হয়েছে নিজস্ব প্রতীকেই নির্বাচন করতে। অতীতে ছোট দলগুলো নিজের প্রতীকে ভোট করে জেতার বাস্তব সুযোগ পেত না, এ কারণে তারা বড় জোটের প্রতীকে নির্ভর করত। ২০০১ সালের নির্বাচন তার বড় উদাহরণ, যেখানে ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা আমিনী কিংবা শাহীনুর পাশা চৌধুরীরা বিএনপির ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে জিতে সংসদে প্রবেশ করেন। বিএনপি–জামায়াত জোট সেই নির্বাচনে বিপুল বিজয় পেলেও ছোট শরিকদের টিকে থাকার মূল কারণ ছিল ধানের শীষ প্রতীকের জনপ্রিয়তা এবং বিএনপির গ্রাসরুট সমর্থকদের একযোগে ভোট দেওয়া। একইভাবে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) তখন চারটি আসন পেয়েছিল ধানের শীষ প্রতীক নিয়েই।
২০১৮ সালের নির্বাচন, যা ‘রাতের ভোট’ বিতর্কে কলঙ্কিত হয়েছিল, সেখানে গণফোরামের দুজন প্রার্থী—সুলতান মনসুর ও মোকাব্বির খান—জোটগত সমন্বয় ও প্রতীক–সংকটের সুযোগে ধানের শীষ বা উদীয়মান সূর্য প্রতীকে জিতে সংসদে প্রবেশ করেন। তাদের সাফল্যের পেছনেও বিএনপির ভোটারদের সমর্থন বড় ভূমিকা রেখেছিল। ২০১৪ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনগুলোতে আওয়ামী লীগ তাদের শরিকদের নৌকা প্রতীক দিলেও পূর্ণ সমর্থন দেয়নি বিধায়, অধিকাংশে পরাজিত হয়েছে শরিক প্রার্থীরা। বিশেষভাবে ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিজেদের অনেক নেতাকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে উৎসাহিত করেছিল, উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনকে ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ’ দেখানো—ফলে শরিকরা নৌকা প্রতীক নিয়েও যথেষ্ট সমর্থন পায়নি।
এই প্রেক্ষাপটে মূল সমস্যা দাঁড়িয়েছে—এবার প্রতিটি দলকে নিজ প্রতীকেই ভোট করতে হবে। ফলে ছোট দলগুলো নিজেদের প্রতীকের জনপ্রিয়তা এবং সংগঠনের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার যে ক্ষমতা, তা অনেক সীমিত। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবেশে বিএনপি এবং জামায়াতের সাংগঠনিক শক্তি ও ভোটব্যাংক তুলনামূলক বড় হলেও অন্য ছোট দলগুলো বড় ধরনের বিপদে পড়বে। কারণ একদিকে তাদের নিজস্ব প্রতীক অতটা পরিচিত নয়, অন্যদিকে বড় শরিকদের সমর্থন সম্পূর্ণভাবে পাওয়া নিয়েও প্রশ্ন আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—যদি বিএনপি কোনো আসন শরিককে ছাড়াও, সেই আসনে বিএনপির কোনো প্রভাবশালী নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হন, তবে শরিকের জেতার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। বিএনপির মতো বড় দলগুলোর ইতিহাস বলছে, ভেতরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনো কখনো শরিকদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
এদিকে জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়িপাল্লা প্রতীক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অপ্রচলিত থাকলেও চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের জয় তাদের সাংগঠনিক পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ফলে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক গ্রাসরুটে আবারও সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। একই সঙ্গে ইসলামী দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ভোটে যাওয়ার প্রস্তুতি তাদের ভোট–সমীকরণকে আরও শক্তিশালী করবে। বিএনপি–জামায়াতের ভোটব্যাংক সম্মিলিত হলে ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লা–এই দুই প্রতীকই সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। আর যেহেতু নৌকা নেই, ফলে ক্ষমতার প্রতীকধারীর মূখ্য আকর্ষণও নেই।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বলে—জোটগত নির্বাচনে ছোট শরিকদের সাফল্যের তিনটি প্রধান কারণ থাকে। প্রথমত, বড় দলের প্রতীক ব্যবহার। দ্বিতীয়ত, বড় দলের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন। তৃতীয়ত, বড় দলের কর্মী–সমর্থকদের পুরোপুরি সমর্থন নিশ্চিত করা। ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এই তিনটির কোনোটি নিশ্চিত করতে পারেনি—ফলে নৌকা প্রতীক পেলেও শরিকরা হেরে যায়। এবার বিএনপি–জামায়াত জোট চাইলেও প্রথম সুবিধাটি পাচ্ছে না, কারণ আইন তাদের প্রতীক ছেড়ে দিতে দিচ্ছে না। ফলে অন্য দুটি সুবিধা—স্বতন্ত্র বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ কর্মীদের আন্তরিক সমর্থন—এই দুই দিকেই তাদের সাফল্য নির্ভর করবে।
রাজনৈতিক বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের ছোট রাজনৈতিক দলগুলো নিজের প্রতীকে ভোট জয়ের জন্য প্রস্তুত নয়। বহু বছরের প্রতীকের পরিচিতি, ভোটার–আস্থার ভিত্তি, গ্রাসরুট নেটওয়ার্ক—এসবই বড় দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ছোট দলগুলো অবহেলা করেছে বা গড়ে ওঠেনি। এখন হঠাৎ প্রতীক–নির্ভরতার নিয়ম পরিবর্তনে তারা নিজেদের সংগঠনের শক্তি কতটা পুনর্গঠন করতে পারবে, তার ওপরই বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে। কিছু দল বলছে, এটি তাদের জন্য আত্মপরিচয় পুনর্গঠনের সুযোগ। কিন্তু বাস্তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, প্রতীক সীমাবদ্ধতা ছোট দলগুলোর জন্য অন্তত আগামী এক–দুই নির্বাচনে বড় ধাক্কা হবে।
এর ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল দুই–তিনটি বড় দলের প্রভাব–প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে সঙ্কুচিত হতে পারে। নৌকা নেই, তাই আওয়ামী লীগ স্বাভাবিকভাবেই বাইরে। লাঙলও এখন দুর্বল। বাকি শক্তিগুলোকে দেখলে দেখা যায়—ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লাই এখন সবচেয়ে সংগঠিত ও পরিচিত প্রতীক। অন্য প্রতীকগুলো ভোটারদের কাছে সীমিত পরিচিত। ফলে বড় শরিকদের আন্তরিক সমর্থন না থাকলে ছোট দলগুলোর জেতা অত্যন্ত কঠিন হবে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বলে—প্রতীক শুধু একটি চিহ্ন নয়, এটি একটি বিরাট রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব। প্রতীকের সঙ্গে জড়িত থাকে দলের ইতিহাস, সংগ্রাম, বিজয়–পরাজয়, নেতৃবৃন্দের স্মৃতি এবং ভোটারের আবেগ। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে নতুন প্রতীক বা কম পরিচিত প্রতীককে ভোটাররা কতটা গুরুত্ব দেবে, তা নিশ্চিত নয়। বিশেষ করে যখন দুটি বড় দল দীর্ঘ সময় ধরে জনগণের রাজনৈতিক আবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছে, তখন ছোট দলগুলোকে জনগণ হঠাৎ নতুন করে মূল্যায়ন করবে, এমনটা সহজভাবে ধরে নেওয়া যায় না।
সুতরাং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের সংশোধন বাংলাদেশের জোট রাজনীতিকে নতুন পথে ঠেলে দিয়েছে। আগামী নির্বাচনে দেখা যাবে—কীভাবে বড় দলগুলো এই নতুন আইনি সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাদের শরিকদের সঙ্গে সমন্বয় করে। বিএনপি–জামায়াত যদি তাদের নিজ নিজ প্রতীকেই শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ রোধ করতে পারে, তবে তাদের শরিকদের কিছু আসন ভাগ করে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু ছোট দলগুলোকে নিজেদের সাংগঠনিক সক্ষমতা নতুন করে প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় নতুন নির্বাচনী বাস্তবতা সংসদকে দুই–তিনটি বড় দলের ঘরেই সীমাবদ্ধ করে ফেলবে এবং বহু ছোট দল, যারা এত দিন জোটের কারণে সংসদে টিকে ছিল, তারা বড় ধরনের রাজনৈতিক অস্তিত্বসঙ্কটে পড়বে।
এই প্রতীক–ভিত্তিক বাধ্যবাধকতা দেশের রাজনীতিকে দীর্ঘমেয়াদে আরও প্রতিযোগিতামূলক করতে পারে—যদি ছোট দলগুলো সত্যিকার অর্থে নিজেদের পরিচয় ও সক্ষমতা পুনর্নির্মাণে সফল হয়। কিন্তু তা হবে সময়সাপেক্ষ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত চিত্র হলো—ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের আধিপত্যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন দুই বৃহৎ ধারার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রূপ নেবে। আর ছোট দলগুলোকে প্রমাণ করতে হবে, তারা প্রতীকের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে সত্যিকারের বিকল্প রাজনীতির মুখ হতে পারে কি না।






আপনার মতামত জানানঃ