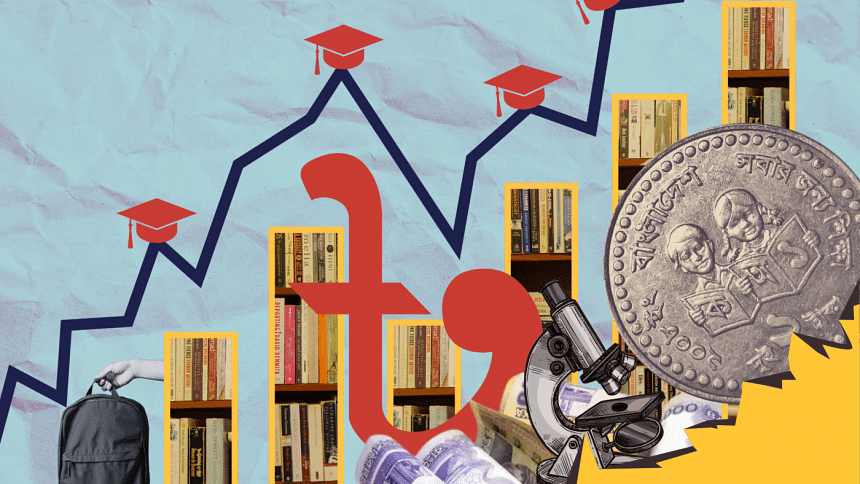 টাকা ছাপানো নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক সময়েই একটি সহজ ধারণা থাকে—সরকার চাইলে তো কাগজে ছাপ দিয়ে যত খুশি টাকা তৈরি করতে পারে, তাহলে অর্থনৈতিক সংকট কেন? নিত্যপণ্যের দাম বাড়লে কেন তা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না? অথবা ব্যাংকে টাকা না থাকলে সরকার চাইলেই তো নতুন টাকা ছাপাতে পারে! অথচ অর্থনীতির বাস্তবতা বলছে, টাকা ছাপা যতটা সহজ মনে হয়, এর ফলাফল ততটাই ভয়াবহ হতে পারে।
টাকা ছাপানো নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক সময়েই একটি সহজ ধারণা থাকে—সরকার চাইলে তো কাগজে ছাপ দিয়ে যত খুশি টাকা তৈরি করতে পারে, তাহলে অর্থনৈতিক সংকট কেন? নিত্যপণ্যের দাম বাড়লে কেন তা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না? অথবা ব্যাংকে টাকা না থাকলে সরকার চাইলেই তো নতুন টাকা ছাপাতে পারে! অথচ অর্থনীতির বাস্তবতা বলছে, টাকা ছাপা যতটা সহজ মনে হয়, এর ফলাফল ততটাই ভয়াবহ হতে পারে।
একটি দেশের অর্থনীতির অন্যতম বড় ভিত্তি হচ্ছে তার মুদ্রা, অর্থাৎ টাকার ওপর মানুষের আস্থা। এই আস্থা তৈরি হয় অর্থনীতির বাস্তব শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে—দেশে কত পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে, কতটা সেবা দেওয়া হচ্ছে, দেশের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ কত, কর আদায়ের দক্ষতা কেমন, সরকারি ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা কী রকম। এই বাস্তব ভিত্তি ছাড়া টাকা ছাপালে সেটি শুধু কাগজের টুকরোই থেকে যায়, যার পেছনে কোনো মূল্য থাকে না।
ধরা যাক, বাংলাদেশ ব্যাংক হুট করে ৫০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়ে বাজারে ছেড়ে দিল। এতে প্রথমেই দেখা যাবে—লোকজনের হাতে টাকার পরিমাণ বেড়ে গেছে। তাদের কেনাকাটার সামর্থ্য বাড়বে। কিন্তু বাজারে যে পরিমাণ চাল, ডাল, তেল, পোশাক বা সেবা রয়েছে, তা তো বাড়েনি। ফলে একই পণ্যের জন্য বেশি মানুষ বেশি দাম দিতে প্রস্তুত থাকবে। এতে দ্রব্যমূল্য বাড়বে। মূল্যস্ফীতি শুরু হবে। অর্থাৎ, বাজারে টাকার সরবরাহ বাড়ার কারণে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে যাবে। মানুষ বুঝতে পারবে, আগের মতো আরেকশ টাকা দিয়ে বাজার করা যাচ্ছে না।
মূল্যস্ফীতি একবার শুরু হলে তা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। যদি সরকার আরও টাকা ছাপে মূল্যস্ফীতির চাপ সামলাতে, তাহলে সেই আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ হয়। এই পরিস্থিতিই একসময় ‘হাইপারফ্লেশন’-এ রূপ নেয়, যেখানে পণ্যের দাম দিনে দিনে নয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়তে থাকে। মানুষ তখন টাকা জমিয়ে রাখতে চায় না, কারণ সে জানে—আগামীকাল এই টাকার মূল্য থাকবে না।
এমন বিপর্যয়ের বাস্তব উদাহরণ ইতিহাসে অনেক আছে। জিম্বাবুয়ে ২০০৮ সালে যখন সীমাহীন টাকা ছাপাতে থাকে, তখন এক বছরের মধ্যে তাদের মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ২৩ কোটি ১০ লাখ শতাংশে। এতটা বেশি যে, এক কাপ চা খেতে লাগতো ট্রিলিয়ন ডলার! অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সরকার ১০০ ট্রিলিয়ন ডলারের নোট ছাপাতে বাধ্য হয়, যা এখনো বিশ্বে সর্বোচ্চ মূল্যমানের ব্যাংকনোট হিসেবে পরিচিত। জিম্বাবুয়ের মানুষ শেষ পর্যন্ত তাদের জাতীয় মুদ্রাকে পরিত্যাগ করে মার্কিন ডলার ও দক্ষিণ আফ্রিকার র্যান্ড ব্যবহার শুরু করে।
আরেকটি উদাহরণ ভেনেজুয়েলা। ২০১৯ সালে দেশটি বাজেট ঘাটতির ৩০ শতাংশ মেটাতে অতিরিক্ত টাকা ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়। দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন ও ব্যর্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কারণে সেই টাকা উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ না হয়ে শুধু ভর্তুকি, বেতন ও রাজনৈতিক খরচে চলে যায়। ফলাফল—মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ১০,০০০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। বাজারে মাংস, চাল, তেল, ওষুধ কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না। মানুষ খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোতে পাড়ি দিতে শুরু করে।
তাহলে প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশ কি এই ভুল পথে হাঁটছে? সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে ছয়টি বেসরকারি ব্যাংকের জন্য ২২ হাজার কোটি টাকা ছেপেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। যদিও এটি ছিল একটি সংকট মোকাবেলার প্রয়াস, তবুও অর্থনীতিবিদদের অনেকেই এটিকে ঝুঁকিপূর্ণ বলছেন। কারণ, এর ফলে বাজারে তারল্য বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু উৎপাদন বাড়েনি। ফলে এই বাড়তি টাকা মূল্যস্ফীতিকে আরও উসকে দিতে পারে।
বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণত তিনটি বৈধ ও প্রয়োজনীয় কারণে টাকা ছাপে—প্রথমত, পুরনো ও ছেঁড়া নোট বাতিল করে নতুন নোট ছাপানোর জন্য; দ্বিতীয়ত, উৎসব বা মৌসুমি সময়গুলোতে বাড়তি লেনদেন সামলাতে; তৃতীয়ত, অর্থনীতির আকার যখন বাড়ে, তখন বাজারে টাকার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কিছুটা বাড়তি টাকা ছাপানো হয়। এই সবই নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত পদক্ষেপ। কিন্তু বাজেট ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে বা রাজনৈতিক চাপ সামলাতে অতিরিক্ত টাকা ছাপা বিপদ ডেকে আনতে পারে।
মূল্যস্ফীতি শুধু অর্থনীতির নয়, সামাজিক দুর্যোগও বটে। যখন মানুষের আয়ের চেয়ে খরচ বেড়ে যায়, তখন তারা সঞ্চয় খরচ করতে বাধ্য হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধীরে ধীরে নিম্নবিত্তে পরিণত হয়। গরিব মানুষ আরও গরিব হয়ে পড়ে। জীবনযাত্রার মান কমে যায়, দারিদ্র্য বাড়ে, বৈষম্য তীব্র হয়। এর ফলে সমাজে অস্থিরতা দেখা দেয়, বেকারত্ব বাড়ে, অপরাধ প্রবণতা বাড়ে। এক সময় পুরো অর্থনীতিই মুখ থুবড়ে পড়ে।
সরকার চাইলে সংকট মোকাবেলায় টাকা ছাপা ছাড়া আরও অনেক বিকল্প পথে হাঁটতে পারে। যেমন—কর আদায়ের পরিধি বাড়ানো, অপচয় রোধ করা, দুর্নীতি কমানো, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ সংগ্রহে স্বচ্ছতা আনা, উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। এগুলো সবই সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর কাজ, কিন্তু টেকসই সমাধান।
বাংলাদেশে করজালের আওতায় জনগণের একটি বড় অংশ নেই। যেসব ধনবান ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আয় কর দেয়ার কথা, তাদের অনেকেই নানা ফাঁকফোকর দিয়ে কর ফাঁকি দেয়। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। সরকার যখন ভোটমুখী হয়ে জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে চায়, তখন ভর্তুকি, বোনাস, রাজনৈতিক প্রকল্পে অতিরিক্ত ব্যয় করে। এসবই বাজেট ঘাটতির কারণ হয়, আর সেই ঘাটতি পূরণে টাকা ছাপানোর লোভ জাগে।
কিন্তু অর্থনীতি কোনো যাদুবিদ্যার খেলা নয়। এটি বাস্তবতা, পরিমিতি ও আস্থার উপর দাঁড়ানো এক কঠিন কাঠামো। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের টাকা ছাপানোর ক্ষমতা থাকলেও সেটি কোনো খেলনার মতো ব্যবহার করা যায় না। আক্ষরিক অর্থেই এটি দুই ধার বিশিষ্ট তরবারি—সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে বিপদ সামাল দেওয়া যায়, কিন্তু ভুলভাবে ব্যবহার করলে পুরো অর্থনীতি রক্তাক্ত হয়ে পড়ে।
অতএব, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শুধু সংখ্যার হিসাব নয়, জনগণের জীবনমান, বাজারের স্থিতিশীলতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আর্থিক নিরাপত্তাকেও মাথায় রাখতে হয়। টাকাকে যদি শুধু ছাপার কাগজ ভাবা হয়, তাহলে সেটি একসময় কেবল কাগজই হয়ে পড়ে। কিন্তু টাকাকে যদি মূল্য, আস্থা ও অর্থনীতির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবেই তা দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তিতে রূপ নিতে পারে।
সুতরাং, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকার যখনই টাকা ছাপার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সেটি কেবল একটি আর্থিক সিদ্ধান্ত নয়, সেটি একটি জাতীয় নৈতিকতারও পরীক্ষা। কারণ, টাকা ছাপানো যায়, কিন্তু তার মূল্য যদি বাজার, জনগণ ও দেশের ওপর পড়ে, তাহলে সেই মূল্য অনেক বেশি ভয়ংকর হতে পারে। ইতিহাস আমাদের তা দেখিয়েছে বারবার—এখন সময় সাবধান হওয়ার।






আপনার মতামত জানানঃ