 বাংলাদেশের সরকারি বকেয়া ঋণ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ২১ ট্রিলিয়ন টাকা অতিক্রম করেছে। দীর্ঘদিনের দুর্বল রাজস্ব সংগ্রহ এবং উচ্চ ব্যয়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো এই ঋণ বৃদ্ধিকে দ্রুততর করেছে। অর্থ বিভাগের নতুন ঋণ বুলেটিন অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন শেষে মোট সরকারি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১.৪৪ ট্রিলিয়ন টাকা, যা এক বছর আগের ১৮.৮৯ ট্রিলিয়ন টাকার তুলনায় প্রায় ১৪ শতাংশ বেশি।
বাংলাদেশের সরকারি বকেয়া ঋণ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ২১ ট্রিলিয়ন টাকা অতিক্রম করেছে। দীর্ঘদিনের দুর্বল রাজস্ব সংগ্রহ এবং উচ্চ ব্যয়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো এই ঋণ বৃদ্ধিকে দ্রুততর করেছে। অর্থ বিভাগের নতুন ঋণ বুলেটিন অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন শেষে মোট সরকারি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১.৪৪ ট্রিলিয়ন টাকা, যা এক বছর আগের ১৮.৮৯ ট্রিলিয়ন টাকার তুলনায় প্রায় ১৪ শতাংশ বেশি।
বিদেশি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯.৪৯ ট্রিলিয়ন টাকা, যা মোট ঋণের ৪৪ শতাংশেরও বেশি। গত পাঁচ বছরে বিদেশি ঋণ দ্রুত বেড়েছে—২০২১ সালে যার পরিমাণ ছিল মাত্র ৪.২০ ট্রিলিয়ন টাকা। দেশীয় ঋণও একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১১.৯৫ ট্রিলিয়ন টাকা, যা আগের বছরের ১০.৭৬ ট্রিলিয়ন টাকার তুলনায় প্রায় ১১ শতাংশ বেশি। তথ্য বলছে, বিদেশি ঋণ দেশীয় ঋণের তুলনায় দ্বিগুণ গতিতে বাড়ছে।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, মহামারির পর উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলোর বাজেট সহায়তা এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, ঢাকা মেট্রোরেল, মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্পে দ্রুত অর্থ ছাড়ের কারণে ঋণ বেড়েছে। সিপিডির বিশিষ্ট গবেষক প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান মন্তব্য করেন যে সরকারি ঋণের বর্তমান ধারা বাংলাদেশে উদ্বেগ তৈরি করছে। তিনি বলেন, দুর্বল রাজস্ব সংগ্রহের কারণে উন্নয়ন খরচ চালাতে সরকারকে ক্রমাগত ঋণ নিতে হচ্ছে, এবং দেশীয় ঋণে সুদের হার যেমন বেশি, বিদেশি ঋণের বেশিরভাগই নন-কনসেশনাল—অর্থাৎ উচ্চ সুদের হার, স্বল্প মেয়াদি পরিশোধের চাপ এবং খুব কম গ্রেস পিরিয়ড থাকে। ফলে ঋণ পরিষেবার চাপ প্রতি বছর বাড়ছে।
বাংলাদেশে বিদেশি ঋণ বৃদ্ধির গতি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ বলে সাম্প্রতিক এক এডিবি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। গত অর্থবছরে সুদ পরিশোধে সরকারের খরচ হয়েছে ১,৩২,৪৬০ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি। বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধ বেড়েছে ২১ শতাংশ এবং দেশীয় ঋণের সুদ পরিশোধ বেড়েছে ১৬ শতাংশ। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে নেওয়া ট্রেজারি বিল ও বন্ডের সুদ ব্যয় এক বছরে ৪৩ শতাংশ বেড়েছে।
আইএমএফ জানিয়েছে, বহিরাগত ঋণের ঝুঁকি বাড়তে থাকায় FY26 অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ কত বিদেশি ঋণ নিতে পারবে তার একটি সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বছর সর্বোচ্চ ৮.৪৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ নেওয়া যাবে, এবং ত্রৈমাসিকভাবে এই ঋণ গ্রহণের ওপর নজরদারি করা হবে। আইএমএফের সর্বশেষ ঋণস্থিতি বিশ্লেষণে বাংলাদেশকে “লো রিস্ক” থেকে নামিয়ে “মডারেট রিস্ক” শ্রেণিতে আনা হয়েছে, কারণ ঋণ পরিশোধের চাপ এখন রপ্তানি ও রাজস্ব আয়ের তুলনায় অনেক বেশি। FY24 সালে ঋণ-রপ্তানি অনুপাত বেড়ে হয়েছে ১৬২.৭ শতাংশ, যা তাদের পূর্বাভাসের তুলনায় অনেক বেশি। ঋণ পরিষেবা-রাজস্ব অনুপাতও বেড়েছে, ফলে সরকারের নতুন ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা সংকুচিত হয়েছে।
প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান মনে করেন, নতুন সরকারকে রাজস্ব বৃদ্ধি প্রাধান্য দিতে হবে—কারণ বাংলাদেশে রাজস্ব সংগ্রহ দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের অর্ধেকের মতো। এজন্য এনবিআর-এর প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বাড়াতে হবে এবং শাসনব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। নতুন ঋণ গ্রহণেও সতর্কতা প্রয়োজন, যাতে সুদের হার, উৎস, পরিশোধের মেয়াদ ও গ্রেস পিরিয়ড বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং পুরোনো ঋণ শোধ করতে নতুন ঋণ নেওয়ার দুষ্টচক্রে পড়া না হয়।
এদিকে সরকার একটি একীভূত ডেট ম্যানেজমেন্ট অফিস (DMO) গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, যাতে সরকারি ঋণের তদারকি আরও শক্তিশালী হয় এবং ঝুঁকি কমে। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক এই উদ্যোগে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। তারা বলেছে যে বর্তমানে ঋণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিভিন্ন সংস্থায় ছড়িয়ে রয়েছে, ফলে সমন্বয়হীনতা তৈরি হচ্ছে, তথ্যভান্ডার অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে পড়ছে এবং একটি কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যালোচনা করা কৌশল তৈরি করা কঠিন হচ্ছে। তাদের মতে, দেশের কাছে একটি অডিটেড, কেন্দ্রীয় ঋণ ডেটাবেস নেই এবং সঠিক নগদ প্রবাহ পূর্বাভাস ব্যবস্থাও অনুপস্থিত—যা কার্যকর ও সাশ্রয়ী ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরি।
প্রস্তাব অনুযায়ী, প্রথম ধাপে অর্থ বিভাগের অধীনে সরকারি এবং সরকারি গ্যারান্টিযুক্ত সব ঋণ ব্যবস্থাপনা একীভূত করা হবে। নতুন অফিসটি দেশীয় ঋণ ইস্যু তদারকি করবে, বার্ষিক ঋণ গ্রহণ পরিকল্পনা তৈরি করবে, ঝুঁকি বিশ্লেষণ করবে এবং বিদ্যমান বিভিন্ন ডেটাবেস একত্রিত করে একটি অভিন্ন ঋণ তথ্যভান্ডার তৈরি করবে। এর জন্য পরিষ্কার আইনি কাঠামো, দক্ষ জনবল, আধুনিক আইটি সিস্টেম এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে দৃঢ় সমন্বয় প্রয়োজন হবে। পরবর্তী সময়ে এই অফিস আরও স্বায়ত্তশাসিত হয়ে ঋণ-সম্পর্কিত ঝুঁকি ও দায় পর্যবেক্ষণ এবং বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্বও নিতে পারে। পুরো প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং ধাপে ধাপে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এই একীভূত ঋণ ব্যবস্থাপনা অফিস চালু হলে বাজারে আস্থা বাড়বে, ঋণ গ্রহণের খরচ কমবে, ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।


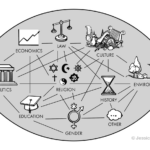



আপনার মতামত জানানঃ