
বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন আবারও অস্থিরতার এক চক্রে প্রবেশ করছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গসংগঠনের বহু নেতাকর্মী রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক, মোড় এবং আবাসিক এলাকার গলিতে ঝটিকা মিছিল করছে—এমন দৃশ্য সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বারবার ঘটছে। এই মিছিলগুলোর লক্ষ্য সরাসরি সংঘর্ষে জড়ানো নয়; বরং শহরের স্বাভাবিক আবহাওয়ার ভেতরে হঠাৎ করে উপস্থিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব এবং সক্রিয়তার জানান দেওয়া। এই কাজটিই এখন হয়ে উঠেছে একটি মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কৌশল। আর এর জবাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও সমান তৎপর। গত দশ মাসে রাজধানীর বিভিন্ন থানা ও ইউনিট মিলে প্রায় তিন হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে—এমন তথ্য জানানো হয় পুলিশের মিডিয়া ব্রিফিংয়ে।
গ্রেপ্তারের সংখ্যা শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়; এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক অস্বস্তি, রাস্তার নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার মনস্তাত্ত্বিক খেলা। ঝটিকা মিছিল সাধারণত খুব দ্রুত সংগঠিত হয়, কয়েক মিনিট স্থায়ী থাকে এবং হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। কোনো বড় সমাবেশ নয়—অনেক ক্ষেত্রেই ৩০ থেকে ১২৫ জনের দল রাস্তার ওপর হঠাৎ ব্যানার নিয়ে দাঁড়ায়, স্লোগান দেয়, কখনো ব্যানার-ফেস্টুন তুলে ধরা হয়, তারপর পুলিশ উপস্থিত হওয়ার আগেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সামাজিক মাধ্যমে এর ছবি এবং ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া—এই হলো প্রধান লক্ষ্য। জনতার মনে প্রশ্ন জাগানো: “তারা কি তবে সত্যিই নিস্তেজ হয়ে যায়নি? তারা কি এখনও সক্রিয়?” রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং নাগরিক সমাজের কাছে একটি বার্তা পাঠানো: “আমরা আছি।”
পুলিশ বলছে, এই মিছিলগুলোর পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট সংগঠিত অর্থায়ন। কেউ একজন বা কয়েকজন পেছন থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, যোগাযোগ রাখছে, অংশগ্রহণকারীদের অর্থ প্রণোদনা দিচ্ছে। তাদের কাজকে পুলিশ শুধু মিছিল নয়, বরং “জনমনে আতঙ্ক তৈরি করার প্রচেষ্টা” হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে এসব মিছিল থেকে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটেছে। বিস্ফোরণের শব্দ সাধারণ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তাকে নষ্ট করে, শহরের আবহকে অস্থির করে, এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সক্রিয়ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য করে। তাই কেবল মিছিল নয়, এটিকে পুলিশের চোখে “স্ট্রিট প্রেসার পলিটিক্স” হিসেবে দেখা হচ্ছে।
কর্তৃপক্ষের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে শুধু যারা মিছিলে হাতেনাতে ধরা পড়ছে তারাই গ্রেপ্তারের তালিকায় পড়ছে। তবে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে তাদের অতীত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, আগের কোনো মামলায় যুক্ততা, এবং সহিংসতা বা ভাঙচুরে সম্পৃক্ততা আছে কি না। এই ‘যাচাই-বাছাই’ প্রক্রিয়াটি নিজেই একটি মনস্তাত্ত্বিক চাপ হিসেবে কাজ করে—কারণ যারা গ্রেপ্তার হচ্ছে বা হতে পারে, তাদের পরিবার, পরিচিতি এবং রাজনৈতিক নেটওয়ার্কের ওপর শঙ্কা বেড়ে যায়। রাজনীতির ভাষায় এটি ‘কন্ট্রোলিং দ্য স্ট্রিট প্রেসার।’
এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার—শহরের নিয়ন্ত্রণ এখন শুধু প্রশাসনিক নয়, মনস্তাত্ত্বিকও। রাজধানী ঢাকাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক হৃদস্পন্দন। যে দল বা শক্তি ঢাকার রাস্তায় তাদের উপস্থিতি দেখাতে পারে, তাকে সাধারণ মানুষও রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারাবাহিকতার সম্ভাব্য দাবিদার হিসেবে দেখে। তাই নিষিদ্ধ দলটির জন্য ঝটিকা মিছিল এখন একটি প্রতীকী ‘টেরিটরি ক্লেইম’। আর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পদক্ষেপ হলো সেই প্রতীকী দাবি থামিয়ে দেওয়া, যেন পরিস্থিতি বড় ধরনের সংঘর্ষ বা বিশৃঙ্খলায় রূপ না নেয়।
কাউন্টার টেররিজম ইউনিটসহ নানা বিশেষায়িত পুলিশ শাখার যুক্ত হওয়া দেখায়, রাষ্ট্র এই ঘটনাকে কেবল সাধারণ রাজনৈতিক মিছিল হিসেবে দেখছে না। কারণ এই ধরনের দ্রুত সংগঠিত মিছিল এবং আকস্মিক বিস্ফোরণ কৌশল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ‘লিডারশিপ-লেস এ্যাকটিভিজম’ বা ‘মাইক্রো-মবিলাইজেশন’ এর অংশ হিসেবে পরিচিত। এতে নেতৃত্ব প্রকাশ্যে থাকে না, কিন্তু অংশগ্রহণকারীরা নির্দেশনা অনুযায়ী সক্রিয় থাকে। এতে সংগঠনকে ধরা কঠিন হয়। তাই পুলিশ বলছে, তাদের নজর শুধুই মাঠের কর্মীদের দিকে নয়, বরং আর্থিক সহায়তাকারী, পরিকল্পনাকারী এবং আহ্বায়ক কাঠামোর দিকে। অর্থাৎ যে স্তরে রাজনৈতিক সংগঠন আবার ভিত গড়তে পারে, সেই স্তরটিকেই তারা টার্গেট করছে।
অন্যদিকে, যে সকল নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যও রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথের কিছু ইঙ্গিত বহন করে। অনেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন, অনেকেই ভাড়া করা ছাত্রীবাস বা বাসায় অবস্থান করে হঠাৎ মিছিলের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। এটা প্রমাণ করে যে দলটি এখনও নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ধরে রেখেছে। যদিও প্রকাশ্যে সভা-সমাবেশের অনুমতি নেই, কিন্তু বিকল্প পদ্ধতিতে উপস্থিতি জানানোর চেষ্টা চলছে।
এই পরিস্থিতিতে রাজধানীর নাগরিক জীবনে একটি অদৃশ্য চাপ তৈরি হয়েছে। সকালবেলা বা কর্মঘণ্টায় মানুষ বের হলে আর নিশ্চিত থাকতে পারে না যে কোন মোড়ে হঠাৎ স্লোগান, পুলিশি ধাওয়া বা বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসবে কি না। শহরের মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ অস্থির থাকলে মানুষ অর্থনীতি, ব্যবসা, শিক্ষা বা কর্মে স্থিরতা খুঁজে পায় না। রাজনৈতিক বার্তা তাই শুধু রাজনৈতিক নয়—এটি অর্থনৈতিক এবং সামাজিকও।
পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গ্রেপ্তারগুলো গণগ্রেপ্তার নয়, বরং হাতেনাতে ধরা পড়া পরিস্থিতিভিত্তিক ব্যবস্থা। তবে যেভাবে গত দশ মাসে সংখ্যাটি তিন হাজার ছাড়িয়েছে, তা দেখায় যে রাজনৈতিক ঝটিকা উপস্থিতির জবাবও হচ্ছে ধারাবাহিক এবং কেন্দ্রীভূত। ভবিষ্যতেও এই ধারা চলতে পারে—বিশেষ করে যদি রাস্তায় ক্ষমতার প্রতীকী প্রতিযোগিতা তীব্র হয়।
রাজনীতিতে কখনো কখনো সরাসরি লড়াইয়ের চেয়ে উপস্থিতির বার্তা বেশি কার্যকর হয়। পোস্টার নয়, দেয়ালে লেখা নয়, মাঠে বড় সমাবেশ নয়—কেবল মুহূর্তের জন্য হলেও রাস্তায় দাঁড়ানো, স্লোগান দেওয়া এবং তা ক্যামেরায় ধরা পড়া। এই যুগে রাজনীতি অনেকটাই দৃশ্যমানতা এবং মিডিয়া প্রভাব-নির্ভর। তাই এই ঝটিকা মিছিলগুলো প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ভাষার এক পরিবর্তিত রূপ।
এই পরিবর্তিত ভাষা বুঝতে ব্যর্থ হলে পরিস্থিতি কেবল আইন-শৃঙ্খলা সমস্যা বা সংঘর্ষ হিসেবেই সামনে আসবে। বাস্তবে এটি রাজনীতির ক্ষমতা-প্রতিযোগিতা, টিকে থাকা, বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া এবং ভবিষ্যৎ ভূমিরেখা তৈরি করার এক চলমান প্রক্রিয়া।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ তাই শুধু সংসদ ভবন বা দলের কার্যালয়ে নির্ধারিত হচ্ছে না; নির্ধারিত হচ্ছে রাস্তায়, মোড়ে, মুহূর্তের ভিড়ে, মোবাইল ক্যামেরার ফ্রেমে—আর সেই মুহূর্তগুলোকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে উভয় পক্ষ।
এখন প্রশ্ন শুধু গ্রেপ্তারের নয়—প্রশ্ন হলো এই পাল্লা কোন দিকে ঝুঁকবে, কে রাজধানীর মানসিক ও সাংগঠনিক দখল রাখবে, এবং নাগরিকরা কখন আবার স্বাভাবিক দিনগুলোর স্থিরতা ফিরে পাবে।


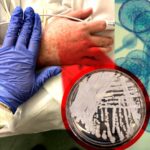


আপনার মতামত জানানঃ