
বাংলাদেশের কর্মসংস্থান সংকট আজ শুধু অর্থনৈতিক নয়, গভীরভাবে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক এক সংকটের রূপ নিয়েছে। এই সংকটের শেকড় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায়, যা প্রায় দুই শতাব্দী আগে ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়েছিল মূলত ব্রিটিশ শাসকের স্বার্থে। উদ্দেশ্য ছিল এমন এক শিক্ষিত শ্রেণি তৈরি করা, যারা বিদ্যা অর্জনের চেয়ে বেশি মনোযোগ দেবে শাসকের দপ্তরে চাকরি করার জন্য প্রস্তুত হতে। স্বাধীনতার এত বছর পরও আমরা সেই মানসিক কাঠামো থেকে বের হতে পারিনি। আজও আমাদের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হয়ে আছে সরকারি চাকরি—একটি ‘সোনার হরিণ’—যা শুধু অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নয়, সামাজিক মর্যাদারও নিশ্চয়তা দেয়।
শৈশব থেকেই আমাদের পাঠ্যবই, গল্প ও সামাজিক বয়ানে এমন একটি শ্রেণিচেতনা গড়ে তোলা হয় যেখানে ধনী হওয়া এবং শিক্ষিত হওয়া একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দেখা হয়। দরিদ্রদের মেধা বা সততা ব্যতিক্রম হিসেবে চিত্রিত হয়, যেন সেটা অস্বাভাবিক কিছু। শিশুতোষ গল্পে জয়ী চরিত্রকেই বীর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, আর পরাজিত চরিত্র স্বাভাবিকভাবেই খলনায়ক হয়ে যায়। এই মানসিকতা বড় হয়ে জীবনের পেশা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে—শিক্ষা যেন কেবল আর্থিক ও সামাজিক উত্থানের সিঁড়ি, জ্ঞানার্জনের জন্য নয়।
১৮৩৫ সালে থমাস ম্যাকওলে তার কুখ্যাত “মিনিট অন ইন্ডিয়ান এডুকেশন”-এ ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চাপিয়ে দেন। এতে ইংরেজি জানা মানেই সরকারি চাকরির যোগ্যতা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, চাকরি ও শিক্ষার মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা পরবর্তী প্রজন্মেও প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি উপনিবেশ শেষ হওয়ার ৮০ বছর পরও এই চাকরি-প্রার্থী মনোভাব আমাদের সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত।
বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা আজ সমগ্র একাডেমিক জ্ঞানকে প্রায় একপাশে সরিয়ে দিয়ে সরকারি চাকরির প্রস্তুতিকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়ে ফেলেছে। এর পেছনে প্রধান কারণ শুধু আর্থিক নিশ্চয়তা নয়, বরং সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা। উপনিবেশকালে ব্রিটিশ দপ্তরে লেখক বা এমনকি চাপরাশি হওয়াও ছিল একধরনের গর্বের বিষয়, কারণ এতে সমাজের চোখে এক ধাপ উঁচুতে ওঠা যেত। সেই মনস্তত্ত্ব আজও পরিবর্তিত হয়নি, বরং প্রতিযোগিতা যত বেড়েছে, ততই গভীর হয়েছে।
কিন্তু এই পরিস্থিতি শুধু শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পছন্দের ফল নয়। এর জন্য সমানভাবে দায়ী রাষ্ট্রের কর্মসংস্থান নীতি ও শিক্ষানীতি। বাজারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমন্বয় করা যায়নি। ফলে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। আশির দশকের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা চাকরির বাজারকে অকার্যকর করে তোলে। মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে বহুজাতিক কোম্পানির দাপট এবং বেসরকারিকরণ একদিকে চাকরির সুযোগ বাড়ালেও, অন্যদিকে নিরাপত্তাহীনতা ও শোষণ বাড়িয়েছে। এই বাস্তবতায় তরুণরা আবার সরকারি চাকরির নিরাপত্তার দিকে ঝুঁকেছে।
জুলাই ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান মূলত কোটা সংস্কারের দাবিকে কেন্দ্র করে হলেও, এর গভীরে ছিল কর্মসংস্থান ও শিক্ষাব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী সংকটের প্রতিবাদ। অথচ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও উচ্চশিক্ষার সংকট মোকাবেলায় কোনো কমিশন গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেনি। এটি হতে পারত অভ্যুত্থানের অন্যতম বড় অর্জন, কিন্তু তা হয়নি। ফলে, শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের সুযোগ আবার হাতছাড়া হলো।
বাংলাদেশের কর্মসংস্থান সংকট সমাধান করতে হলে প্রথমেই স্বীকার করতে হবে যে এর মূল শিকড় শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরে। ঔপনিবেশিক মানসিকতার সেই কাঠামো ভেঙে দিয়ে শিক্ষাকে শুধুমাত্র চাকরির প্রশিক্ষণ হিসেবে নয়, বরং জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশের মাধ্যমে বহুমুখী কর্মসংস্থানের পথ তৈরির মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আর এর জন্য উচ্চশিক্ষা কমিশনের মতো একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান এখন সময়ের দাবি। নইলে এই সংকট শুধু স্থায়ী হবে না, বরং আগামী প্রজন্মকে আরও গভীর হতাশার দিকে ঠেলে দেবে।

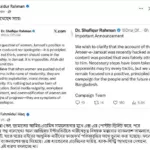




আপনার মতামত জানানঃ