 চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ক্রেন, সারি সারি কনটেইনার আর পণ্যভরা জাহাজ বাংলাদেশের অর্থনীতির ধুকপুক হৃদয়ের প্রতীক। এই বন্দর দিয়েই দেশের আমদানি–রপ্তানির বড় অংশ সম্পন্ন হয়, লাখ লাখ মানুষের জীবিকা জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। ঠিক এই জায়গাটিই এখন নতুন এক বিতর্কের কেন্দ্রে—চট্টগ্রামের লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল এবং ঢাকার কাছে পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনালের দায়িত্ব দীর্ঘমেয়াদে বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে দেশজুড়ে প্রশ্ন, উদ্বেগ আর মতবিরোধ তীব্র আকার নিয়েছে।
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ক্রেন, সারি সারি কনটেইনার আর পণ্যভরা জাহাজ বাংলাদেশের অর্থনীতির ধুকপুক হৃদয়ের প্রতীক। এই বন্দর দিয়েই দেশের আমদানি–রপ্তানির বড় অংশ সম্পন্ন হয়, লাখ লাখ মানুষের জীবিকা জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। ঠিক এই জায়গাটিই এখন নতুন এক বিতর্কের কেন্দ্রে—চট্টগ্রামের লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল এবং ঢাকার কাছে পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনালের দায়িত্ব দীর্ঘমেয়াদে বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে দেশজুড়ে প্রশ্ন, উদ্বেগ আর মতবিরোধ তীব্র আকার নিয়েছে।
অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে থাকা বাংলাদেশ এমন এক সময় এই চুক্তি করেছে, যখন তাদের ম্যান্ডেটের ব্যাপ্তি ও সীমারেখা নিয়েই জনমনে আলোচনা চলছে। অন্তর্বর্তী সরকার দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকবে না—এ ধারণা থেকেই অনেকেই জানতে চাইছেন, ত্রিশ বছর ও বাইশ বছরের মতো দীর্ঘ মেয়াদি বন্দর ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার নৈতিক ও রাজনৈতিক দায় তারা কীভাবে নিলেন। চুক্তি অনুযায়ী, ডেনমার্কভিত্তিক এপিএম টার্মিনালস লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পাবে ৩০ বছরের জন্য, আর সুইজারল্যান্ডভিত্তিক মেডলগ পাবে পানগাঁও টার্মিনাল পরিচালনার কাজ ২২ বছরের জন্য। অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে থাকা সীমিত সময়ের মধ্যে এত দীর্ঘ মেয়াদি ও কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়াকে অনেকে ‘তাড়াহুড়োর আয়োজন’ হিসেবে দেখছেন, আবার আরেক পক্ষ এটিকে সাহসী ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত বলেও তুলে ধরছেন।
গণঅধিকার কমিটির সদস্য অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে। তাঁর যুক্তি, যে সরকার কয়েকদিন পর আর ক্ষমতায় থাকবে না, তারা যদি এমন স্পর্শকাতর ও দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করে, ভবিষ্যতে কোনো জটিলতা তৈরি হলে তার জবাবদিহি করবে কে? বন্দর, সমুদ্রসীমা বা কৌশলগত অবকাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো সাধারণত নির্বাচিত সরকারের রাজনৈতিক জবাবদিহির কাঠামোর ভেতরে হয়; অন্তর্বর্তী কাঠামো সেখানে কতটা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার রাখে, এটাও একটি নৈতিক প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। বিপরীতে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম ঠিক উল্টো জায়গা থেকে যুক্তি দিয়েছেন—তার মতে, অনেক সময় নির্বাচিত সরকার রাজনৈতিক চাপ, স্বার্থজড়িত গোষ্ঠীর প্রভাব এবং নির্বাচনী রাজনীতির কারণে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, সেখানে অন্তর্বর্তী সরকারের ‘রাজনৈতিক বোঝা’ তুলনামূলক কম থাকায় তারা দ্রুত ও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে।
বাংলাদেশের বন্দর ব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিযোগ নতুন কিছু নয়। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়ীরা বলে আসছেন, চট্টগ্রাম বন্দরে দুর্নীতি, ধীরগতি, দীর্ঘ ওয়েটিং টাইম, অদক্ষ কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কারণে দেশের বাণিজ্য ব্যয় বাড়ছে, প্রতিযোগিতা ক্ষমতা কমছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও এসব সমস্যার সমাধান হিসেবে বিদেশি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ, টার্মিনাল ব্যবস্থাপনায় বিদেশি অপারেটর আনার প্রস্তাব ওঠে। ২০২৩ সালে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনালের দায়িত্ব সৌদি আরবের একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যার পরপরই ‘বন্দর বিদেশিদের হাতে চলে যাচ্ছে’, ‘জাতীয় সম্পদ বিক্রি হচ্ছে’—এমন শ্লোগানে রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজের একাংশ প্রতিবাদে নামেন। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনা নিয়েও দুবাইভিত্তিক কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েনের মধ্যে আটকে ছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় আবার তাতে গতি এসেছে। এক পর্যায়ে দেশের অন্তত পাঁচটি টার্মিনালের কনটেইনার হ্যান্ডলিং বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা সামনে আসে, যা বন্দর ব্যবহারকারী সংগঠনসমূহের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
এই প্রেক্ষাপটে লালদিয়া ও পানগাঁও–সংক্রান্ত নতুন চুক্তি যেন আগুনের ওপর আরও ঘি ঢেলে দিল। চট্টগ্রাম কাস্টমস এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, কিছু রাজনৈতিক সংগঠন ও পেশাজীবী মহল খুব কম সময়ের মধ্যে চুক্তি সই হওয়া এবং এর স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাদের বক্তব্য, এ ধরনের জটিল ও বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ ও পরিচালন-সম্পর্কিত চুক্তির ক্ষেত্রে বিস্তারিত প্রস্তাব মূল্যায়ন, দরকষাকষি, বিভিন্ন স্তরে অনুমোদন—এসব প্রক্রিয়া সাধারণত সময় সাপেক্ষ, অথচ এখানে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব শেষ করে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় কিছু গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, এপিএম টার্মিনালস মাত্র কয়েক দিন আগে কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব জমা দেওয়ার পর এত দ্রুত চুক্তি সই হওয়ায় ‘তাড়াহুড়ো’ নিয়ে আশঙ্কা আরও বেড়েছে।
কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে যে ছবি আঁকা হচ্ছে, তা অন্য রকম। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে পুরো বিষয়টিকে ‘শিল্প রূপান্তরের ভিত্তি’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার যুক্তি, ডেনমার্কের এপি মোলার-মেয়ার্স্ক গ্রুপের অংশ এপিএম টার্মিনালস বিশ্বের শীর্ষ কয়েকটি বন্দর পরিচালনা করছে, ইউরোপ থেকে শুরু করে এশিয়ার একাধিক দেশে তাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলে এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থায়নে লালদিয়া চরে নতুন টার্মিনাল নির্মাণ, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের জন্য একদিকে বড় ধরনের বৈদেশিক বিনিয়োগ, অন্যদিকে বন্দর দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করবে। তিনি জানাচ্ছেন, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে প্রায় ৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ করবে প্রতিষ্ঠানটি, আর প্রতিটি হ্যান্ডল হওয়া কনটেইনারের জন্য নির্দিষ্ট ফি পাবে বাংলাদেশ। তার মতে, ভলিউম বাড়লে দেশের আয়ের অঙ্কও বাড়বে এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ রেগুলেটর হিসেবে নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকায় থাকবে।
এখানেই এসে দাঁড়ায় ‘স্বচ্ছতা বনাম গোপনীয়তা’র প্রশ্ন। এই চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে নন–ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (এনডিএ) থাকায় পূর্ণাঙ্গ দলিল বা বিস্তারিত শর্তাবলি প্রকাশ করা যাবে না—এমন বক্তব্য এসেছে সরকারি পক্ষ থেকে। বিডা চেয়ারম্যানের যুক্তি, সরকারি ক্রয়নীতি ও পিপিপি গাইডলাইন অনুযায়ী কিছু তথ্য গোপন রাখতে হয়, বিশেষ করে বেসরকারি অংশীদারের বাণিজ্যিক গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে। তিনি এমন দাবিও করেছেন, পৃথিবীর কোনো দেশই সাধারণত এ ধরনের পিপিপি চুক্তির পুরো দলিল জনসমক্ষে প্রকাশ করে না। কিন্তু সমালোচকদের পাল্টা প্রশ্ন, বন্দর–সংক্রান্ত চুক্তির মতো জনস্বার্থ–সম্পৃক্ত বিষয়ে অন্তত নীতিগত কাঠামো, আয়ের ভাগাভাগি, ঝুঁকি বণ্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার কতটা কার হাতে থাকবে—এসব মৌলিক তথ্য জনগণের জানার অধিকার থেকে বাদ যায় কীভাবে? আরও বড় প্রশ্ন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট চুক্তিকে গোপনীয়তার মোড়কে ঢেকে রাখলে ভবিষ্যতে জবাবদিহির জায়গা কোথায় থাকবে?
বিডা চেয়ারম্যান যেমন সমালোচনাকে ব্যাখ্যা করছেন, তাতে তিনি একটি রাজনৈতিক মাত্রাও টেনে আনছেন। তার মতে, যারা এতদিন বন্দর–সংক্রান্ত দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি থেকে সুবিধা পেয়েছেন, তারাই এখন ‘দেশ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে’ ধরনের স্লোগান তুলে নিজেদের অবস্থান রক্ষা করতে চাইছেন। অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে, পরিবর্তন বিরোধীদের একটি অংশ আসলে পুরনো স্বার্থেরই রক্ষক। অন্যদিকে, সমালোচকরা মনে করেন, দেশের সক্ষমতা গড়ে তোলার বদলে সব দায় ‘অদক্ষতা’ বা ‘দুর্নীতি’ শব্দের আড়ালে রেখে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়াটা সহজ পথ বেছে নেওয়ার সমান। আনু মুহাম্মদের মত হলো, দেশের বন্দর ব্যবস্থাপনার সমস্যা কোথায়, কারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, কীভাবে সিস্টেম ঠিক করা যায়—এসব নিয়ে আন্তরিক পদক্ষেপের বদলে সরাসরি বিদেশি অপারেটরের হাতে হস্তান্তর দীর্ঘমেয়াদে দেশের নিয়ন্ত্রণক্ষমতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে।
আন্তর্জাতিক উদাহরণ টেনে সমালোচনার মাত্রা আরও তীব্র করা হচ্ছে। জিবুতি কিংবা শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলোতে বন্দর ও অবকাঠামো প্রকল্পে বিদেশি কোম্পানির আধিপত্য এবং ঋণজালে জড়িয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা অনেকের কাছেই সতর্কতা হিসেবে দেখা হয়। যদিও বাংলাদেশের বর্তমান চুক্তিগুলো সেই একই ধাঁচের কি না, সেটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, তবু সমালোচকেরা সতর্ক করে দিচ্ছেন—আজকের লাভের হিসাবের আড়ালে যেন আগামী দিনের ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি ঢেকে না যায়। কারণ বন্দর শুধু অর্থনীতির নয়, কৌশলগত নিরাপত্তারও অংশ; এখানে ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল।
তবে বাস্তবতা হলো, চট্টগ্রাম বন্দর বিশ্বব্যস্ততম বন্দরের সারিতে উপরে উঠলেও, সেবা ও দক্ষতার মান সবসময় প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। বছরের পর বছর ধরে ব্যবসায়ীরা ‘মডার্নাইজেশন’ আর ‘অটোমেশন’র কথা বলছেন, অথচ বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে খুব ধীরে। দীর্ঘ ওয়েটিং টাইম, জাহাজের ভিড়, কনটেইনার সরানোর ধীরগতি—সব মিলিয়ে আমদানি–রপ্তানির খরচ ও সময় দুই-ই বেড়েছে। এ অবস্থায় সরকারের যুক্তি, অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক অপারেটররা উন্নত প্রযুক্তি, দ্রুত সেবাপ্রদান ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এনে পরিস্থিতি বদলে দিতে পারবে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমও এটিকে ‘এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ইউরোপীয় বিনিয়োগ’ এবং ‘শিল্প রূপান্তরের ভিত্তি’ হিসেবে তুলে ধরে জনগণকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন।
তবুও বিতর্ক থেমে নেই, বরং প্রশ্ন আরও বেড়েছে—এই মডেল কি বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি বন্দর নীতির অংশ, নাকি অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে করা কিছু বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত? যদি এটি বৃহত্তর নীতির অংশ হয়, তাহলে তার রূপরেখা কোথায়? দেশের নিজস্ব সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা কী? বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রযুক্তি, জনবল, ব্যবস্থাপনা—সব মিলিয়ে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী না করে শুধুই বিদেশি অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কি টেকসই সমাধান?
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে জনগণের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা। চট্টগ্রাম ও পানগাঁও–সংক্রান্ত চুক্তিগুলো কীভাবে করা হলো, কতজন বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন বা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির মতামত নেওয়া হলো, এসব প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব এখনো সামনে আসেনি। যারা বন্দর ব্যবহার করেন—শিপিং এজেন্ট, কাস্টমস এজেন্ট, এক্সপোর্টার–ইম্পোর্টার—তাদের একটা অংশ নিজেকে সিদ্ধান্ত–প্রক্রিয়ার বাইরে মনে করছেন। এতে করে নতুন নীতি শুরু হওয়ার আগেই অবিশ্বাসের একটি দেয়াল তৈরি হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে নীতি বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
অবশেষে প্রশ্নটা এসে দাঁড়ায় ভারসাম্যের জায়গায়। একদিকে আধুনিকায়ন, বিদেশি বিনিয়োগ, দক্ষ ব্যবস্থাপনা—অন্যদিকে জাতীয় স্বার্থ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা। লালদিয়া ও পানগাঁও–এর চুক্তিগুলো নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, সেগুলো কেবল দুটি টার্মিনালকে ঘিরে নয়; বরং বাংলাদেশের বন্দর নীতি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের ওপর জনস্বার্থের অধিকার—এই বৃহত্তর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। অন্তর্বর্তী সরকার হয়তো যুক্তি দেখাতে পারে, তারা সময় নষ্ট না করে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে; সমালোচকেরা বলবেন, ঠিক সেই ‘দ্রুততা’র ভেতরেই গোপন রয়েছে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সংকটের বীজ।
বাংলাদেশ ঠিক কোন পথে হাঁটবে—পুরোটাই কি আন্তর্জাতিক অপারেটরের হাতে, নাকি শক্তিশালী সুশাসনের মাধ্যমে নিজস্ব বন্দর ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও দক্ষ করে তোলার পথে—এর উত্তর এখনই স্পষ্ট নয়। তবে লালদিয়া ও পানগাঁও নিয়ে তৈরি হওয়া এই বিতর্ক অন্তত একটি কথা পরিষ্কার করে দিয়েছে: বন্দর আর শুধু কনটেইনার ওঠানামার জায়গা নয়, এটি এখন জাতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূরাজনীতি ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহির মিলনস্থল। এখানে নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি শুধু কর্ণফুলীর মোহনায় নয়, দেশের সামগ্রিক ভবিষ্যতের ওপরও পড়ে যাবে—একটি চুক্তি, একটি টার্মিনাল, কিংবা একটি সরকারের মেয়াদ ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত।


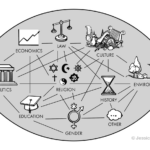



আপনার মতামত জানানঃ