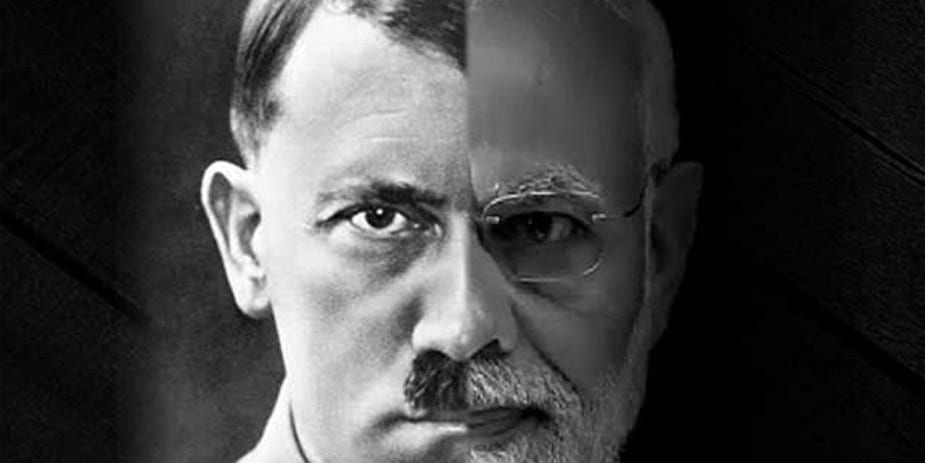 ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রতিক এক প্রবণতা এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যা কেবল আইন ও প্রশাসনের প্রশ্ন নয়, বরং ক্ষমতা, ভয়, পরিচয় এবং রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের নতুন এক কাঠামোকে সামনে এনেছে। প্রবণতাটির নাম—‘বুলডোজার রাজনীতি’। একটি সাধারণ নির্মাণযন্ত্রকে রাজনৈতিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে অভিযুক্ত ব্যক্তি, বিক্ষোভকারী কিংবা সরকারের সমালোচকদের বাড়িঘর ভাঙা এখন অনেক রাজ্যে এক ভয়ংকর বাস্তবতা। বিষয়টি নিছক আইন প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি বিচারবহির্ভূত শাস্তি দেওয়ার এক ধরনের প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে। বিশেষত আদালতের রায়, তদন্ত বা প্রমাণ হাজিরের আগেই এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালানো প্রশাসনের নিজস্ব শক্তিমত্তার এক নির্মম বার্তা বহন করে। আইন, মানবাধিকার এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ওপর এর প্রভাব এতটাই গভীর যে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যত নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রতিক এক প্রবণতা এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যা কেবল আইন ও প্রশাসনের প্রশ্ন নয়, বরং ক্ষমতা, ভয়, পরিচয় এবং রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের নতুন এক কাঠামোকে সামনে এনেছে। প্রবণতাটির নাম—‘বুলডোজার রাজনীতি’। একটি সাধারণ নির্মাণযন্ত্রকে রাজনৈতিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে অভিযুক্ত ব্যক্তি, বিক্ষোভকারী কিংবা সরকারের সমালোচকদের বাড়িঘর ভাঙা এখন অনেক রাজ্যে এক ভয়ংকর বাস্তবতা। বিষয়টি নিছক আইন প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি বিচারবহির্ভূত শাস্তি দেওয়ার এক ধরনের প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে। বিশেষত আদালতের রায়, তদন্ত বা প্রমাণ হাজিরের আগেই এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালানো প্রশাসনের নিজস্ব শক্তিমত্তার এক নির্মম বার্তা বহন করে। আইন, মানবাধিকার এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ওপর এর প্রভাব এতটাই গভীর যে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যত নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
এই বুলডোজার রাজনীতির উত্থান রাতারাতি হয়নি। এর পেছনে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক পরিকল্পনা, জনমতের গতিপ্রবাহ, সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং শাস্তি–প্রদর্শনের সাংস্কৃতিক রূপায়ণ কাজ করেছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই প্রবণতাকে জনপ্রিয়তা ও বৈধতার পর্যায়ে নিয়ে যেতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখেন। গণমাধ্যমে যিনি ‘বুলডোজার বাবা’ নামে পরিচিতি পান, তিনি প্রথমে তাঁর রাজ্যে কুখ্যাত অপরাধী বা মাফিয়াদের বাড়িঘর ভাঙার মাধ্যমে নিজেকে ‘কঠোর প্রশাসক’ হিসেবে তুলে ধরেন। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা যায়, এই নীতির প্রয়োগ অপরাধী দমনের গণ্ডি ছাড়িয়ে সরকারের সমালোচক, বিক্ষোভকারী এবং বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। রাজনৈতিক সমাবেশে খেলনা বুলডোজার নিয়ে উৎসবমুখর সমর্থকদের উপস্থিতি প্রমাণ করে, এটি কতটা সফল নির্বাচনী কৌশলে পরিণত হয়েছে। উত্তর প্রদেশের পর বিজেপিশাসিত অন্যান্য রাজ্য—মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, গুজরাট, হরিয়ানা—এই মডেল অনুসরণ করতে শুরু করে এবং অনেক ক্ষেত্রে দাঙ্গা বা বিক্ষোভের পরেই মুসলিমদের বাড়িঘর ভাঙা হয় ‘প্রশাসনিক পদক্ষেপ’ হিসেবে।
বিভিন্ন বিশ্লেষকের মতে, ভারতের এই নীতি কিছুটা হলেও অনুপ্রাণিত ইসরায়েলের ব্যবহৃত কৌশল থেকে, যেখানে ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে বহু বছর ধরে বাড়িঘর ধ্বংস করার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। ব্রিটিশ ম্যান্ডেট যুগে শুরু হলেও ইসরায়েল এই পদ্ধতিকে রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত করে এবং ‘হাফরাদা’ বা বিচ্ছিন্নতার নীতির অধীনে হাজার হাজার ফিলিস্তিনির ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলে। এর উদ্দেশ্য ছিল জনসংখ্যাকে নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখা, ভয় সৃষ্টি করা এবং মধ্যবিত্ত ফিলিস্তিনিদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা। ভারতের ক্ষেত্রে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এটি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ বলে স্বীকার না করলেও ঘটনাগুলোর সময় ও ধরন স্পষ্ট করে দেয় যে এটি ‘সতর্কবার্তা’ নয়, বরং বিচারবহির্ভূত শাস্তি প্রদানেরই একটি রূপ।
ভারতে বুলডোজার অভিযানগুলো সাধারণত কোনো বিক্ষোভ, দাঙ্গা, বা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার ঠিক পরপরই চালানো হয়। অর্থাৎ এটি প্রশাসনিক পদক্ষেপের চেয়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার মতো আচরণ করে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অভিযোগ অনুযায়ী, মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি এই ধ্বংসযজ্ঞের হার আশঙ্কাজনকভাবে বেশি। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য মতে, ২০২২ সালের কয়েক মাসেই কমপক্ষে ১২৮টি সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে, যার ফলে শত শত মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। বহু ক্ষেত্রে বাড়ি ভাঙার আগেই নোটিশ দেওয়া হয়নি, কিংবা দেওয়া হলেও সময় ছিল অত্যন্ত অল্প। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রমাণ বা আদালতের অনুমতি ছাড়াই ‘অবৈধ নির্মাণ’ বা ‘অপরাধীর বাড়ি’—এমন অজুহাতে অভিযান চালানো হয়। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই প্রক্রিয়াকে স্পষ্টভাবে আইনবহির্ভূত বলে অভিহিত করেছে, কারণ প্রশাসনের কাজ বিচার করা নয়। কিন্তু সরকারের একটি অংশ এবং ক্ষমতাসীন দলের অনেক নেতা-বক্তা এটিকে অপরাধ দমনে ‘দৃঢ় বার্তা’ হিসেবে উপস্থাপন করতে থাকে।
এই নীতির সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো এর সামাজিক প্রভাব। যখন রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ব্যবহার করে একটি জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়, তখন মানুষের মনে ভীতি ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। বাড়ি ভাঙা মানে শুধু একটি কাঠামো ধ্বংস করা নয়, বরং স্মৃতি, পরিচয়, নিরাপত্তার বোধ, এবং আর্থিক স্থিতিশীলতাকে এক মুহূর্তে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য এটি এমন ধাক্কা, যা থেকে উত্তরণ প্রায় অসম্ভব। একেকটি বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বহু বছরের সঞ্চয়, পরিশ্রম, আবেগ এবং সামাজিক অবস্থান; বুলডোজারের এক ধাক্কায় সেসব ভস্মীভূত হয়। এ কারণেই বুলডোজার রাজনীতিকে শুধু প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক বিতর্কে সীমাবদ্ধ রেখে বোঝা যায় না; এটি মানবিক বিপর্যয়ের এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।
এই ধ্বংসযজ্ঞের একটি সাংস্কৃতিক দিকও রয়েছে। ‘হিন্দুত্ব পপ’ বা ‘H-pop’ নামে ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়া গানগুলোতে বুলডোজারকে সুপারহিরোর মতো উপস্থাপন করা হয়। রঙিন ভিডিও, চটকদার সঙ্গীত, ছন্দময় বিট এবং উল্লাসপূর্ণ নাচের দৃশ্যে বুলডোজারকে পরিণত করা হয় এক ধরনের ন্যায্য প্রতিশোধের প্রতীকে। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্ম নেয় এক অদ্ভুত উল্লাস—যা অন্য সম্প্রদায়ের দুর্ভোগকে আনন্দের উৎসবে রূপান্তরিত করে। “বুলডোজার ওয়ালে বাবা” বা “জিত গায়া বাবা বুলডোজার ওয়ালা” ধরনের ট্র্যাকগুলো যোগী আদিত্যনাথকে ‘রক্ষক’ হিসেবে তুলে ধরে, যেন তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিচার করছেন। বাস্তবতা হচ্ছে, এসব কনটেন্ট রাষ্ট্রীয় সহিংসতাকে বিনোদনের উপাদানে পরিণত করে, এবং অসহায়ের ওপর বলপ্রয়োগকে বৈধতা দেয়। এই সাংস্কৃতিক রূপায়ণই বুলডোজার রাজনীতিকে কেবল নীতি নয়, বরং একটি আবেগময় অভিজ্ঞতায় পরিণত করেছে।
তবে এই নীতির বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তীব্র সমালোচনা উঠেছে। সাবেক বিচারপতি, আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মীরা এটিকে ‘আইনের শাসনের অবমাননা’ ও ‘সম্মিলিত শাস্তির নীতি’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। ২০২৪ সালের নভেম্বরে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক রায় দিয়ে বুলডোজার অভিযানকে স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনি ঘোষণা করে। আদালত স্পষ্ট করে জানায়, সম্পত্তি ধ্বংস করা কোনোভাবেই প্রশাসনের কাজ নয়; যথাযথ তদন্ত, বিচারিক প্রক্রিয়া এবং আদালতের রায় ছাড়া এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ সংবিধানবিরোধী। যদিও রাজ্য সরকারগুলো রায়কে স্বাগত জানায় বলে জানায়, বাস্তবে পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন হয়নি।
বুলডোজারের ব্যবহার এতটাই সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে যে ব্রিটিশ কোম্পানি JCB—যা মূলত এসব যন্ত্র তৈরি করে—ভারতীয় জনমনে প্রতীকী অর্থ অর্জন করেছে। ক্ষমতাসীন দলের এক মুখপাত্র এটিকে ব্যঙ্গ করে ‘জিহাদি কন্ট্রোল বোর্ড’ বলেও উল্লেখ করেছেন। মানবাধিকার সংস্থার অভিযোগে জেসিবিকে এই ব্যবহারের দায়বদ্ধতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। কোম্পানি অবশ্য জানিয়েছে, তারা ডিলারদের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে এবং ব্যবহারের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু করপোরেট নৈতিকতা ও মানবাধিকার প্রশ্নে এই অবস্থান কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।
বুলডোজার রাজনীতির উত্থান শেষ পর্যন্ত এক বৃহত্তর গল্প বলে—রাষ্ট্র যখন আইনকে পাশ কাটিয়ে বিচারবহির্ভূত শাস্তিকে জনপ্রিয় করে তোলে, তখন গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের আনন্দ, অন্যদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভীতি—এই দ্বৈত বাস্তবতা ভারতীয় সমাজে গভীর বিভাজন তৈরি করছে। আইন, ন্যায়বিচার ও নাগরিক অধিকারের যে কাঠামো ভারতের গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছিল, তা এখন বুলডোজারের শব্দে কেঁপে উঠছে। সর্বোচ্চ আদালতের কঠোর নির্দেশিকা সত্ত্বেও বাস্তবতার পরিবর্তন ধীর, এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক লাভের হিসাব মানবিক ক্ষতির চেয়েও প্রাধান্য পাচ্ছে। একটি দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কতটা টেকসই, তা বোঝা যায় তখনই, যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি কেমন আচরণ করে। ভারতের বুলডোজার রাজনীতি সেই পরীক্ষায় উদ্বেগজনক সংকেত দিচ্ছে—এটি কেবল কিছু বাড়িঘর ভেঙে ফেলার গল্প নয়, বরং সমগ্র বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনিক নীতি এবং সামাজিক সহাবস্থানের মূল কাঠামোকে নাড়িয়ে দেওয়ার গল্প। ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে রাষ্ট্র, আদালত এবং নাগরিক সমাজ কতটা শক্তভাবে দাঁড়াতে পারে এই স্বেচ্ছাচারী প্রবণতার বিরুদ্ধে।






আপনার মতামত জানানঃ