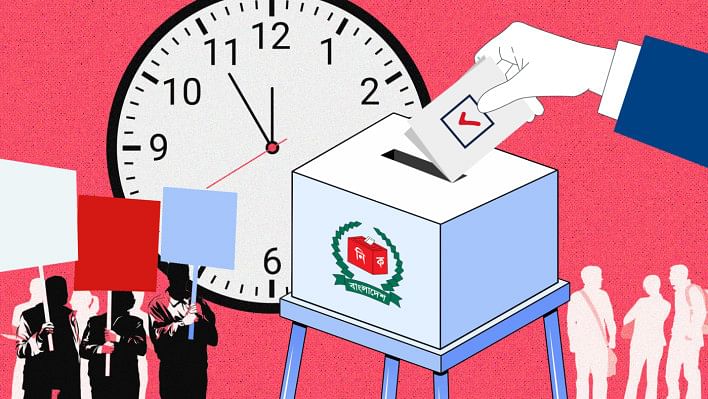
বাংলাদেশের রাজনীতি আবারও এক অনিশ্চয়তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েন, সহিংসতা, এবং জনগণের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ইতিহাসের মধ্য দিয়ে দেশ এবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। তবে এই নির্বাচন ঘিরে একাধিক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সরকার নির্বাহী আদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। অন্যদিকে একটি মহল জাতীয় পার্টিকেও স্বৈরশাসনের সহযোগী হিসেবে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলছে। প্রশ্ন এখন একটাই—যদি আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে থাকে, তবে তাদের কোটি কোটি সমর্থক ভোটার কী করবেন?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাস ও বর্তমান প্রেক্ষাপটের দিকে নজর দিতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশে যত নির্বাচন হয়েছে, তার মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন খুবই সীমিত। ১৯৯১ সালের নির্বাচন ছিল একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, যেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জনগণ অবাধে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু সেই ব্যবস্থাকেই পরবর্তীতে বাতিল করে দিয়ে ক্ষমতাসীন দল নিজেদের জন্য একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করেছে।
বর্তমান নির্বাচন কমিশন নানা সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে। ১৯৭২ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবের মধ্যে আছে সশস্ত্র বাহিনীকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে ব্যবহার, গুরুতর অনিয়মে পুরো আসনের নির্বাচন বাতিল, প্রার্থীর দেশি–বিদেশি সম্পদের হিসাব জমা দেওয়া, পলাতক আসামিদের অযোগ্য ঘোষণা ইত্যাদি। এগুলো কাগজে-কলমে সঠিক মনে হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আইন অনেক সময়ই ক্ষমতার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
‘না’ ভোট চালুর প্রস্তাব নিয়েও বিতর্ক আছে। নির্বাচন কমিশন বলেছে, একক প্রার্থীর ক্ষেত্রে ভোটারদের ‘না’ বলার সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু এর মাধ্যমে কি সত্যিই গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে, নাকি কেবল কারসাজির নতুন সুযোগ তৈরি হবে? ১৯৯৬ সালে বিএনপি এবং ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগের বিপুলসংখ্যক প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন যদি ‘না’ ভোট থাকত, নির্বাচনের গুণগত পার্থক্য হতো কি? বরং বিজয়ী দল দাবি করত, তারা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত। তাই এই বিধান চালুর আগে এর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিণতি ভেবে দেখা জরুরি।
প্রশ্ন হচ্ছে, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি ছাড়া একটি জাতীয় নির্বাচন কতটা অর্থবহ হবে? বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান দুটি ধারাই বহু বছর ধরে এই দুই দলের প্রভাবে গড়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া দল, আর জাতীয় পার্টি সামরিক শাসনের উত্তরাধিকার বহন করলেও দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জোটে ক্ষমতার অংশীদার। এই দুটি দলকে হঠাৎ নির্বাচন থেকে বাইরে রাখা হলে তাদের বিশাল ভোটারগোষ্ঠী বিভ্রান্ত ও হতাশ হয়ে পড়বে। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো ভোটারদের আস্থা। কিন্তু যখন তাদের প্রিয় দলকে মাঠে দেখা যাবে না, তখন সেই আস্থা ভেঙে পড়বে।
ইতিহাস প্রমাণ করে, বড় দলগুলিকে বাদ দিয়ে নির্বাচনের আয়োজন করলে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটকেন্দ্রে যায় না। ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিএনপি না থাকায় শত শত কেন্দ্রে ভোটারশূন্য অবস্থা ছিল। একইভাবে ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ না নেওয়ায় অংশগ্রহণ কমে গিয়েছিল। গণতন্ত্রের জন্য এই শূন্যতা ভয়ংকর। এবার যদি আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি উভয়ই বাইরে থাকে, তাহলে ভোটারদের সিংহভাগই কার্যত ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
ভোটারদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করাও জরুরি। বাংলাদেশের ভোটাররা সাধারণত দলভিত্তিক। তারা নিজেদের রাজনৈতিক পছন্দকে দলীয় প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করে। গ্রামীণ সমাজে রাজনৈতিক পরিচয় প্রায় পারিবারিক উত্তরাধিকারের মতো। এমন প্রেক্ষাপটে প্রিয় দলের প্রার্থী না থাকলে ভোটাররা হয় ভোট দিতেই আগ্রহী হবে না, নয়তো বিকল্প হিসেবে নিরপেক্ষ প্রার্থী খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হবে। এতে নির্বাচনী অংশগ্রহণ হ্রাস পাবে, যা গণতন্ত্রকে আরও দুর্বল করবে।
এখন প্রশ্ন ওঠে—তাহলে এই ভোটাররা কী করবেন? তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত, তারা ভোটকেন্দ্রে না গিয়ে নীরব প্রতিবাদ করবেন। দ্বিতীয়ত, তারা বিকল্প প্রার্থীকে ভোট দেবেন, যদিও সেটি তাদের কাছে তেমন অর্থবহ মনে হবে না। তৃতীয়ত, তারা সংগঠিত হয়ে নির্বাচন বর্জন বা প্রতিবাদে নামতে পারেন। তিনটি পরিস্থিতির যেকোনো একটি ঘটলেও এর রাজনৈতিক অভিঘাত মারাত্মক হতে পারে।
এদিকে নির্বাচন কমিশন বলছে, গরিষ্ঠসংখ্যক ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে আনা তাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ। কমিশনের একজন সদস্য বলেছেন, ভোটাররা নির্বাচনের প্রথম চোখ। কিন্তু ভোটারদের সেই চোখ যদি তাদের প্রিয় দলকে না দেখে অন্ধকার হয়ে যায়, তবে তারা ভোট দিতে আগ্রহী হবে না। জনগণ যদি ভোটাধিকার প্রয়োগ না করে, তাহলে নির্বাচন প্রক্রিয়াই প্রহসনে পরিণত হবে।
রাজনৈতিক দলগুলো সবসময় দাবি করে সুষ্ঠু নির্বাচন চায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তারা নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। একদিকে নির্বাহী আদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে, অন্যদিকে জাতীয় পার্টিকে নিয়েও সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। এ পরিস্থিতি ভোটারদের মনে প্রশ্ন জাগাচ্ছে—এটি কি সত্যিই একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন, নাকি নির্বাচনী প্রহসন?
বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো আস্থা সংকট। ভোটাররা যদি মনে করে তাদের ভোটে কিছু পরিবর্তন আসবে না, তবে তারা ভোট দিতে যাবে না। আর রাজনৈতিক দলগুলো যদি মনে করে কমিশন নিরপেক্ষ নয়, তবে তারা নির্বাচন বর্জন করবে। এই আস্থা সংকট দূর না হলে কোনো সংস্কারই কার্যকর হবে না।
আজকের পরিস্থিতিতে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। প্রথমত, নির্বাচন কমিশনকে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি ছাড়া নির্বাচনের আয়োজন করলে সেটি কাগজে কলমে বৈধ হলেও জনগণের কাছে বৈধতা হারাবে। দ্বিতীয়ত, আইনের প্রয়োগে স্বচ্ছতা আনতে হবে। যদি কোনো দল বা প্রার্থী সত্যিই আইন ভঙ্গ করে, তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হোক; কিন্তু সেটি যেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়। তৃতীয়ত, ভোটারদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে স্বচ্ছ প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে জনগণ নিশ্চিত হয় যে তাদের ভোট গোনা হবে এবং ফলাফলে প্রতিফলিত হবে।
ভবিষ্যতের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন। আমাদের রাজনীতিতে দলীয় আনুগত্য এতটাই প্রভাবশালী যে ব্যক্তি প্রার্থীর যোগ্যতা ও সততা গৌণ হয়ে গেছে। যদি দল বড় হয়, তবে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রার্থীরাও সহজে নির্বাচিত হয়। এই সংস্কৃতি না বদলালে ভোটারদের হতাশা কখনো কাটবে না।
এখন পর্যন্ত যা বোঝা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির অনুপস্থিতি একটি বড় সংকট তৈরি করবে। তাদের কোটি কোটি ভোটার হয়তো ভোটকেন্দ্রে যাবে না, বা গেলে বিকল্প প্রার্থীকে ভোট দেবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও। এতে নির্বাচনের অংশগ্রহণ কমে যাবে এবং নির্বাচনের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে।
বাংলাদেশের গণতন্ত্র ইতিমধ্যে বহু ধাক্কা খেয়েছে। একদলীয় শাসন, জালিয়াতি নির্বাচন, সহিংসতা—সবই আমরা দেখেছি। এবার যদি জনগণের প্রধান দুই দলের ভোটারদের প্রান্তিক করে দেওয়া হয়, তবে সেটি হবে গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় আঘাত। তাই এখনই সময় নির্বাচন কমিশন, সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর একসঙ্গে বসে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার। অন্যথায় নির্বাচনী প্রক্রিয়া জনগণের চোখে হাস্যকর হয়ে উঠবে, এবং গণতন্ত্র একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়বে।
ভোটারদের প্রশ্ন আজ স্পষ্ট: যখন তাদের প্রিয় দল নেই, তখন তারা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে কী করবে? এই প্রশ্নের জবাব যদি এখনই না দেওয়া যায়, তবে আগামীর নির্বাচন হবে কেবল আরেকটি রাজনৈতিক নাটক, যেখানে জনগণ থাকবে দর্শকের আসনে, আর ক্ষমতার খেলা চলবে মঞ্চে।






আপনার মতামত জানানঃ