 ভারতকে পাশ কাটিয়ে ক্রমে পাকিস্তানের দিকে ট্রাম্পের ঝোঁকার অর্থ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বৃত্তে এক গভীর বার্তা। এ শুধু আমেরিকা-পাকিস্তান সম্পর্কের উষ্ণতা নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক ভারসাম্য এক বড় ধাক্কা খেতে চলেছে—এটাই বর্তমান পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফার প্রেসিডেন্সির এই নতুন যুগে, তিনি যেন সেই পুরনো কূটনৈতিক নীতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন, যার কেন্দ্রে ছিল ভারতকে কৌশলগত মিত্র হিসাবে ধরে রাখা ও পাকিস্তানকে দূরে ঠেলে দেওয়া। অথচ এখন সেই ট্রাম্প-ই বলছেন, “কে জানে, একদিন হয়তো দেখা যাবে পাকিস্তান ভারতেও তেল বিক্রি করছে!”
ভারতকে পাশ কাটিয়ে ক্রমে পাকিস্তানের দিকে ট্রাম্পের ঝোঁকার অর্থ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বৃত্তে এক গভীর বার্তা। এ শুধু আমেরিকা-পাকিস্তান সম্পর্কের উষ্ণতা নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক ভারসাম্য এক বড় ধাক্কা খেতে চলেছে—এটাই বর্তমান পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফার প্রেসিডেন্সির এই নতুন যুগে, তিনি যেন সেই পুরনো কূটনৈতিক নীতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন, যার কেন্দ্রে ছিল ভারতকে কৌশলগত মিত্র হিসাবে ধরে রাখা ও পাকিস্তানকে দূরে ঠেলে দেওয়া। অথচ এখন সেই ট্রাম্প-ই বলছেন, “কে জানে, একদিন হয়তো দেখা যাবে পাকিস্তান ভারতেও তেল বিক্রি করছে!”
এই উক্তি নিছক ঠাট্টা নয়, বরং এক বহুমাত্রিক কৌশলগত সংকেত। একদিকে ভারতে চাপ সৃষ্টি করা, অন্যদিকে পাকিস্তানকে কাছে টানা—দুটি কাজ ট্রাম্প একই সঙ্গে করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ভারতের ওপর ২৫% শুল্ক আরোপের ঠিক পরপরই ট্রাম্প যে পাকিস্তানের সঙ্গে জ্বালানি সহযোগিতার ঘোষণা দেন, তা নিছক কাকতাল নয়। বরং এটিই আজকের ‘আমেরিকান ফরেন পলিসি’-র বাস্তব চেহারা—যেখানে অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক।
ট্রাম্প প্রশাসন এ মুহূর্তে পাকিস্তানের খনিজ তেল খাতকে যৌথভাবে বিকশিত করার ঘোষণা দিয়েছে। যদিও সেই তেলের মজুদের সুনির্দিষ্ট তথ্য আজও অধরা, তথাপি ঘোষণাটিই যথেষ্ট ছিল বোঝাতে যে ইসলামাবাদ ও ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক সম্পর্ক এক নতুন মোড় নিচ্ছে। কয়েক বছর আগেও যে পাকিস্তানকে ট্রাম্প মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক বলেছিলেন, এখন সেই পাকিস্তানকেই তিনি ‘ফেনোমেনাল পার্টনার’ বলে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন।
এই পুরো প্রেক্ষাপটে ভারতের ভূমিকা এখন কোথায়? মার্কিন নীতি-পরিবর্তনের ফলে ভারত বেশ কিছু শুল্ক ও শাস্তিমূলক করের মুখোমুখি হয়েছে। একই সময়ে পাকিস্তান শুধু যে জ্বালানি চুক্তি করতে পেরেছে, তা-ই নয়, বরং মার্কিন ডিফেন্স হার্ডওয়্যার—যেমন এফ-১৬ যুদ্ধবিমান, মিসাইল, ও রকেট সিস্টেমের জন্য নতুন করে দরকষাকষি শুরু করেছে।
একই সঙ্গে মার্কিন সেনাপ্রধান জেনারেল কুরিলাকে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সামরিক খেতাব ‘নিশান-ই-ইমতিয়াজে’ দেওয়া, কিংবা ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের হোয়াইট হাউসে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ পাওয়া, সবই প্রমাণ করে যে পাকিস্তান এখন আবার মার্কিন ঘনিষ্ঠতায় ফিরেছে। ভারত এই সময়ে স্পষ্টভাবে এক কূটনৈতিক একাকীত্বের শিকার।
আরও এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পাকিস্তানের সঙ্গে ট্রাম্প পরিবারের ব্যবসায়িক যোগাযোগ। ট্রাম্প পরিবারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ‘ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফিনান্সিয়াল’-এর সঙ্গে পাকিস্তানের সম্ভাব্য অংশীদারিত্ব কেবল ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ বা লেনদেনের বিষয় নয়, বরং সেটা স্পষ্টতই একটি বাণিজ্যিক স্বার্থে গাঁথা রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব—যার মধ্য দিয়ে ট্রাম্প নিজের ও পরিবারের আর্থিক স্বার্থকেও কৌশলগত সম্পর্কের ছায়ায় নিয়ে এসেছেন।
তবে শুধু অর্থনীতি ও সামরিক সহযোগিতা নয়, বরং আন্তর্জাতিক সম্মান ও কূটনৈতিক স্বীকৃতিও এই ঘনিষ্ঠতার এক বড় কারণ। পাকিস্তান যে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করেছে, তারও একটি অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী প্রভাব পড়েছে। এই প্রস্তাবটিকে ট্রাম্প দারুণভাবে পুঁজি করেছেন এবং নিজের কূটনৈতিক অর্জন হিসেবে তুলে ধরেছেন।
তবে প্রশ্ন হলো—ভারতের জন্য এর অর্থ কী? ভারতের কূটনৈতিক চাপ এখন দুই দিক থেকে। একদিকে চীনের সাথে সীমান্ত উত্তেজনা, অন্যদিকে পাকিস্তান-মার্কিন ঘনিষ্ঠতা। ‘কোয়াড’ জোটের সদস্য হিসেবে এতদিন আমেরিকা ভারতের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চললেও, ট্রাম্পের সময় এ জোটকে প্রায় অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। তার বক্তৃতায় ‘কোয়াড’ এখন অনুপস্থিত, ভারতও অনেকটাই প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে।
এই বাস্তবতায় ভারতের সাবেক কূটনীতিকদের অনেকেই বলছেন, আমেরিকা হয়তো এখন চীনের সঙ্গে সরাসরি ডিল করতেই বেশি আগ্রহী, এবং সেক্ষেত্রে ভারত আর ‘ব্যালান্সিং ফ্যাক্টর’ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কে সি সিং যেমন বলেন, “ট্রাম্প হলেন সেই মানুষ, যিনি মধ্যস্থতা নয়, সরাসরি লেনদেনে বিশ্বাসী।” এই সরাসরিতার মধ্যেই পাকিস্তান হয়ে উঠছে নতুন অংশীদার।
ভারতের অর্থনৈতিক দিক থেকেও এটি অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির ফলে ভারতের রপ্তানিমুখী শিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি খাত বিপুল চাপের মুখে পড়ছে। তার ওপর যদি পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও সামরিক চুক্তি বাস্তবায়িত হয়, তবে তা দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্য একেবারে পাল্টে দিতে পারে।
এবং এই সমীকরণ ভারতের পশ্চিম সীমান্তে যে নতুন সামরিক উদ্বেগ তৈরি করবে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। চীন-পাকিস্তান যৌথ সামরিক উপস্থিতি, আমেরিকার প্রযুক্তিগত ও অস্ত্র সহায়তা, এবং ভারতের সঙ্গে আমেরিকার কৌশলগত দূরত্ব—সব মিলিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় এক নতুন শীতল যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
অতএব, ট্রাম্পের পাকিস্তান ঘেঁষা এই নতুন কূটনীতি শুধুই সাময়িক বাণিজ্যিক বা সামরিক কৌশল নয়, বরং তা একটি বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক অভিসন্ধির অংশ। এর পরিণতি ভারত, পাকিস্তান, চীন ও গোটা এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের কৌশলগত কাঠামোকে আগামী বছরগুলোতে আমূল বদলে দিতে পারে। ভারত যদি এই পরিবর্তনের উপযুক্ত উত্তর খুঁজে না পায়, তবে শুধু আমেরিকার কূটনৈতিক কাছাকাছি নয়, বরং আন্তর্জাতিক কূটনীতি থেকে তার ধীরে ধীরে ছিটকে পড়াও অস্বাভাবিক নয়।


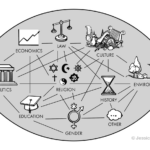



আপনার মতামত জানানঃ