
২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে, গণঅভ্যুত্থানের মাত্র এক মাস পর ড. মো. মাহবুবুল আলম একটি নিবন্ধে বলেছিলেন, “অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না।” তখন প্রায় সবাই আশাবাদী ছিলেন যে, দেশের রাজনৈতিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু ২০২৫ সালের জুলাইতে এসে সেই আশাবাদ এখন প্রশ্নবিদ্ধ—বাংলাদেশ কি সত্যিই আবারো একটি বড় সুযোগ হারালো?
কোটা সংস্কার থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন এক সময় একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে সার্বজনীন গণআন্দোলনে রূপ নেয়। সব মত-পথ, ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি-পেশার মানুষ রাজপথে এক হয়েছিলেন। দেশের মানুষ আশা করেছিল, অন্তর্বর্তী সরকার স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সঙ্গে পথ দেখাবে। কিন্তু সেই আশা অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ হয়নি।
একটি বড় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় ছাত্র নেতাদের সরাসরি সরকারের অংশ হয়ে যাওয়ায়। আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি হয়ে যারা উঠে এসেছিলেন, তারা যখন অতিদ্রুত রাজনৈতিক ক্ষমতার বলয়ে ঢুকে পড়েন, তখন সাধারণ মানুষ বিস্মিত হয়। নাহিদ ইসলাম সরকারের অংশ থেকে পদত্যাগ করলেও, ততদিনে সরকার ও ছাত্র নেতৃত্ব—দুই পক্ষের প্রতি মানুষের আস্থা তলানিতে পৌঁছে গেছে।
সরকারের ব্যর্থতা প্রথমেই দেখা যায় প্রশাসনিক দুর্বলতায়। প্রধান উপদেষ্টার আবেগপ্রবণ বক্তৃতা, আনসার বিদ্রোহ, আহত আন্দোলনকারীদের চিকিৎসায় অবহেলা, এবং আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা—এসব ঘটনাই সরকারের ভবিষ্যত প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। যদিও সরকার বিদেশ থেকে দক্ষ পেশাজীবীদের ফিরিয়ে এনে বড় দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তারা দেশে এসে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আনতে ব্যর্থ হয়েছেন।
একটি চমৎকার উদাহরণ হলো বিনিয়োগ সম্মেলন। আয়োজনটি ভালো হলেও, কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে এর বাস্তব সফলতা সীমিত। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমেরিকার শুল্ক নীতির চাপ, ডোনাল্ড ট্রাম্পের অগোছালো অর্থনৈতিক নীতি—সব মিলিয়ে সরকার বাণিজ্য ঘাটতির মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে।
সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা দেখা গেছে আইনের শাসন ও নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে। অনিরাপত্তার অনুভূতি, মামলাবাজির বিস্তার, প্রকৃত অপরাধীর রেহাই ও নিরীহদের শাস্তি—সব মিলিয়ে দেশের আইন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। পুলিশ বাহিনী এখনো পুরোপুরি সক্রিয় নয়। পুলিশের মধ্যে স্বজনপ্রীতি ও উদাসীনতা বিরাজমান, আর সরকারের সংস্কার কমিশনগুলোও ফলপ্রসূ হয়নি।
সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সংস্কার, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার। এসব বিষয়ে সরকার জোরালো পদক্ষেপ না নেয়ায়, জনগণের সমর্থন দুর্বল হয়ে পড়েছে। পিআর পদ্ধতি, নির্বাচনী সংস্কার, কিংবা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা—এসব বিষয়েও সরকার দ্বিধাগ্রস্ত থেকেছে।
বিএনপির ভেতরও দেখা গেছে সাংগঠনিক দুর্বলতা। শতাধিক নেতাকর্মীকে বহিষ্কার করা হলেও, তাদের অনেকেই এখনো দলীয় কর্মকাণ্ডে জড়িত। এটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে ভুল বার্তা দিয়েছে। দলটির মধ্যে এখনো রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সততার ঘাটতি স্পষ্ট। দীর্ঘ ১৭ বছরের অপশাসনের শিকার দলটি এখনো প্রকৃত সংস্কারের পথে নামেনি।
এই রাজনৈতিক স্থবিরতার মূল কারণ হতে পারে ছাত্র নেতাদের আচরণ। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে অতিদ্রুত রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হওয়া, ক্ষমতার লোভে জড়িয়ে পড়া, নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করা—এসব আচরণ জনগণের মনে হতাশা তৈরি করেছে। কেউ কেউ আন্দোলনের নাম ভাঙিয়ে চাঁদাবাজি শুরু করেছে। এতে সংস্কারের পথ আরও কঠিন হয়েছে।
সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, সংকটের সময় সরকারের অভ্যন্তরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আবার পরিবর্তন করার প্রবণতা, এবং দায়িত্বশীলদের বক্তব্যে অতিরিক্ত আবেগ—এসব কারণে জনগণের আস্থা নষ্ট হয়েছে। জনগণ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, সরকারের ভেতরে আরেকটি সরকার কাজ করছে।
এই প্রেক্ষাপটে বড় প্রশ্ন হলো, অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে থাকা ড. ইউনুস এই সংকটের মুহূর্তে কি একটি শক্ত নেতৃত্ব দিতে পারবেন? তিনি কি সত্যিই একজন ঐতিহাসিক নেতা হয়ে উঠবেন, নাকি তিনিও ইতিহাসের একটি ‘হারানো সুযোগ’ হিসেবেই স্মরণীয় হবেন?
এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি। সরকার চাইলে, সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজকে নিয়ে নতুন করে সংস্কারের রূপরেখা তৈরি করতে পারে। আইনের শাসন নিশ্চিত করা, দখল-চাঁদাবাজি রোধ, রাজনৈতিক শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা—এসব পদক্ষেপ নিলে এখনও দেশের ভবিষ্যতকে আলোর পথে ফেরানো সম্ভব। তবে এর জন্য প্রয়োজন সাহসী, দূরদর্শী ও স্বচ্ছ নেতৃত্ব। যেটি এখনো অনুপস্থিত।


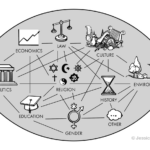



আপনার মতামত জানানঃ