 ঢাকা যেন হঠাৎ করে নিজেরই ভঙ্গুরতা নতুন করে আবিষ্কার করছে। কয়েক দিনের ব্যবধানে রাজধানী ও এর আশপাশের এলাকায় লাগাতার ভূমিকম্প—কখনো মাঝারি, কখনো তুলনামূলক মৃদু—মানুষকে শুধু ভয় পাইয়ে দিচ্ছে না, বরং বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘদিনের উদ্বেগকে আরও স্পষ্ট করে সামনে এনে দিচ্ছে। শুক্রবার সকালে নরসিংদীর মাধবদী থেকে উৎপন্ন ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প এবং পরের দিন ঢাকা–নরসিংদী অঞ্চলে হওয়া আরও কয়েকটি কম্পন দেখিয়ে দিয়েছে, এই শহর শুধু যানজট, জলাবদ্ধতা আর বায়ুদূষণের ঝুঁকিতে নয়; ভূমিকম্পজনিত বৃহৎ দুর্যোগের মুখেও দাঁড়িয়ে আছে।
ঢাকা যেন হঠাৎ করে নিজেরই ভঙ্গুরতা নতুন করে আবিষ্কার করছে। কয়েক দিনের ব্যবধানে রাজধানী ও এর আশপাশের এলাকায় লাগাতার ভূমিকম্প—কখনো মাঝারি, কখনো তুলনামূলক মৃদু—মানুষকে শুধু ভয় পাইয়ে দিচ্ছে না, বরং বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘদিনের উদ্বেগকে আরও স্পষ্ট করে সামনে এনে দিচ্ছে। শুক্রবার সকালে নরসিংদীর মাধবদী থেকে উৎপন্ন ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প এবং পরের দিন ঢাকা–নরসিংদী অঞ্চলে হওয়া আরও কয়েকটি কম্পন দেখিয়ে দিয়েছে, এই শহর শুধু যানজট, জলাবদ্ধতা আর বায়ুদূষণের ঝুঁকিতে নয়; ভূমিকম্পজনিত বৃহৎ দুর্যোগের মুখেও দাঁড়িয়ে আছে।
ভূমিকম্পবিদদের ভাষায়, ঢাকার বিপদ মূলত তিনটি স্তরে জমে আছে—ভূগর্ভের ফাটল রেখা, মাটির গঠন আর মানুষের হাতের তৈরি নগরচিত্র। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে হওয়া ৩৯টি ভূমিকম্পের মধ্যে ১১টির উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার খুব কাছাকাছি, ৮৬ কিলোমিটারের মধ্যে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রার কম্পনটি—৫ দশমিক ৭—ঘটেছে নরসিংদীর মাধবদীতে। আরও কয়েকটি কম্পন লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ, রাঙামাটি, সিলেট, দিনাজপুর, কুড়িগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে হলেও ঢাকার আশপাশে ভূমিকম্পের ঘনত্ব বিশেষজ্ঞদের চোখে নতুন সংকেত দিচ্ছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের সাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বর্তমানে অধিদপ্তরের পরিচালক মো. মমিনুল ইসলাম ব্যাখ্যা করলেন, দেশের ভেতরে তিন দিকে তিনটি সক্রিয় টেকটনিক প্লেট আমাদের ঘিরে রেখেছে। সীমান্তের আশপাশে এসব প্লেটের সংযোগস্থল বা প্লেট বাউন্ডারি বরাবর ছোট ছোট ভূমিকম্প নিয়মিতই হচ্ছে, আর সেখানেই বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা লুকিয়ে থাকে। নরসিংদী অঞ্চলে আগে কম মাত্রার কম্পন হলেও সেগুলোকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এখন বোঝা যাচ্ছে, সেখানে যে সাব–ফল্ট বা উপ–ফাটল আছে, তা ঢাকার কাছ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বেশ বড় আকারের। তার ভাষায়, সাম্প্রতিক ভূমিকম্প প্রমাণ করেছে—ঢাকা এখন বড় ধরনের ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে অস্বস্তিকরভাবে অবস্থান করছে।
শুক্রবারের ভূমিকম্পের গভীরতাও এই ঝুঁকি বাড়িয়ে দেখায়। মাধবদী এলাকার ভূকম্পনের উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্প বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম হলো, উৎপত্তিস্থল যত অগভীর হবে, উপরের অংশে কম্পন তত বেশি অনুভূত হবে। তাই ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় মানুষ যেভাবে ঝাঁকুনি টের পেয়েছে, তা স্মরণকালের অনেক ঘটনার চেয়ে বেশি তীব্র। এতে শিশুসহ ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, ৬ শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন, অনেকে আতঙ্কে ভবন থেকে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। এত অল্প সময়ে, এত বড় এলাকায়, এত বেশি মানুষের অনুভূত কম্পন—নিজেই এক ধরনের সতর্কবার্তা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও ভূমিকম্পবিশেষজ্ঞ হুমায়ুন আখতার এই ঘটনাকে একটি চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখছেন। তাঁর মতে, সাবডাকশন জোনে, যেখানে দুটি টেকটনিক প্লেট একে অন্যের নিচে সরে যায়, সেখানে বহু বছর ধরে বিপুল পরিমাণ শক্তি জমা হয়ে আছে। এখন পর্যন্ত সেই শক্তির অতি সামান্য অংশ, ১ শতাংশেরও কম, নির্গত হয়েছে। বারবার যে মাঝারি ও মৃদু ভূকম্প হচ্ছে, তা আসলে শক্তি নির্গমনের শুরু—যাকে আমরা ‘আফটার শক’ ভাবছি, তা হতে হতে কোনো এক সময় বড় ভূমিকম্পে রূপ নিতে পারে। তাঁর কথায়, ভূগর্ভের যে ফাটল এতদিন প্রচণ্ড চাপে আটকে ছিল, তা এখন নড়তে শুরু করেছে—এই নড়াচড়াই বড় বিপদের পূর্বাভাস।
ঢাকার জন্য এই সতর্কবার্তা আরও জোরালো হয়ে ওঠে যখন মাটির গঠন, নগর পরিকল্পনা আর জনঘনত্বের বাস্তবতা সামনে আসে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক রাকিব হাসান ঢাকার ঝুঁকিকে চারটি মূল কারণে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম কারণ, ফল্ট লাইনের নৈকট্য—ঢাকার এত কাছে বড় একটি সাব–ফল্টের অস্তিত্ব এত স্পষ্টভাবে আগে চিহ্নিত ছিল না, এখন সেটি ‘খুলে যাচ্ছে’ এবং সক্রিয় হচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ, মাটির ধরন। ঢাকার নতুন অনেক অংশ, বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণাংশ, নিচু ভূমি ভরাট করে গড়ে তোলা হয়েছে। নরম, ভরাটকৃত মাটি ভূমিকম্পের কম্পনকে বাড়িয়ে তোলে; ফলে একই মাত্রার ভূমিকম্পের প্রভাব এখানে আরও তীব্র হতে পারে।
তৃতীয় কারণ, ইমারত নির্মাণে বিধি–বিধান না মানা। ভূমিকম্প–সহনশীল নকশা, সঠিক ডিজাইন কোড, গুণমানসম্পন্ন নির্মাণসামগ্রী—এসব ব্যবহারের কথা কাগজে কলমে থাকলেও বাস্তবে তার ব্যাপক অনিয়ম রয়েছে। অসংখ্য ভবন অনুমোদনবিহীন, আবার অনুমোদিত ভবনের ক্ষেত্রেও ডিজাইন অনুযায়ী কাজ হয়েছে কি না, তার তদারকি দুর্বল। ফলে শহরের ভবনগুলোর বড় একটি অংশ শক্তিশালী কম্পনের ধকল সইতে সক্ষম কি না, তার কোনো নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা নেই। আর চতুর্থ কারণ, জনঘনত্ব—ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ শহর। ফলে কোনো বড় ভূমিকম্প হলে এখানে ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি ও পরবর্তী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা—সবই বহুগুণ কঠিন হয়ে উঠবে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ভূমিকম্প হওয়ার সময়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত পাঁচ বছরে দেশের ভেতরে হওয়া ৩৯টি ভূমিকম্পের মধ্যে ২৩টি হয়েছে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৬টার মধ্যে। অর্থাৎ বেশির ভাগ কম্পন রাতের বেলা, যখন মানুষ ঘরে, অনেকেই ঘুমিয়ে থাকে। এমন সময়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প হলে মানুষ ঘর থেকে বের হতে দেরি করে, আতঙ্কে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, আলো না থাকলে নামার পথ খুঁজতে সমস্যা হয়—ফলে প্রাণহানি ও আহতের সংখ্যা বাড়ার শঙ্কা অনেক বেশি। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে অনেক শিক্ষার্থী ও বাসিন্দার ভবন থেকে লাফ দেওয়া, দ্রুত নেমে আসতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে পড়ে আঘাত পাওয়া—এসব ঘটনার পেছনেও সচেতনতা ও অনুশীলনের অভাবই প্রধান কারণ।
প্রশ্ন হলো, এত ঝুঁকি জেনে আমাদের প্রস্তুতি কতটা? সরকারি কাগজে–কলমে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পের কথা থাকলেও বাস্তব অগ্রগতি হতাশাজনক। ২০১৬ সালে ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় একটি ন্যাশনাল অপারেশন সেন্টার নির্মাণের জন্য চীনের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। তেজগাঁওয়ে এই কেন্দ্রের জন্য জমিও বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রায় এক দশক পার হতে চললেও সেই কেন্দ্র নির্মাণের কাজই শুরু হয়নি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন—নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত জায়গা না পাওয়ায় প্রকল্প এগোয়নি। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এত বড় ঝুঁকিতে থাকা একটি দেশের জন্য এটি এক ধরনের অবহেলাই।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলায় সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজ চলছে; বড় দুর্যোগে সশস্ত্র বাহিনী, ফায়ার সার্ভিসসহ বিভিন্ন সংস্থার যৌথ শক্তি কাজে লাগানো হয়। নগর ও উপকূলে স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তুলেও সরকার কিছুটা আশাবাদী—ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় উপকূলে যেভাবে ৮০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক কাজ করছেন, নগরেও ৪৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে ভূমিকম্প বিষয়ে সচেতনতার কাজ শুরু করা হবে। কিন্তু কেবল সরঞ্জাম কেনা আর স্বেচ্ছাসেবক তৈরির ঘোষণায় বিশেষজ্ঞরা সন্তুষ্ট নন।
দুর্যোগ ফোরামের সদস্যসচিব গওহর নঈম ওয়ারা মনে করেন, প্রকৃত প্রস্তুতির জায়গায় এখনো আমাদের বড় ঘাটতি রয়েছে। তাঁর মতে, দুর্যোগের তথ্য সংগ্রহ ও তাৎক্ষণিক উদ্যোগ নেওয়ায়ও গলদ দেখা গেছে—নরসিংদীর মতো ঘটনাতেও সঠিক তথ্য আসতে এক দিনের বেশি সময় লেগেছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যে ধরনের পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই মাঠ থেকে তথ্য আসার কথা, সেখানে আবার কেন চিঠি দিয়ে তথ্য চাইতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সময়ই যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে এই ধীরগতি বিপদের ইঙ্গিত বহন করে।
আরেকটি বড় দুর্বলতা হলো, স্থানীয় সরকারকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকরভাবে যুক্ত না করা। বিশ্বের অনেক দেশেই স্থানীয় সরকারই প্রথম প্রতিক্রিয়া, উদ্ধারকাজ ও পুনর্বাসনের মূল চালিকা শক্তি। সেখানে আমাদের বাস্তবতায় জেলা, পৌরসভা বা সিটি করপোরেশনের ভূমিকাই যথেষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নি। গওহর নঈম ওয়ারার মতে, ভূমিকম্পের মতো জটিল দুর্যোগ মোকাবিলায় শুধু কেন্দ্রীয় দপ্তরের ওপর নির্ভর করলে হবে না; ওয়ার্ড, মহল্লা, স্কুল–কলেজ—সব জায়গায় সমন্বিত পরিকল্পনা ও অনুশীলন গড়ে তুলতে হবে।
সচেতনতার অভাবও ঢাকার বড় দুর্বলতা। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে অনেক শিক্ষার্থী ও বাসিন্দা আতঙ্কে ভবন থেকে লাফিয়ে পড়েছেন, সিঁড়িতে হুড়োহুড়ি করে নেমে আঘাত পেয়েছেন—এ সবই দেখিয়ে দিয়েছে, মানুষ জানে না কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়। এ কারণে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্প ও দুর্যোগ–সচেতনতা স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক পাঠ্যসূচির অংশ হতে হবে। নিয়মিত ড্রিল, মহড়া, আগুন লাগলে বা ভূমিকম্প হলে কীভাবে নিরাপদে বের হওয়া যায়—এসব অনুশীলন প্রতিষ্ঠানভিত্তিকভাবে চালু না থাকলে, যেকোনো পরিকল্পনাই কাগজে সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।
ঢাকা আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, সেখানে দুর্যোগ মানেই শুধু প্রাকৃতিক নয়, মানবসৃষ্ট অসচেতনতা ও অপরিকল্পিততার সমন্বিত ফল। ভূগর্ভের ফাটল আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না, প্লেট টেকটনিক বদলাতে পারব না। কিন্তু আমরা ভবন–নির্মাণে ন্যূনতম কোড মানতে পারি, পরিকল্পনাহীন ভরাট বন্ধ করতে পারি, স্কুল থেকে শুরু করে অফিস পর্যন্ত সবাইকে নিয়মিত মহড়ার মধ্যে আনতে পারি। ভূমিকম্প হবে কি হবে না—এই অনিশ্চয়তার পেছনে সময় নষ্ট না করে, ধরে নিতে হবে যে হবে, আর তার আগে কী কী প্রস্তুতি নেওয়া যায়, সেটাই এখন মূল প্রশ্ন। সাম্প্রতিক কয়েকটি কম্পন যেন সেই প্রশ্নটাই আরও জোরালো করে ঢাকার প্রতিটি মানুষের সামনে রেখে গেছে।




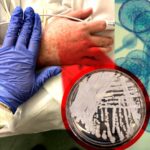

আপনার মতামত জানানঃ