
বাংলাদেশের রাজনীতিতে গত কয়েক বছরে যে উত্তেজনা ও বদল ঘেরা আছে—চলমান ছাত্র আন্দোলন, বিরোধীদলীয় তৎপরতা, নির্বাচনী-প্রস্তুতির প্রশ্ন এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর পুনঃসংਰক্ষণ—সবকিছুর মাঝেও গত অক্টোবরের শেষ দিকে এক আন্তর্জাতিক দল ঢাকায় আসে। এই দল ছিল আন্তর্জাতিক নীতি ও নির্বাচনী বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত, মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের নির্বাচনী পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা রূপায়ন করা। তারা একটি প্রাক-নির্বাচনী মূল্যায়ন মিশন পরিচালনা করে এবং ৫ নভেম্বর তারিখে একটি মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রকাশ করে। মিশন এবং রিপোর্ট উভয়ে দৃষ্টিগোচর হয় একটি বড় প্রশ্নের: একটি মধ্য-আন্তরিক সরকারের অধীনে, উন্নত নির্বাচনী প্রশাসন এবং রাজনৈতিক সংস্কার কতটা বাস্তবায়নযোগ্য হতে পারে?
এই মিশনের সূচনা হয় ২০২৫ সালের ২০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত। তারা ঢাকায় উপস্থিত হয়ে দেখা-শোনা করে, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, সাংবাদিক ও সংশ্লিষ্ট সংগঠন-সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করে। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, মিশনটি ছিল “রাজনৈতিক পরিবেশ, নির্বাচনী প্রস্তুতি ও অংশগ্রহণ-ক্ষমতা” আন্দাজ করার প্রয়াস। দলটি ঢাকার বাইরে যাওয়ার পূর্বে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে, রাজনৈতিক দলগুলোর মনোবল, নির্বাচন কমিশন-র কার্যক্রম ও সুশীল সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।
রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী-কালীন সরকার, যা Dr. Muhammad Yunus–এর নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে—নির্বাচন কমিশনের সংস্কার এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পুনঃধারণার ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা ১১টি কমিশনের মাধ্যমে একটি বড় সংস্কার কর্মসূচি শুরু করেছে, যার চূড়ান্ত রূপ হলো ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ নামে পরিচিত একটি নথি, যার মধ্যে প্রায় প্রতিটি গণতান্ত্রিক কাঠামোকে স্পর্শ করে এমন ৮৪টি প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সনদকে রিপোর্টে একটি সম্ভাব্য রূপকার হিসেবে দেখা হয়েছে, যা দেশকে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা, অংশগ্রহণ ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর দিকে গতি দিতে পারে।
তবে রিপোর্ট একই সঙ্গে সংযমে জানায়—যদিও এই সনদ-মূলক পরিকল্পনাগুলো বহুলভাবে সমর্থিত হয়েছে, তবুও তার বাস্তবায়ন এখনো অনিশ্চিত। কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে প্রক্রিয়াগত অস্পষ্টতা, সময়সাপেক্ষ বাস্তবায়ন, এবং রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে অভিন্ন মতের অভাব। নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মনোবল-মতভেদ এবং স্থানীয় প্রশাসন-নিরপেক্ষতার ওপর বহু প্রশ্ন রয়ে গেছে।
নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে বিশেষ এক দিক হলো ভোটার অংশগ্রহণ ও নির্বাচন প্রশাসনের সক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা। রিপোর্টে বলা হয় যে, নির্বাচন কমিশন প্রবাসী ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছে, নির্বাচন নিরাপত্তা জোরদারের জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে নির্বাচন নিরাপত্তা কাঠামোর অংশ করার পরিকল্পনা করছে। এটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক এক পদক্ষেপ, কারণ বহুসংখ্যক প্রবাসী বাঙালি রয়েছে যারা ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন না। তবে এই পদক্ষেপগুলোর বাস্তব প্রভাব এখনও পরিমাপ করা কঠিন। কারণ নিরাপত্তা বাহিনীর অংশগ্রহণ কখনো কখনো রাজনৈতিক পক্ষপাত-অনুভূতির উৎস হতে পারে, এবং স্থানীয় প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে।
রিপোর্টে রাজনৈতিক দলসমূহের মনোনয়ন প্রক্রিয়া-স্বচ্ছতার অভাব উল্লেখ আছে — যেটি নির্বাচনের প্রতিযোগিতা ও বৈধতা উভয়কেই প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষত নারীর অংশগ্রহণ এখনও সীমিত। রাজনৈতিক কর্মসূচির ডিজাইনে এবং মেয়েদের প্রতিনিধি হিসেবে জায়গা নিতে গিয়ে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো — দেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করতে পারে এমন চরমপন্থী ও ধর্মীয় কঠোর মতাদর্শী গোষ্ঠীর উত্থান। এই গোষ্ঠীগুলো কখনো কখনো সাধারণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে এবং একাংশের বিরুদ্ধে এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে যে ভোটাররা নির্ভয়ে অংশগ্রহণ করতে সাহস পান না।
তবে আশার সূচনা পাওয়া গেছে—রিপোর্টে বলা হয়েছে যে যুবনেতৃত্বাধীন নতুন রাজনৈতিক দলগুলোর আবির্ভাব এবং প্রথমবার ভোট দিতে যাওয়া তরুণ ও প্রবাসী ভোটারদের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা দেশকে নতুন গতি দিচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে হালকা হলেও একটি উত্তেজনাপূর্ণ অন্বেষণ দেখা যাচ্ছে — জনগণ অংশ নিতে আগ্রহী, নতুন রাজনৈতিক শক্তি উদ্ভব হচ্ছে, নির্বাচনকে শুধুই রাজনৈতিক নেতাদের এক-মঞ্চ হিসেবে না দেখে সাধারণ মানুষও নিজেকে অংশীদার হিসেবে দেখছে। এই বিকাশ গণতান্ত্রিক সংস্কারকে ত্বরান্বিত করতে পারে, যদি যথাযথভাবে ট্র্যাক করা ও সমর্থন করা হয়।
নির্বাচনের সামনে করণীয় বিষয়গুলি জানিয়েছেন রিপোর্টে — বাংলাদেশ যখন ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে, তখন পরিষ্কার হবে এই প্রশ্ন: আলোচনায়, প্রতিশ্রুতি রূপ নিয়েছে কি কাগজে-কলমেই থেকে গেছে? আসল সিদ্ধান্ত থাকবে বাস্তবায়ন-টিমিং-প্রক্রিয়াতে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সফলতা নির্ভর করবে: তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, নিরাপত্তা-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের সংস্কার এজেন্ডা বাস্তব রূপ দেয়ার ওপর। জুলাই জাতীয় সনদ এক রূপরেখা দিয়েছে, কিন্তু তার বাস্তবতা অনেকাংশে নির্ভর করবে পরবর্তী সংসদের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর। অভিন্ন সংলাপ, স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দলের বিশ্বাসযোগ্য অংশগ্রহণ — এই তিনটি বিষয় হবে মূল চাবিকাঠি।
এই পর্যায়ে মিশনের পর্যালোচনায় রিপোর্ট বলছে—এই দল ২১টি বৈঠক করেছে, যেখানে ৫৯ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন রাজনৈতিক দল, অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশনের সদস্য, গণমাধ্যম, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি। সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তারা একটি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছে। তাদের রিপোর্ট শেষে তারা সকল ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানিয়েছে যারা মতবিনিময়ে অংশ নিয়েছেন।
রিপোর্টে কিছু স্পষ্ট সংকেত রয়েছে: যে নির্বাচন প্রশাসনের ক্ষেত্রে গতিরোধ বা লেগে-থাকার সমস্যাগুলো রয়েছে — যেমন মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব, রাজনৈতিক উত্তেজনায় সহিংসতার বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি অবিশ্বাস, স্থানীয় প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন — এসব বিষয় শুধুই উল্লেখ করে শেষ হয় না, তারা সুপারিশও করেছে। যেমন: মনোনয়ন প্রক্রিয়া পুনরায় নিরীক্ষণযোগ্য করা,নারী ও তরুণ অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া, রাজনৈতিক পার্টি-অর্থায়ন ও প্রার্থীদের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ-নিরাপত্তা কর্মসূচিকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার না করার নিশ্চয়তা দেওয়া।
এখানে প্রশ্ন উঠেছে: এই সুপারিশগুলো কতটা বাস্তবায়নযোগ্য হবে? কারণ রাজনৈতিক সংস্কার সাধারণত অভ্যন্তর-বহির্ভূত বিরোধ, সময়সীমার চাপ, এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎসাহীতার অভাবে ধীর হয়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মনোবল-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া, ভোটার-ভিত্তিক অংশগ্রহণ, স্থানীয় প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর নিরপেক্ষতা—সবকিছু একসাথে প্রয়োগ-যোগ্য হওয়ার জন্য একটি সম্মিলিত সাড়া প্রয়োজন। দ্রুত-অগ্রগামী রূপান্তর হলে দেশের নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক ও মানবিক প্রতিষ্ঠানগুলো একটি নতুন গতি পেতে পারে—but তা একদিনে স্থায়ী হবে না।
পাশাপাশি, বর্তমান সময়কাল মনে করিয়ে দিচ্ছে যে ‘রূপান্তর-অনুকূল’ সময়টি ইতিমধ্যেই উপস্থিত রয়েছে। কারণ ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে নতুন প্রবাসী ভোটারদের আগ্রহ, নতুন রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্ভব—সব মিলিয়ে একটি সামাজিক উত্তেজনা ও পরিবর্তনের মনস্তত্ত্ব তৈরী করেছে। এই মনস্তত্ত্বকে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামোর সঙ্গে সংযোগ করলে একটি সার্বিক সংস্কার সম্ভব। তবে ক্ষমতা ভাগাভাগি এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে স্বভাবগত বাধাগুলো এখনও অদৃশ্য নয়। যদি রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন প্রক্রিয়া, অর্থায়ন, অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতায় মনোযোগ না দেয়, তবে এই মনোভাব-উৎকর অর্থহীন ঘূর্ণিতে পরিণত হতে পারে।
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—রিপোর্টটি শুধুই একটি নিরীক্ষণ রিপোর্ট নয়; এটি চ্যালেঞ্জও দিয়েছে, এবং একই সঙ্গে একটি সম্ভাবনার রাস্তা চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক রূপান্তরের গতিপথ মূলত নির্ভর করবে: জুলাই জাতীয় সনদ-এর অগ্রগতি কতটা টেকসই হয়, রাজনৈতিক দলগুলো কতটা আন্তরিকভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি এই রূপরেখা মূলনীতিতে রূপান্তরিত হয় — যেমন স্বচ্ছ নির্বাচন, ব্যাপক অংশগ্রহণ, নিরাপত্তা ও প্রশাসনের নিরপেক্ষতা—তাহলে দেশের নির্বাচন শুধু অনুষ্ঠিত হবে না; তার প্রতিযোগিতা ও বৈধতা থাকবে। অন্যথায়, নির্বাচনের আগেই পরবর্তী এক সংকটের সংক্রমণ তৈরি হতে পারে—নির্বাচন হবে অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ।
শেষ পর্যন্ত, এই মূল্যায়ন মিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল পাঠিয়েছে—বাংলাদেশ বেছে নিয়েছে একটি পরিবর্তনের রূপরেখার দিকে যাত্রাপথ। কিন্তু রূপ শুধু খসড়া নয়; এটি কার্যকর রূপ পাবে কি না, তা নির্ভর করবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক সক্ষমতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণের ওপর। নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক—সবকিছু মিলিয়ে যদি একটি নতুন গঠনশীল প্রকল্পে রূপান্তরিত হয়, তাহলে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন শুধু একদিনের ঘটনা হবে না—সে হতে পারে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের এক মাইলফলক।



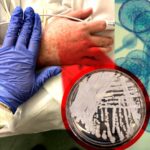


আপনার মতামত জানানঃ