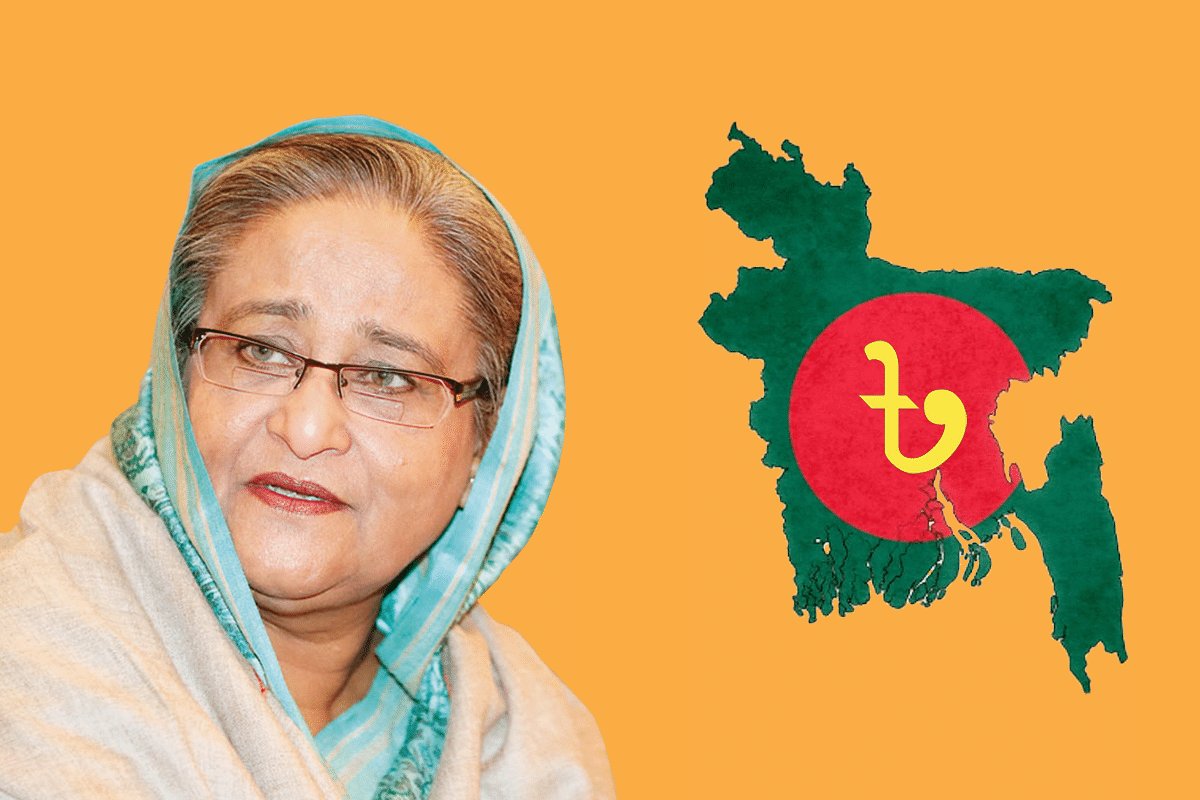
বাংলাদেশের অর্থনীতির ইতিহাসে অর্থপাচার সবসময় একটি জটিল ও ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে দেশের ভেতরের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একটি শ্রেণি বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার করেছে। সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) নতুন করে যে তথ্য প্রকাশ করেছে তা এই সমস্যার গভীরতা এবং ভয়াবহতা আরও স্পষ্ট করেছে। তাদের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পত্তি, যা বাংলাদেশের বাইরে পাচার হওয়া অর্থের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছে। এই অনুসন্ধান শুধু সংখ্যার দিক থেকে নয়, বরং একটি রাষ্ট্রের আর্থিক নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
সিআইসির এই অনুসন্ধান চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে শুরু হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় তারা পাঁচটি দেশের সাতটি শহরে সরেজমিন তদন্ত চালায়। এর ফলেই জানা যায়, বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ দিয়ে সেখানে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে বিপুল সম্পদ গড়ে তোলা হয়েছে। মহাপরিচালক আহসান হাবিব প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত অন্তত তিনশ ছেচল্লিশটি সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলো কেবল প্রাথমিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। তার ভাষায়, এটি আইসবার্গের চূড়া মাত্র। কারণ এখনো অগণিত তথ্য তাদের হাতে রয়েছে যা বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই করতে সময় প্রয়োজন। এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচারের পরিমাণ বাস্তবে আরও বহুগুণ বেশি হতে পারে।
অনুসন্ধান থেকে যে আরেকটি উদ্বেগজনক তথ্য সামনে এসেছে তা হলো বিদেশি পাসপোর্ট ক্রয়ের প্রবণতা। অন্তত নয়টি দেশে তিন শতাধিক বাংলাদেশি টাকা দিয়ে পাসপোর্ট কিনেছে। অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, অস্ট্রিয়া, ডমিনিকা, গ্রেনেডা, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, নর্থ মেসিডোনিয়া, মাল্টা, সেন্ট লুসিয়া ও তুরস্কে এই পাসপোর্টগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। সাধারণত এই ধরনের পাসপোর্ট কেনার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে বিদেশে স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ তৈরি করা, কর ফাঁকি দেওয়া অথবা পাচারকৃত অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ফলে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও একটি অংশ বিদেশি নাগরিকত্বের আড়ালে অপরাধমূলক কার্যক্রমকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যও একটি বড় হুমকি।
সিআইসির অনুসন্ধান বলছে, পাচার হওয়া অর্থ দিয়ে সবচেয়ে বেশি সম্পত্তি গড়ে তোলা হয়েছে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দুবাই এবং লন্ডনে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া এবং ফ্লোরিডাতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পত্তি চিহ্নিত হয়েছে। এই তালিকা থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রবাসী বাণিজ্যিক শহর এবং অর্থনৈতিকভাবে আকর্ষণীয় অঞ্চলগুলোই পাচারকারীদের প্রথম পছন্দে পরিণত হয়েছে। কারণ এসব শহরে বিনিয়োগ করলে শুধু বৈধ ব্যবসার ছদ্মবেশ তৈরি করা যায় না, বরং সম্পদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দুবাই দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণ এশিয়ার অর্থপাচারকারীদের অন্যতম আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত। আর লন্ডন বা নিউইয়র্কে সম্পত্তি কেনা একটি মর্যাদার প্রতীক হিসেবেও কাজ করে, যা পাচারকারীদের সামাজিক অবস্থানকে দৃশ্যত শক্তিশালী করে তোলে।
প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এই অনুসন্ধান রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর একেবারেই কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন, এই ধরনের লুটপাট সরাসরি দেশদ্রোহিতার শামিল। দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিজেদের আখের গোছাতে চেয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে উদাহরণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, দুদক, সিআইসি, পুলিশের সিআইডি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা একযোগে কাজ করবে যাতে সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করে দেশের অনুকূলে আনা যায়। তার মতে, ভবিষ্যতে যেন কেউ সাহস না পায় দেশের সম্পদ বিদেশে সরিয়ে নিতে, সেজন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা জরুরি।
আহসান হাবিবের বক্তব্য অনুযায়ী, অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িতরা অতীতে শেখ হাসিনার শাসনামলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডাটাবেস নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের লোক বসিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গায়েব করে দেয়। তবে আশার কথা হচ্ছে, বর্তমানে সিআইসি তথ্য পুনরুদ্ধারে এমন দক্ষতা অর্জন করেছে যা মুছে ফেলা তথ্যও উদ্ধার করতে সক্ষম। অর্থাৎ পূর্ববর্তী সময়ে যত তথ্য গোপন করার চেষ্টা করা হোক না কেন, প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এখন সেই সব তথ্য আবারও আলোর মুখ দেখছে। এটি ভবিষ্যতে অর্থপাচার তদন্তের ক্ষেত্রে একটি বড় ইতিবাচক দিক।
প্রশাসনিকভাবে এই অনুসন্ধান ইতিমধ্যে দৃশ্যমান প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। জানা গেছে, এনবিআর ইতোমধ্যে কর ফাঁকি দেওয়া কিছু করদাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং প্রায় দশ হাজার কোটি টাকার কর ও জরিমানা আদায়ের প্রক্রিয়া চলছে। এর ফলে প্রমাণিত হয়, শুধু পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না উদ্যোগ, বরং দেশীয় রাজস্ব আয়ও বাড়াতে সরাসরি ভূমিকা রাখছে এই অভিযান। একদিকে পাচারকারীরা তাদের সম্পদ হারানোর ভয় পাচ্ছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে নতুন আয় যুক্ত হচ্ছে। এটি দেশের অর্থনীতির জন্য নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক।
তবে প্রশ্ন উঠছে, এই বিশাল প্রক্রিয়া কতটা সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। অর্থপাচারের সঙ্গে সাধারণত প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই জড়িত থাকে, যাদের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক যোগাযোগ থাকে। ফলে তাদের আইনের আওতায় আনা সবসময় সহজ নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অনেক সময় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা শাস্তির মুখোমুখি হয় না। তাই জনগণের প্রত্যাশা হচ্ছে, এইবার যেন সেই পুরোনো ধারা না চলে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে ইতোমধ্যেই শক্ত বার্তা দেওয়া হয়েছে, যা আশার আলো জাগায়। কিন্তু বাস্তবে এই প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করবে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, আইনি প্রক্রিয়ার দৃঢ়তা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর।
এই ঘটনা বাংলাদেশের জন্য এক ধরনের সুযোগও তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি প্রায়শই দুর্নীতি, অর্থপাচার ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি এই উদ্যোগ সফল হয় এবং পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনা যায়, তবে তা আন্তর্জাতিকভাবে ইতিবাচক বার্তা দেবে। পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে আস্থা তৈরি হবে। তারা বুঝতে পারবে যে, রাষ্ট্র তার আর্থিক স্বচ্ছতা রক্ষায় কঠোর অবস্থানে রয়েছে।
অন্যদিকে এই অনুসন্ধান সাধারণ মানুষের মধ্যেও নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকে মনে করছেন, দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতিবাজরা যে অর্থ বিদেশে পাচার করেছে তা দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহার হলে আজ বাংলাদেশের চেহারাই অন্যরকম হতো। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো কিংবা কর্মসংস্থানে বিপুল বিনিয়োগ করা যেত, যার ফলে মানুষের জীবনমান সরাসরি উন্নত হতো। অথচ সেই অর্থ দেশের বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত বিলাসিতা বা বিদেশি সম্পদে আটকে আছে। তাই জনগণ এখন প্রত্যাশা করছে, অন্তত আংশিক হলেও এই অর্থ দেশে ফেরত আনা সম্ভব হবে এবং তা জনস্বার্থে ব্যয় করা হবে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, এই অনুসন্ধান বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট। কারণ এত বড় অঙ্কের অর্থপাচারের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আগে কখনো এতটা প্রকাশ্যে আসেনি। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোও জরুরি। অর্থপাচার সাধারণত সীমান্ত অতিক্রম করে হয়, তাই এককভাবে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে এটি রোধ করা সম্ভব নয়। ইতোমধ্যেই ছয়টিরও বেশি আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে। ভবিষ্যতে আরও দেশ ও সংস্থা যুক্ত হলে পাচারকৃত সম্পদের সন্ধান ও পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া আরও কার্যকর হবে।
শেষ পর্যন্ত এই অনুসন্ধান কেবল একটি আর্থিক ঘটনার বিবরণ নয়, এটি একটি জাতির সংগ্রামের কাহিনি। দুর্নীতি ও পাচারের বিরুদ্ধে যে লড়াই বহু বছর ধরে চলে আসছে, তার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো এভাবে। বাংলাদেশ যদি সত্যিই এই অর্থ ফিরিয়ে আনতে পারে এবং দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে পারে, তবে তা দেশের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হবে। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শক্ত বার্তা যাবে যে, রাষ্ট্র কখনোই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবে না। আর যদি ব্যর্থ হয়, তবে আবারও প্রমাণিত হবে যে, প্রভাবশালী চক্রের সামনে রাষ্ট্র অসহায়। এখন দেখার বিষয়, এই লড়াই কোন পথে এগোয়।






আপনার মতামত জানানঃ