
খুব বেশি না, এক শতক আগেও দুনিয়ায় মুরগির আইটেম খাওয়ার এমন চল ছিল না। আমেরিকানদের ক্ষেত্রেও ছিল একই চিত্র। সারা বছর নরম কিন্তু খুব একটা স্বাদহীন মুরগির মাংস খাওয়া বেশ আধুনিক চিত্র।
খুব বেশি না, এক শতক আগেও দুনিয়ায় মুরগির আইটেম খাওয়ার এমন চল ছিল না। আমেরিকানদের ক্ষেত্রেও ছিল একই চিত্র। সারা বছর নরম কিন্তু খুব একটা স্বাদহীন মুরগির মাংস খাওয়া বেশ আধুনিক চিত্র। বলা যায় আধুনিক জীবন ব্যবস্থার একটি লক্ষণ। ‘বিকল্প মাংস’ থেকে চিকেন কীভাবে আমেরিকানদের প্রধান মাংসের উৎস হয়ে উঠল সে গল্প বেশ বিচিত্র। এ গল্পের শুরুটা হয়েছিল গম থেকে।
বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মুরগি খাওয়া হতো মূলত বসন্তকালে। তখন মুরগি পালনকারীদের মূল মনোযোগ ছিল ডিম উৎপাদন। তাই ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার পর সব মোরগ বিক্রি করে দেয়া হতো। এগুলো তুলনামূলক কম বয়সী হতো, খাওয়া হতো রোস্ট করে বা ভেজে। এদের বলা হতো ‘স্প্রিং চিকেন’। এর বাইরে অন্য সময়ে চিকেন মানে ছিল বয়স্ক মুরগি। এটাই ছিল তখনকার আমেরিকায় মুরগি খাওয়ার রীতি।
মার্কিন খাদ্য ইতিহাসবিদ ও পুটিং মিট অন দি আমেরিকান টেবল গ্রন্থের লেখক রজার হোরোভিৎস বলেন, ‘বিশ শতকের শুরুর দিকে কৃষকরা বাজারে নানা বর্ণ, জাত, বয়সের মুরগি সরবরাহ করতেন।’ তবে এগুলো সবই ছিল ডিম উৎপাদনের পর বাড়তি হয়ে যাওয়া মোরগ-মুরগি। মানে বাজারে এদের সবসময় পাওয়া যেত এমনটা নয়। নরম মাংসের মুরগির দাম ছিল বেশি। সবাই সেটা খাওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন না, অন্তত আজকের দিনের মতো। আবার বেশি দামের কারণে সেটা সীমাবদ্ধ ছিল অবস্থাপন্ন মানুষের মধ্যে। এ নরম মাংসের মুরগিকেই ব্রয়লার বলা হতো, অর্থাৎ যে মাংস সহজে সেদ্ধ করা যেত।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গরু, শূকরের মাংসের সরবরাহ সাধারণ মানুষের জন্য সীমিত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রচারণা শুরু হয় মুরগি ও মাছ খেয়ে ‘গরু, শূকর ও ভেড়া’র মাংস যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্য সরবরাহ নিশ্চিত করার। ধীরে ধীরে মুরগি খাওয়া নিত্যদিনের অভ্যাস হয়ে উঠতে থাকে। সবার পছন্দ অল্প বয়সী নরম মাংসের মুরগি, যা ব্রয়লার নামে পরিচিত হয়ে ওঠে, আর থাকে বুকের মাংসের বড় টুকরোর প্রতি আকর্ষণ।
এদিকে যুদ্ধ শেষ হয়ে এল। গরু, ভেড়ার জন্য যে বিপুল গমের শস্য মজুদ করা হয়েছিল তা নিয়ে ফিড মিলাররা ভাবনায় পড়লেন। সমাধানও অবশ্য তাদের সামনে ছিল। যেহেতু মুরগির চাহিদা তৈরি হয়েছে তাহলে তাদের খাবার হিসেবেই কাজে লাগানো হবে এ গম। কিন্তু মুরগির খামার করতে ব্যাংকগুলো তখন ঋণ দিতে রাজি নয়। তখন ফিড মালিকরা নিজেরাই কৃষকদের বাকিতে খাবার ও অন্য দরকারি জিনিসপত্র সরবরাহ করেন। এভাবেই আধুনিক কন্ট্রাক্ট পোলট্রি খামার গড়ে ওঠে।
ব্রয়লারের প্রতি আমেরিকানদের আগ্রহ ঠিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়নি। ১৯৩০-এর দশকে আমেরিকানরা বছরে গড়ে সাড়ে চার কেজি মুরগির মাংস খেতেন। এখন সেটা ৭০ কেজির কাছাকাছি। আমেরিকানরা মুরগিকে ঠিক ‘মাংস’ হিসেবে মেনে নেননি বহু বছর ধরে, গরু ছিল খাওয়ার জন্য প্রকৃত ‘মাংস’। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে মুরগির খামারি ও ফিড ব্যবসায়ীরা ব্রয়লার মুরগির বিভিন্ন রেসিপিকে জনপ্রিয় করতে ভূমিকা রেখেছেন।
আমেরিকার ফুড কোম্পানি টাইসন ফুডসের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ডন টাইসনের একটি কথা খুব বিখ্যাত—‘মুরগির বুকের মাংসের পাউন্ড যদি ২ ডলার হয়, তাহলে ডার্ক মিট (অন্য অংশের) হওয়া উচিত ১ ডলার। আমি কোনটা নেব?’ কিন্তু এ বিশেষ টুকরোর প্রতি আকর্ষণ সবসময় ছিল না। শুরুতে সবাই পুরো মুরগিই কিনতেন। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসে। আস্ত মুরগির পরিবর্তে পছন্দসই টুকরো কেনাটাই রীতি হয়ে ওঠে।
পরে করপোরেট কোম্পানিগুলো মুরগির জীবনচক্রের ‘ডিম থেকে থালা পর্যন্ত’ সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিল। তারা শুধু মুরগি পালনের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করেনি, বরং মুরগির জিনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, খাদ্যাভ্যাস, পরিবেশগত সাড়া এবং প্রক্রিয়াজাতের প্রতিটি ধাপই তারা এমনভাবে গড়ে তোলে, যাতে সর্বোচ্চ মুনাফার নিশ্চয়তা মেলে। ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৯ দশমিক ২ বিলিয়ন ব্রয়লার মুরগি উৎপাদন হয়েছে। প্রতিটির গড় ওজন ছিল ৬ পাউন্ড বা ২ দশমিক ৭ কেজি। এ মুরগিগুলোর প্রতি পাউন্ড মাংস উৎপাদনে খরচ হয়েছে প্রায় ১ দশমিক ৮ পাউন্ড (৮২০ গ্রাম) খাদ্যশস্য, মূলত ভুট্টা।
গত ৭০ বছরে মুরগি আর আগের মতো নেই। এর প্রতিটি কোষ, পাখা, দেহের গঠন তৈরি হয়েছে লাভ আর দক্ষতার যুক্তিতে। ‘এক পাউন্ড মাংস তুলতে কতটা খাবার, পানি, বাতাস আর সময় লাগবে’—এ হিসাবের নিখুঁত গাণিতিক কাঠামোয়ই গড়ে উঠেছে আধুনিক ব্রয়লার শিল্প।
পৃথিবীতে মুরগির জাতের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক, শুনে অবাক লাগতে পারে। কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময়কর সত্য হলো আপনি যত চিকেন নাগেট, ব্রেস্ট পিস, কিংবা চিকেন নুডলস স্যুপ খেয়েছেন, তার প্রায় সবই এসেছে একটি মাত্র বিশেষ জাত কর্নিশ ও হোয়াইট রক জাতের সংকর প্রজাতি থেকে উৎপন্ন মুরগির কাছ থেকে।
বিশ্বের বৃহত্তম পোলট্রি কোম্পানিগুলোর কাছে তাদের মুরগির জেনেটিক বংশপরম্পরা কঠোরভাবে গোপন রাখা সম্পদ। তবে একটি বাণিজ্যিকভাবে বহুল ব্যবহৃত ব্রিড হলো কব ৫০০। এর উৎপত্তি হয় ১৯৪০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত এক প্রতিযোগিতা থেকে, যার নাম ছিল যথার্থই ‘চিকেন অব টুমরো’। সে প্রতিযোগিতার বিজয়ী ছিল ‘ভ্যানট্রেস’ নামের এক জাতের মুরগি, যা ১৯৫০-এর দশকে স্ট্যান্ডার্ড মিট চিকেন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।
১৯২০-এর দশকে একটি মুদি দোকানে বিক্রি হওয়া মুরগির গড় ওজন ছিল মাত্র ২ দশমিক ৫ পাউন্ড বা প্রায় ১ দশমিক ১৩ কেজি। অথচ আজকের দিনে সে গড় ওজন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬ পাউন্ড বা ২ দশমিক ৭ কেজিতে। ন্যাশনাল চিকেন কাউন্সিলের তথ্যানুযায়ী, একটি ব্রয়লার মুরগি মাত্র ৪৭ দিনেই এ ওজনে পৌঁছে যেতে পারে। এর চেয়েও কম বয়সী ও ছোট আকারের মুরগি ব্যবহার হয় ফাস্ট ফুড রেস্তোরাঁগুলোর জন্য।
কোটি কোটি ডলারের গবেষণার ফলে এখন এমন মুরগি তৈরি হয়েছে, যাদের বুকের মাংস অস্বাভাবিকভাবে বিশাল। কিন্তু এত দ্রুত মাংস গঠন করতে হলে তাদের প্রায় সারাক্ষণই খেতে হয়, ফলে তাদের চলাফেরা খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত ওজন ও অস্বস্তি থেকেই দেখা দেয় বেড়ে ওঠার যন্ত্রণা, আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় নিষ্ক্রিয়, প্রায় স্থবির এক জীবন।
পেন স্টেট এক্সটেনশনের সহযোগী অধ্যাপক ফিলিপ ক্লাওয়ার জানান, ‘আসলে এখন এমন রোবট আছে, যা চাকা লাগানো অবস্থায় মুরগির খামারে ঘুরে বেড়ায়, ক্যামেরা দিয়ে মুরগিদের পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের হাঁটতে বাধ্য করে, যাতে অন্তত কিছুটা হলেও তারা চলাফেরা করে।’
বাজারজাতের দিক থেকে সাদা পালক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ রঙিন পালকবিশিষ্ট মুরগির শরীরে থাকা ছোট পালক (পিন ফেদার) এবং ফলিকলগুলোয় রঙ লেগে থাকতে পারে, যা জবাইয়ের পর মাংসের গায়ে দাগ ফেলে। ফলাফল এ মুরগিগুলো দেখতে ‘পরিষ্কার’ লাগে না, আর রুচিশীল ও খুঁতখুঁতে ভোক্তাদের কাছে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। তাই সাদা পালকবিশিষ্ট মুরগিই বাজারে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়।
তবে অনেকের মতে, মুরগির শিল্পায়ন মানুষকে দিয়েছে প্রচুর মাংস, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে পছন্দের স্বাধীনতা। মার্কিন খাদ্য ইতিহাসবিদ রজার হোরোভিৎস বলেন, ‘আপনি যদি ১৯২০ ও ’৩০-এর দশকের রান্নার বইগুলো দেখেন, তাহলে দেখবেন এক ধরনের রান্নার জন্য মোটা মুরগি ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে, আরেক রেসিপিতে ফ্রায়ার বা ব্রয়লার। বাজারও এসব আলাদা জাতের মুরগির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করত। এখন সেসবের বালাই নেই।’
বাজার যখন ভরে উঠল এক জাতি কর্নিশ-ক্রস মুরগির একচ্ছত্র আধিপত্যে, তখনই কিছু ব্র্যান্ড নতুনভাবে বৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল—হাড্ডিবিহীন, চামড়াবিহীন কাটা মাংস, প্যাকেটজাত ও প্রসেসড প্রডাক্ট দিয়ে। এর মাধ্যমে স্বাদ বাড়ানোও সম্ভব হলো, যেহেতু এ একঘেয়ে জাতের মাংসের স্বাদ ছিল বেশ নিস্তেজ। তবে ভোক্তারা এখন চাইছেন এমন মুরগি, যা কেবল উৎপাদনের জন্য নয়, বরং পরিবেশ, নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যের প্রশ্নে টেকসই।
এরই মধ্যে বিশ্বের বড় পোলট্রি কোম্পানিগুলোর প্রজননবিদ ও জিনতত্ত্ববিদরা কর্নিশ-ক্রসের উন্নতিতে ব্যস্ত। তারা এখন শুধু দ্রুত বৃদ্ধির দিকেই নজর দিচ্ছেন না। বরং দেখছেন ২০, ৩০, এমনকি ৪০টিরও বেশি বৈশিষ্ট্য—হাড়ের গঠন, হৃৎপিণ্ডের সক্ষমতা, খাদ্যসহনশীলতা, আবহাওয়া সহনীয়তা, এমনকি খারাপ খাদ্যে বেড়ে ওঠার সক্ষমতা, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি পরীক্ষাগারে তৈরি মাংস বা কোষভিত্তিক বিকল্প প্রযুক্তির অগ্রগতি ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতা বাড়াতে পারে। কিন্তু আপাতত মুরগির দ্রুত বৃদ্ধি ও খরচ-সাশ্রয়ী উৎপাদন এ শিল্পকে একটি অপ্রতিরোধ্য অবস্থানে রেখেছে।

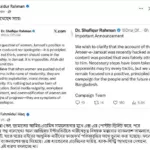




আপনার মতামত জানানঃ