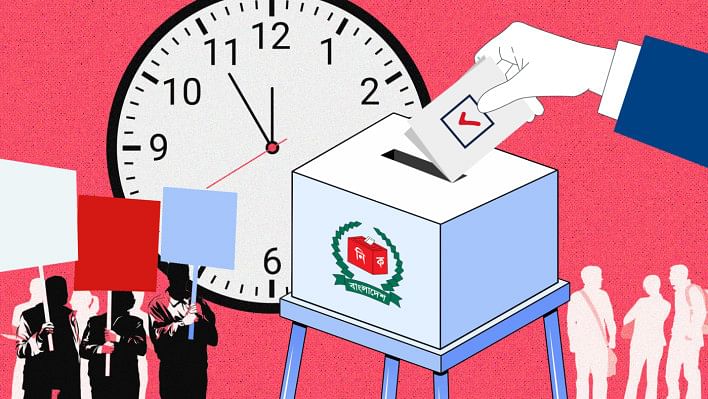
বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে অনিশ্চয়তা প্রতিদিন আরও গভীর হচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গনের কথাবার্তা, উপদেষ্টাদের ভিন্নমুখী বক্তব্য, নতুন দলগুলোর হুমকি এবং বিরোধী দলের অভিযোগ—সব মিলিয়ে জনমনে এখন এক ধরনের বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যদিও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বারবার ঘোষণা করেছেন যে ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে, তবুও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, নানা কারণে এই সময়সীমা নিয়ে সংশয় ক্রমেই বাড়ছে।
এই অনিশ্চয়তার শুরু এক ধরনের রাজনৈতিক নাটকীয়তার ভেতর দিয়েই। লন্ডনের ডরচেস্টার হোটেলে দুই নেতার বৈঠককে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বড় বাঁক বদলের সূচনা হিসেবে দেখা হয়েছিল। সেখানে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়ার ব্যাপারে একটি ধারণা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈঠকের পর যত দিন গড়িয়েছে, ততই ভোটের রোডম্যাপ নিয়ে ধোঁয়াশা বেড়েছে। এখনো স্পষ্ট করে বলা হয়নি নির্বাচনের প্রক্রিয়া কী হবে, ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হয়নি, এমনকি নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে হবে তা নিয়েও বিতর্ক থামেনি।
প্রধান উপদেষ্টা সাম্প্রতিক মালয়েশিয়া সফরে আবারও বলেছেন, তিনি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দিয়ে সরে দাঁড়াবেন। তবে তিনি সতর্কও করেছেন, সংস্কার ও বিচার ছাড়া যদি নির্বাচন হয়, তবে পুরনো সমস্যাগুলো আবার ফিরে আসবে। তাঁর মতে, অন্তর্বর্তী সরকারের তিনটি অঙ্গীকার ছিল—সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন। যদি নির্বাচন আগে করে ফেলা হয়, তবে সংস্কার ও বিচার কার্যত থেমে যাবে এবং নির্বাচিতদের হাতে চলে যাবে সবকিছু। এই বক্তব্য জনমনে নতুন এক সংশয় তৈরি করেছে।
এনসিপি-র নেতারাও একই সুরে কথা বলেছেন। নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী সোজাসাপ্টা বলেছেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হলে গণ-অভ্যুত্থানে যারা প্রাণ হারিয়েছে, তাদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে। তিনি এমনকি সরকারের কাছে শহীদদের লাশ ও বিকলাঙ্গদের অঙ্গ ফেরত দেওয়ার দাবি পর্যন্ত করেছেন। এমন বক্তব্য মানুষের মনে আশঙ্কা আরও বাড়িয়েছে। কারণ, নির্বাচন কবে হবে বা হবে না—এটি সরকারের এখতিয়ার, কোনো দলের একক সিদ্ধান্ত নয়। অথচ এই বক্তব্যগুলো জনমনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে ঘনীভূত করছে।
বিএনপি এই পরিস্থিতিকে স্বৈরাচারের পদধ্বনি বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদের মতে, ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ঠেকাতে নানা হুমকি দেওয়া হচ্ছে, যা আগের স্বৈরশাসনের মতো মনে হচ্ছে। বিএনপির শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তারা একদিকে নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টা দেখছে, অন্যদিকে ক্ষমতার খেলা চলছে বলেও ধারণা করছে।
এদিকে, নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে হবে—এ নিয়েও বিতর্ক চরমে। জামায়াতে ইসলামীসহ বেশ কিছু দল পিআর (সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি) প্রবর্তনের দাবিতে মাঠে নেমেছে। তারা মনে করে, এ পদ্ধতিতে ছোট দলগুলোরও অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। কিন্তু বিএনপি শুরু থেকেই এর বিরোধিতা করছে এবং এটিকে ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করছে। সরকার বা নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি। ফলে অনিশ্চয়তা কাটছে না, বরং জল্পনা বাড়ছে।
এই অনিশ্চয়তা আসলে অন্তর্বর্তী সরকারের মূল অঙ্গীকার নিয়েও প্রশ্ন তোলে। গণ-অভ্যুত্থানের পর সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন—এই তিনটি লক্ষ্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়েছিল। সংস্কার প্রক্রিয়া এখনো চলমান, তবে তা সম্পূর্ণ করতে একটি নির্বাচিত সরকারের প্রয়োজন। বিচার প্রক্রিয়াও সময়সাপেক্ষ। তাই প্রশ্ন ওঠে—সংস্কার ও বিচার শেষ না করে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন সম্ভব কি না? আর যদি হয়ও, তবে সেই নির্বাচন কতটা গ্রহণযোগ্য হবে?
সিনিয়র সাংবাদিক নূরুল কবীর আশঙ্কা করেছেন, বহু রাজনৈতিক শক্তি চাইছে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন না হোক। তাঁর মতে, সরকারের ভেতরেও যেনো দ্বৈততা আছে—তারা একদিকে নির্বাচনের কথা বলে, অন্যদিকে কাজকর্মে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না। ফলে হতাশা আরও বাড়ছে।
এক্ষেত্রে ড. জেকিল ও মি. হাইডের বিখ্যাত গল্পের সাযুজ্য পাওয়া যায়। যেখানে একই ব্যক্তিত্বের ভেতরে দুটি বিপরীত চরিত্র থাকে—একদিকে ভালো, অন্যদিকে মন্দ। অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতরেও একই রকম দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। বাইরে থেকে তারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কিন্তু ভেতরে নানা প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের সময় ও পদ্ধতি নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে। ফলে জনমনে বিশ্বাসযোগ্যতা কমছে।
অন্যদিকে, সময়ও দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। প্রতিশ্রুত ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের আর মাত্র পাঁচ মাস বাকি। এখনো ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হয়নি, রোডম্যাপ নেই, নির্বাচনী আইন সংশোধন সম্পূর্ণ হয়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। জুলাই সনদ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সরকারের উপদেষ্টাদের অনেকেই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগের মুখে। এই অবস্থায় নির্বাচন বিলম্বিত করার নানা আওয়াজও শোনা যাচ্ছে।
জনমনে তাই একটি বড় প্রশ্ন—সরকার কি সত্যিই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত, নাকি সময়ক্ষেপণ করছে? যদি নির্বাচন বিলম্বিত হয়, তবে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হতে পারে, যা দেশের জন্য শুভ হবে না।
সংস্কার ও বিচার সম্পন্ন না করে নির্বাচন হলে দেশ আবারও পুরনো পথে হাঁটতে পারে—ড. ইউনূসের এই সতর্কবাণী হয়তো বাস্তবতার প্রতিফলন। তবে নির্বাচন বিলম্বিত হলে একইভাবে সংকট বাড়বে। একদিকে সংস্কার ও বিচার অসম্পূর্ণ থাকবে, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে।
সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন এক জটিল রাজনৈতিক দোলাচলে দাঁড়িয়ে। নির্বাচন নিয়ে অবিশ্বাস ও সংশয় প্রতিদিন বাড়ছে, অথচ এর সমাধান দেওয়ার দায়িত্ব সরকারেরই। সরকার যদি স্পষ্ট রোডম্যাপ, সময়সূচি ও পদ্ধতি জানায়, তবে হয়তো এই সংশয় কেটে যাবে। কিন্তু যত দিন তা না হয়, তত দিন জনমনে ড. জেকিল ও মি. হাইডের দ্বন্দ্বই চলতে থাকবে—একদিকে আশা, অন্যদিকে গভীর অনিশ্চয়তা।






আপনার মতামত জানানঃ