
বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকদিন পর আবার একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে—বিশেষ করে মুদ্রাবাজারে। ডলারের বিপরীতে টাকার দর বাড়তে শুরু করেছে, আর এই ঘটনাটিকে অর্থনীতিবিদরা দেখছেন একটি বড় ধরনের ইতিবাচক সিগনাল হিসেবে। দীর্ঘ সময় ধরে টাকার অবমূল্যায়নের ফলে দেশের অর্থনীতি চাপের মুখে ছিল। বিশেষ করে আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে মূল্যস্ফীতি আকাশছোঁয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি, বিদেশি ঋণের সহজলভ্যতা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু সাহসী নীতিগত পদক্ষেপের কারণে এখন আবার ডলার-টাকা বিনিময় হার স্থিতিশীলতার দিকে এগোচ্ছে।
মাত্র সাত কর্মদিবসেই ডলারের দর কমেছে প্রায় ২ টাকা ৪০ পয়সা, যা এক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় দরপতন। বর্তমানে আন্তঃব্যাংকে প্রতি ডলার ১২০ টাকা ৩০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষে যেখানে এই দর ১২২ টাকারও বেশি ছিল, সেখানে ২০২৫ সালের জুলাইয়ে এসে টাকার এই ফিরে আসা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।
এই পরিবর্তনের পেছনে অন্যতম কারণ হলো, সরকার পতনের পর প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সের রেকর্ড প্রবৃদ্ধি। যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স ছিল ২৩৯১ কোটি ডলার, সেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা প্রায় ২৭ শতাংশ বেড়ে ৩০৩৩ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। এই বাড়তি রেমিট্যান্স সরাসরি ডলারের জোগান বাড়িয়েছে, ফলে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি হওয়ায় ডলারের দর কমেছে।
অন্যদিকে রপ্তানিও আগের চেয়ে ভালো হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, রপ্তানি আয়েও ভালো প্রবৃদ্ধি এসেছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, এআইআইবি, জাইকা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে পাওয়া ৫ বিলিয়নেরও বেশি ডলারের ঋণ ডলার বাজারে স্বস্তি এনে দিয়েছে। এই ঋণ সহায়তার কারণে জুন শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে হয়েছে ৩১.৭১ বিলিয়ন ডলার, যেখানে একসময় তা নেমে গিয়েছিল ২০ বিলিয়নের নিচে।
একসময় বাংলাদেশ ব্যাংক কৃত্রিমভাবে ডলারের দর ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল—প্রতি ডলার ৮৪ থেকে ৮৫ টাকায় আটকে রাখা হয়েছিল, যা পরে ২০২১ সালের পর ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে। কিন্তু এই কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে পারেনি। বরং এতে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, যা শেষ পর্যন্ত টেকসই হয়নি। এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিনিময় হারকে অধিকতর বাজারমুখী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এই বাজারভিত্তিক হার বাস্তবায়নের পথে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ২০২৩ সালের মে মাসে ‘ক্রলিং পেগ’ চালু করা। এতে প্রতিদিন বিনিময় হার সামান্য পরিবর্তনের সুযোগ থাকায় ডলারের মূল্য ধীরে ধীরে সামঞ্জস্য করা সহজ হয়। এরপর শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সময় হঠাৎ দর বেড়ে গেলেও পরে তা আবার নিয়ন্ত্রণে আসে। নতুন গভর্নরের অধীনে আরও নমনীয়তা আনা হয়—১১৭ টাকার মধ্যবর্তী দর থেকে আড়াই শতাংশ কম-বেশি করার সুযোগ দেওয়া হয়, যা পরে ১২২ টাকায় গিয়ে পৌঁছায়।
মূলত রেমিট্যান্সের ধারাবাহিক উন্নতি, ডলার সরবরাহ বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক ঋণ সহায়তা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বাজারমুখী নীতির ফলে এখন টাকার মূল্যবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। আবার রপ্তানি বাড়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা আয় আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, ডলারের দাম কমার সরাসরি প্রভাব পড়বে আমদানি মূল্য ও মূল্যস্ফীতিতে। যদি বর্তমান প্রবণতা বজায় থাকে, তাহলে নিত্যপণ্যের দাম কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে, যা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য বড় ধরনের স্বস্তি হবে।
তবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা সতর্ক করে বলছেন, শুধু বিনিময় হার কমানো বা রেমিট্যান্স বাড়ানোই যথেষ্ট নয়—অর্থপাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। অতীতে দেখা গেছে, রপ্তানি ও আমদানির আড়ালে বহু অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে, যা রিজার্ভ হ্রাস ও টাকার অবমূল্যায়নে বড় ভূমিকা রেখেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ সালে আমদানি ৩৬ শতাংশ বেড়ে প্রায় ৯ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছেছিল, যার পেছনে প্রকৃত চাহিদার চেয়ে বেশি ছিল অর্থ পাচার।
এই বাস্তবতায় বাংলাদেশ ব্যাংককে আরও শক্তিশালী মনিটরিং ও রেগুলেশন নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি হুন্ডির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, রেমিট্যান্স প্রেরণে ইনসেনটিভ ও ব্যাংকিং চ্যানেলকে আরও সহজলভ্য করার পদক্ষেপ নিতে হবে। এভাবে একদিকে ডলারের জোগান বাড়বে, অন্যদিকে অর্থপাচার কমবে।
সব মিলিয়ে, এখনকার বাজারচিত্র বলছে—টাকা আবার শক্তি ফিরে পাচ্ছে। এটা এক অর্থে সরকারের জন্য স্বস্তিদায়ক হলেও, বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই স্থিতিশীলতা ধরে রাখা। কারণ বৈশ্বিক অর্থনীতি এখনও অনিশ্চয়তায় ঘেরা, আর রাজনৈতিক অস্থিরতা বা দুর্নীতি বেড়ে গেলে এই সুফল দ্রুত হারিয়ে যেতে পারে। তাই সময় এসেছে স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল এবং সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থিতিশীল মুদ্রানীতি নিশ্চিত করার। তাহলেই কেবল টাকার এই পুনরুত্থান স্থায়ী রূপ পাবে এবং দেশের সার্বিক অর্থনীতিও নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে।


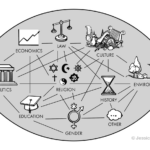



আপনার মতামত জানানঃ