 রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি নিয়ে ভারতের যে ‘জেদি আত্মবিশ্বাস’ গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছিল, সেটায় বড় ধাক্কা দিলো রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শুল্ক আরোপের চাপের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি বন্ধ করল ভারতের এই বৃহত্তম বেসরকারি জ্বালানি কোম্পানি। সংবাদমাধ্যমের ভাষায়, এ যেন শেষ পর্যন্ত মার্কিন চাপে ভারতের নতি স্বীকারই। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে নয়াদিল্লি এখনো নিজেদের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ও জ্বালানি নিরাপত্তার যুক্তি তুলে ধরছে, তবু এই ঘটনাকে অনেকেই ভারতের বাস্তবধর্মী সমন্বয়–রাজনীতির ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন।
রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি নিয়ে ভারতের যে ‘জেদি আত্মবিশ্বাস’ গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছিল, সেটায় বড় ধাক্কা দিলো রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শুল্ক আরোপের চাপের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি বন্ধ করল ভারতের এই বৃহত্তম বেসরকারি জ্বালানি কোম্পানি। সংবাদমাধ্যমের ভাষায়, এ যেন শেষ পর্যন্ত মার্কিন চাপে ভারতের নতি স্বীকারই। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে নয়াদিল্লি এখনো নিজেদের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ও জ্বালানি নিরাপত্তার যুক্তি তুলে ধরছে, তবু এই ঘটনাকে অনেকেই ভারতের বাস্তবধর্মী সমন্বয়–রাজনীতির ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন।
ইউক্রেন যুদ্ধে রুশ তেলের ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা জোরদার হওয়ার পর থেকেই ভারত নতুন এক সুযোগ দেখে। যুদ্ধের আগে ভারতের মোট তেল আমদানির মাত্র সাড়ে ২ শতাংশ আসত রাশিয়া থেকে; কিন্তু ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সেই হার বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৫ দশমিক ৮ শতাংশে। এত বড় উত্তরণ শুধু সংখ্যার খেলা নয়, ভারতের অর্থনীতির জন্যও তা ছিল গেমচেঞ্জার। তুলনামূলক সস্তা রুশ তেল শোধন করে আবার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে ভারত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে; পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানি দামের ওপর চাপ কম রাখতেও এটি সহায়তা করেছে। ফলে পশ্চিমা অসন্তোষ সত্ত্বেও ভারত বারবারই বলেছে—তারা নিজেদের জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে, কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না।
কিন্তু একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রও হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। রাশিয়ার প্রধান তেল উৎপাদনকারী সংস্থা রোসনেফট ও লুকোইলের ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা জোরদার করেছে ওয়াশিংটন। শুধু তাই নয়, মার্কিন প্রশাসন ভারতের ওপরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে—প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত আগস্টে আরোপিত ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্কের মধ্যে ২৫ শতাংশই ছিল রাশিয়া থেকে তেল ও অস্ত্র কেনার ‘শাস্তি’ হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি, এই কেনাকাটার মাধ্যমে মস্কোকে ইউক্রেন যুদ্ধে অর্থায়নের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ভারত অবশ্য শুরুতে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপকে এক ধরনের একতরফা চাপ হিসেবেই তুলে ধরেছে।
এই টানাপোড়েনের মধ্যেই মূল নাটকের কেন্দ্রে আসে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ। ভারতের বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী এবং অন্যতম বড় রিফাইনার হিসেবে রিলায়েন্সই রুশ তেলের প্রায় ৫০ শতাংশ আমদানি করছিল বলে উল্লেখ আছে প্রতিবেদনে। অর্থাৎ রাশিয়া–ভারত তেল বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি ছিল এই একটি কোম্পানি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যখন রোসনেফট ও লুকোইলের ওপর আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা চাপায় এবং ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হতে যাওয়া পণ্য আমদানিসংক্রান্ত বিধিনিষেধ ঘোষণা করে, তখন রিলায়েন্সের সামনে ‘বিকল্পহীন’ এক বাস্তবতা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত কোম্পানিটি সিদ্ধান্ত নেয়—রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি বন্ধ করা হবে, এবং তা নির্ধারিত সময়ের আগেই বাস্তবায়ন করবে, যাতে নতুন বিধিনিষেধ পুরোপুরি মানা যায়।
রিলায়েন্স এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা আসন্ন বিধিনিষেধের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখতে চায় এবং সে কারণেই এই পরিবর্তন আগে থেকেই কার্যকর করা হয়েছে। ব্যবসায়িক ভাষায় এটি ‘কমপ্লায়েন্স’ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ; কিন্তু কূটনৈতিক ভাষায় এই পদক্ষেপের অর্থ ভিন্ন মাত্রা পায়। কারণ, ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না বললেও, দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী করপোরেট গ্রুপ যখন রুশ তেল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়, তখন আন্তর্জাতিক মহলে সেটাকে ভারতের কৌশলগত ঝোঁক পরিবর্তনের এক প্রকার ইঙ্গিত হিসেবেই পড়া হয়। হোয়াইট হাউসও রিলায়েন্সের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে প্রায় একই বার্তা দিয়েছে—ভারত অন্তত আংশিকভাবে হলেও যুক্তরাষ্ট্রের নীতি–অবস্থানের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিচ্ছে।
এখন প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক—রিলায়েন্সের এই পদক্ষেপ ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে? যুদ্ধপরবর্তী সময়ে সস্তা রুশ তেল ভারতের জন্য ছিল এক বড় ‘সেফটি ভাল্ভ’। আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ওঠানামা, মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা কিংবা পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়ার মাঝেও রুশ তেলই ভারতের রিফাইনারিগুলোকে দাম কম রাখতে সহায়তা করেছে। রিলায়েন্স বা অন্য কোনো রিফাইনার যদি রুশ তেল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদের বিকল্প হিসেবে আবারও মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাষ্ট্র বা আফ্রিকার বিভিন্ন উৎসের দিকে ঝুঁকতে হবে। এতে সরবরাহের ঝুঁকি না বাড়লেও, তুলনামূলক দামের চাপ বাড়তে পারে; শোধনাগারের মুনাফা কমতে পারে; শেষ পর্যন্ত ভোক্তার পকেটেও তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
তবে ভারতের দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক নীতি ‘স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি’ বা কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের আলোকে এই সিদ্ধান্তকে এককভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন। একদিকে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি ও বাণিজ্য সহযোগিতা বাড়াচ্ছে; অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গেও ঐতিহাসিক সামরিক ও জ্বালানি অংশীদারত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছে। এমন এক সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে কোনো পক্ষকে পুরোপুরি ‘খুশি’ রাখা সম্ভব নয়। ফলে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, রিলায়েন্স ইস্যুটিকে ভারত এক ধরনের ‘সিলেক্টিভ ব্যালান্সিং’ হিসেবে ব্যবহার করছে—সরাসরি রাষ্ট্রীয় ঘোষণা না দিয়ে বেসরকারি কোম্পানির সিদ্ধান্তের আড়ালে দিয়ে আংশিকভাবে মার্কিন উদ্বেগ দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
অবশ্য এটাও ঠিক, কেবল মার্কিন চাপের কথাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে এমন নয়; ব্যবসায়িক ঝুঁকিও বড় বিষয়। যুক্তরাষ্ট্র তার নিষেধাজ্ঞার আওতা শুধু রুশ কোম্পানির ওপরই সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং যারা এসব কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করবে, তাদের ওপরও গৌণ নিষেধাজ্ঞার হুমকি তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং, বীমা, জাহাজ চলাচল—এ সবকিছুই আজ পরস্পর জড়িত। একটি বড় রিফাইনারি যদি এমন ঝুঁকিপূর্ণ তেল কিনতে থাকে, তবে তার বৈশ্বিক অর্থায়ন ও বাণিজ্যিক অংশীদাররা যে ঝুঁকিতে পড়বে, তা অনুধাবন করতে রিলায়েন্সকে খুব বেশি সময় নিতে হয়নি। তাই অনেকে বলছেন, এটি যতটা না রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, তার চেয়েও বেশি ব্যবসায়িক হিসাব–নিকাশের ফল।
রাশিয়ার জন্যও এই সিদ্ধান্ত ছোট ধাক্কা নয়। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যখন ইউরোপ রুশ তেল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন এশিয়ার দিকে ঝুঁকে মস্কো নতুন বাজার তৈরি করতে চায়। চীন ও ভারতের মতো জনবহুল দেশগুলো সেই সময়ে রাশিয়ার বড় ভরসা হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের আমদানি বাড়তে বাড়তে যখন ৩৫ শতাংশের ঘরে পৌঁছায়, তখন রুশ অর্থনীতিও কিছুটা স্বস্তি পায়। কিন্তু বড় ক্রেতা হিসেবে যদি রিলায়েন্সের মতো প্রতিষ্ঠান সরে যায়, কিংবা অন্য ভারতীয় রিফাইনারিগুলোও ধীরে ধীরে সেই পথে হাঁটে, তাহলে রাশিয়াকে আবারও নতুন ক্রেতা খুঁজতে হবে—অথবা আরও বেশি ছাড় দিয়ে পুরনো ক্রেতাদের ধরে রাখতে হবে। তেলের বিশ্ববাজারে এর প্রভাবও তাই কেবল ভারত–যুক্তরাষ্ট্র–রাশিয়া ত্রিভুজে সীমাবদ্ধ থাকবে না।
ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এই ঘটনাটি আলোচনার জন্ম দিতে পারে। একপক্ষে থাকতে পারে সেই শক্তি, যারা বলবে—যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ভারতের ‘স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি’ প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে; অন্যদিকে আরেক পক্ষ যুক্তি দেবে—বিশ্ব বাস্তবতায় অন্ধ জেদ ধরে রাখার চেয়ে সময়োপযোগী সমন্বয়–রাজনীতিই বেশি বুদ্ধিমানের কাজ। আবার ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ কেউ হয়তো বলবে, রাষ্ট্র যা-ই বলুক, একটি বেসরকারি কোম্পানি সবসময়েই নিজের ঝুঁকি–লাভের সমীকরণ অনুযায়ী পথ বেছে নেবে; সেখানে জাতীয়তার আবেগের জায়গা সীমিত। ফলে ‘নতি স্বীকার’ না ‘ব্যবহারিক সমঝোতা’—এই বিতর্কও ভবিষ্যতে ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে আলোচ্য হয়ে থাকতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদে প্রশ্ন হলো, ভারতের জ্বালানি কৌশল কোন পথে এগোবে। সস্তা রুশ তেলের সুবিধা হারালে, হয়তো নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর যুক্তিও আরও জোরালো হবে। আবার যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলো যদি ভারতের ওপর চাপ কমিয়ে সহযোগিতা বাড়ায়—যেমন প্রযুক্তি স্থানান্তর, বিনিয়োগ বা গ্যাস–ভিত্তিক অবকাঠামোতে সহায়তা—তাহলে ভারতও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু একই সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে পুরোনো প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন করার মতো অবস্থায়ও ভারত যেতে চাইবে না—এটাও বাস্তবতা।
শেষ পর্যন্ত এই ঘটনাকে দেখা যায় বিশ্বের বড় শক্তিগুলোর চাপ–প্রতিচাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক উদীয়মান শক্তির বাস্তবতা হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্র নিজস্ব ভূরাজনৈতিক স্বার্থে নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে; রাশিয়া যুদ্ধের অর্থনীতি টিকিয়ে রাখতে বিকল্প বাজার খুঁজছে; আর ভারত চেষ্টা করছে এ দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব নিজের জাতীয় স্বার্থটুকু নিশ্চিত করতে। রিলায়েন্সের রুশ তেল আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্ত তাই শুধু একটি কোম্পানির ব্যবসায়িক ঘোষণা নয়, বরং এই বৃহত্তর শক্তির খেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত। আগামী দিনে অন্য ভারতীয় রিফাইনাররা কী পথ বেছে নেয়, যুক্তরাষ্ট্র কতটা কঠোর থাকে, আর রাশিয়া কতটা ছাড় দিতে রাজি হয়—সব মিলিয়ে গড়ে উঠবে এক নতুন জ্বালানি–ভূরাজনীতি, যার কেন্দ্রবিন্দুতে ভারতকে রাখতেই চাইছে সবাই।


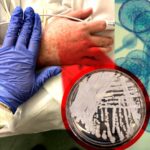



আপনার মতামত জানানঃ