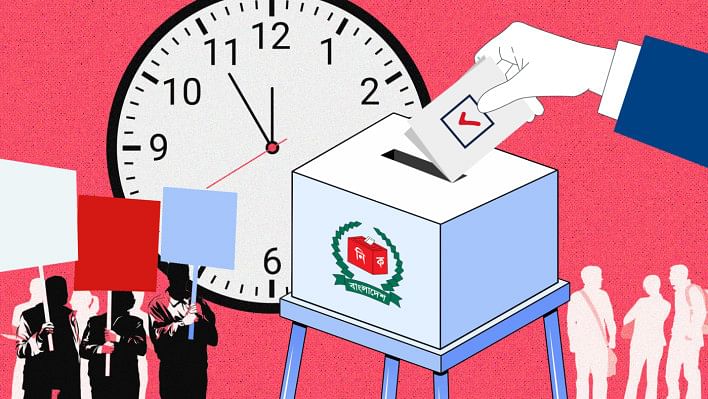
বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচন সবসময়ই সবচেয়ে আলোচিত এবং বিতর্কিত একটি ইস্যু। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে প্রচলিত পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণের জন্য। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন করে আলোচনায় এসেছে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর) পদ্ধতি। জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দল দাবি তুলেছে যে এবারের নির্বাচন এই পদ্ধতিতেই হওয়া উচিত। কিন্তু নির্বাচন কমিশন ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাতে থাকা সীমিত সময়ে এটি বাস্তবায়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এই বিতর্ককে ঘিরে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তৈরি হয়েছে নানামুখী আলোচনা এবং প্রশ্ন উঠছে, আসলেই কি ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পিআর ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব?
বাংলাদেশে বর্তমানে যে ভোট ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সেটি হলো ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট বা এফপিটিপি পদ্ধতি। এ ব্যবস্থায় প্রতিটি আসনে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীই বিজয়ী হন। ফলে কখনও কখনও দেখা যায় একজন প্রার্থী মোট ভোটের অর্ধেকেরও কম পেয়ে সংসদে প্রবেশ করেন এবং সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি হয় ভোটের সামগ্রিক চিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে। সমালোচকরা বলেন, এতে অনেক ভোট নষ্ট হয়, জনগণের প্রকৃত মতামত প্রতিফলিত হয় না। অপরদিকে, প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা পিআর পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মোট প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে সংসদে আসন ভাগ করে নেয়। এতে ছোট রাজনৈতিক দলগুলোও সুযোগ পায় সংসদে প্রবেশ করার, ফলে জনগণের ভোট তুলনামূলকভাবে সমানভাবে প্রতিফলিত হয়।
জামায়াতে ইসলামী দীর্ঘদিন ধরেই এই পদ্ধতির দাবি জানিয়ে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে তারা আরও সরব হয়েছে এবং জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ কয়েকটি ছোট দল তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। জামায়াতের নেতারা বলছেন, জনগণের ভোটের সঠিক প্রতিফলনের জন্য পিআর পদ্ধতি জরুরি। তাদের মতে, এক মাসেই প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন সম্ভব যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে। নির্বাচন কমিশন প্রধান যখন বললেন যে আরপিওতে পিআরের কোনো বিধান নেই, তখন জামায়াত তার সমালোচনা করে বলেছে সিইসি নাকি একটি দলের মতো কথা বলছেন। দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলছেন, সংবিধান ও আরপিও উভয়ই সংশোধনযোগ্য, চাইলে দ্রুতই পরিবর্তন আনা যায়।
তবে বিএনপি, দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেনি। তারা প্রচলিত সংসদীয় ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে একদিকে জামায়াত ও ছোট দলগুলো পিআরের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে বিএনপি ও অন্যান্য বড় দল প্রচলিত ব্যবস্থার পক্ষে। এই বিভক্ত অবস্থার কারণে কোনো ঐকমত্য তৈরি হয়নি। আর নির্বাচনের আগে এই ঐকমত্য না হলে পদ্ধতি পরিবর্তনের বাস্তব সুযোগ থাকে না।
নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব জেসমিন টুলি মনে করেন, পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য শুধু সংবিধান সংশোধন নয়, আরও অনেক ধাপ পেরোতে হবে। প্রথমত, সংসদ প্রতিষ্ঠার বিধান সংবলিত সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে বিধিমালা তৈরি করতে হবে। তৃতীয়ত, নির্বাচনী কর্মীদের নতুনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন হবে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, সাধারণ মানুষকে নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ এফপিটিপি ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত, তারা নিজের এলাকার প্রার্থীকে ভোট দিতে অভ্যস্ত। কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে ভোটের ধরন একেবারেই আলাদা, যেখানে দলীয় ভোটকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পরিবর্তন জনগণকে বুঝিয়ে বলা এবং গ্রহণযোগ্য করে তোলা একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। জেসমিন টুলির মতে, পুরো সিস্টেম সাজাতে দেড় বছরের কম সময়ে শেষ করা সম্ভব নয়। তাই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হলে সেখানে পিআর প্রয়োগ কোনোভাবেই সম্ভব নয়।
অন্যদিকে জামায়াতের নেতারা এসব যুক্তি মানতে নারাজ। তাদের মতে, আইনের জটিলতা অজুহাত মাত্র। তারা মনে করে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এক মাসেই সব সম্ভব। আন্দোলনের মাধ্যমে তারা জাতিকে বোঝাতে চাইছে যে তাদের দাবি যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত। এজন্য তারা যুগপৎ কর্মসূচি, আলোচনার আয়োজন, সংবাদমাধ্যমে প্রচারণা চালাচ্ছে। তাদের বক্তব্যে স্পষ্ট যে, তারা পিআরের দাবিকে একটি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেও ব্যবহার করছে যাতে জনসমর্থন বাড়ানো যায়।
বাংলাদেশে পিআর পদ্ধতির দাবি নতুন নয়। আগে থেকেই বিভিন্ন ছোট দল এই দাবি তুলেছে। তবে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর এই দাবি নতুন করে শক্তি পায়, বিশেষত তরুণদের নেতৃত্বে গঠিত দলগুলো এটি সামনে নিয়ে আসে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের অনেকেই এফপিটিপি পদ্ধতির সমালোচনা করে বলছে যে এতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিফলন ঘটে না। তাদের মতে, পিআর চালু হলে নতুন নেতৃত্বের উত্থানের সুযোগ তৈরি হবে। তবে অন্য একটি অংশ বলছে, এতে সংসদে ছোট ছোট অনেক দল প্রবেশ করবে, ফলে সরকার গঠন ও পরিচালনায় অস্থিরতা বাড়বে।
আন্তর্জাতিক পরিসরেও দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা। যুক্তরাজ্যের মতো অনেক দেশ এখনো এফপিটিপি ব্যবস্থা বজায় রেখেছে। আবার জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশগুলো পিআর পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। যেসব দেশে বহুদলীয় রাজনীতি শক্তিশালী এবং জোট সংস্কৃতি সুসংহত, সেখানে পিআর পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে কার্যকর। কিন্তু যেখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সমঝোতার অভাব, সেখানে পিআর ব্যবস্থা অনেক সময় অচলাবস্থা তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে মেরুকরণ আছে, সেখানে এই আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
সব মিলিয়ে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, আসন্ন ফেব্রুয়ারির মধ্যেই কি পিআর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন সম্ভব? নির্বাচন কমিশন ও বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আইনগত, প্রশাসনিক এবং সামাজিক দিক থেকে এটি অসম্ভব। হাতে থাকা সময়ের মধ্যে সংবিধান সংশোধন, নতুন আইন, বিধিমালা প্রণয়ন, জনবল প্রশিক্ষণ ও জনগণকে সচেতন করার মতো বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং বাস্তবতার বিচারে ফেব্রুয়ারিতে পিআর চালু করা একেবারেই অবাস্তব।
তবে জামায়াত ও কয়েকটি দল এখনো এই দাবি থেকে সরে আসতে রাজি নয়। তারা আন্দোলন চালিয়ে যেতে চায়, আলোচনার পথ খোলা রাখতে চায় এবং জনগণের মাঝে এই ইস্যু নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে চায়। তাদের লক্ষ্য কেবল পিআর চালু করা নয়, বরং একটি রাজনৈতিক এজেন্ডা হিসেবে এটিকে সামনে রেখে জনমত নিজেদের দিকে টেনে নেওয়া।
বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বনাম প্রচলিত ভোট পদ্ধতির বিতর্ক অনেক পুরনো। তবে আসন্ন নির্বাচনের আগে এটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। যদিও বাস্তবতায় ফেব্রুয়ারিতে এই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়, তবুও এই বিতর্ক ভবিষ্যতের রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ একদিকে জনগণের একাংশ আনুপাতিক ব্যবস্থার পক্ষে ক্রমেই সোচ্চার হচ্ছে, অন্যদিকে বড় দলগুলো এফপিটিপি ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরছে। ফলে আগামী বছরগুলোতে এই ইস্যু নিয়ে আরও তীব্র রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, দলগুলোর ঐকমত্যের অভাব, আইনগত কাঠামোর জটিলতা এবং সময়ের সীমাবদ্ধতা—সব মিলিয়ে ফেব্রুয়ারিতে পিআর চালু করার সম্ভাবনা কার্যত নেই। কিন্তু দাবি অস্বীকার করা যাচ্ছে না যে এটি এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত হয়েছে। জনগণের ভোটের প্রকৃত প্রতিফলন নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা নিয়ে যেসব প্রশ্ন উঠছে, আনুপাতিক পদ্ধতি তারই অংশ। তাই হয়তো এই নির্বাচনে নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে এ নিয়ে আরও গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে বাংলাদেশের রাজনীতিকে।




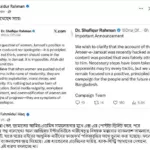

আপনার মতামত জানানঃ