
বাংলাদেশের মানুষের আবেগ, সংস্কৃতি ও ভোজনের ইতিহাসে ইলিশ মাছের জায়গা একেবারেই আলাদা। বর্ষা-শরতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়ার দৃশ্য একসময় নদী তীরের মানুষের কাছে ছিল উৎসবের মতো। ঘরে ঘরে ধোঁয়া ওঠা পাতিল, নতুন ইলিশ ভাজার গন্ধ আর খাওয়া-দাওয়ার আড্ডা বাঙালির চিরচেনা ছবির অংশ। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেই আনন্দ যেন কেবল স্মৃতিতেই আটকে যাচ্ছে। একদিকে উৎপাদন কমছে, অন্যদিকে দাম আকাশচুম্বী। এর মধ্যেই সরকার প্রতিবছর দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেয়। এ বছরের রপ্তানি নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও প্রশ্ন বাড়ছে—কীভাবে দেশের বাজারে পাইকারি দরে যে ইলিশ ১৭৮৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, সেটিই ভারতে রপ্তানি হচ্ছে ১৫২৫ টাকায়? এ বৈপরীত্যের আড়ালে চলছে কি কোনো অনিয়ম, নাকি অর্থপাচারের নতুন কৌশল—এ নিয়েই জোরালো আলোচনা।
বরিশালের পোর্ট রোড ও বরগুনার পাথরঘাটা মোকামে পাইকারি ব্যবসায়ীরা স্পষ্ট বলছেন, হিসাব মেলানো যায় না। কারণ, বাজারে মাছের যোগান কম। মৌসুমে যেখানে প্রতিদিন দুই-তিন হাজার টন ইলিশ আসে, সেখানে এবার দিনে একশ টনও আসছে না। এমন পরিস্থিতিতে রপ্তানিকারকরা যখন বাজার থেকে ইলিশ সংগ্রহ করেন, তখন দেশীয় বাজারে মাছের সংকট আরও বেড়ে যায় এবং দাম নাগালের বাইরে চলে যায়। অথচ সরকারি কাগজে-কলমে রপ্তানি মূল্য ধরা হয়েছে কেজিপ্রতি মাত্র ১২ দশমিক ৫০ ডলার, অর্থাৎ ১৫২৫ টাকা। ফলে দেখা যাচ্ছে, ব্যবসায়ীরা বেশি দামে কিনে কম দামে রপ্তানি করছেন। এতে তারা লোকসান দিচ্ছেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ বলছেন, আসলে কাগজে লোকসান হলেও গোপনে বাড়তি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে আদান-প্রদান হচ্ছে। এই বাড়তি অর্থের হিসাব কাগজে ধরা পড়ে না। ফলে সরকার যেমন রাজস্ব হারাচ্ছে, তেমনি বাজারেও তৈরি হচ্ছে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি।
স্থানীয় জেলে, আড়তদার ও ভোক্তাদের মধ্যে তাই ক্ষোভ চরমে। বরগুনার ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরীর মতো অনেকে বলেছেন, “দেশে বেশি দামে কিনে কীভাবে কম দামে রপ্তানি হচ্ছে—এটা রহস্যজনক।” তাঁদের মতে, বিষয়টি শুধু ব্যবসায়িক লাভ-লোকসানের হিসাব নয়; বরং এর সঙ্গে জড়িত আছে রাজনৈতিক প্রভাব ও শক্তিশালী সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ। আসলে ইলিশ রপ্তানি কখনোই পুরোপুরি অর্থনৈতিক যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না। কারণ, যেই মাছ দেশের সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, সেই মাছই আবার সীমান্ত পেরিয়ে যাচ্ছে সস্তায়।
এই প্রেক্ষাপটে রপ্তানিকারকদের পরিচয় নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এ বছর রপ্তানির অনুমতি পাওয়া ৩৭ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বরিশালের চারটি প্রতিষ্ঠান একই ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে। তিনি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী এবং দীর্ঘদিন ধরেই ইলিশ রপ্তানির সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত। অতীতে রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গেই রপ্তানির অনুমতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। সরকার পরিবর্তন হলেও এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দখল খুব একটা বদলায় না। এবারও একই ছবি দেখা যাচ্ছে। বরিশালের মোকামে ব্যবসায়ীরা বলছেন, এ রপ্তানি কার্যত একজনের হাতেই কেন্দ্রীভূত। এর ফলে বাজারের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা ভেঙে যাচ্ছে, আর ইলিশ নিয়ে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ আরও জোরালো হচ্ছে।
এদিকে ভোক্তাদের অবস্থাও দুঃসহ। মৌসুমেও খুচরা বাজারে ইলিশের দাম এত বেশি যে সাধারণ পরিবার হাত বাড়াতে পারছে না। বরিশালের এক চাকরিজীবী জানান, পরিবারে ইলিশ খাওয়ার আবদার থাকলেও বাজারে গিয়ে দাম শুনে ফিরতে হয়েছে খালি হাতে। তাঁর মতো অনেকেই ভাবছিলেন, মৌসুমের শেষ দিকে হয়তো দাম কিছুটা কমবে। কিন্তু তার আগেই সরকার রপ্তানির ঘোষণা দেওয়ায় হতাশা আরও বেড়েছে। ভোক্তা অধিকার সংগঠন ক্যাব বলছে, সরকারের উচিত ছিল প্রথমে দেশের মানুষের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, তারপর রপ্তানির কথা ভাবা। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে উল্টোটা—দেশের বাজারে সংকট থাকা সত্ত্বেও ইলিশ রপ্তানি চলছে।
অর্থনৈতিক দিক থেকে বিষয়টি আরও জটিল। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নির্ধারিত দামে রপ্তানি দেখালেও বাস্তবে ভারতীয় বাজারে ইলিশ বিক্রি হয় স্থানীয় দরে। সেখানকার ব্যবসায়ীরা বাড়তি অর্থ পরিশোধ করেন নগদে বা হুন্ডির মাধ্যমে। ফলে সরকার যে ন্যূনতম দরে রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ করেছে, কাগজে সেই টাকাই ব্যাংকের মাধ্যমে আসে। কিন্তু অতিরিক্ত লেনদেনের কোনো সরকারি হিসাব নেই। শুধু এ বছরের অনুমোদিত ১২০০ মেট্রিক টনের আড়ালে যদি কেজিপ্রতি ২৬৩ টাকা বাড়তি হিসাব ধরা হয়, তবে প্রায় ৩১ কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেন হতে পারে। অর্থনীতিবিদদের মতে, এভাবে অর্থপাচারের পথ প্রশস্ত হচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর।
এমন প্রশ্ন নতুন নয়। ২০১৯ সালে যখন প্রথম ইলিশ রপ্তানি শুরু হয়, তখন থেকেই বিতর্ক চলছিল। সরকারের যুক্তি ছিল, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ইলিশের চাহিদা প্রবল, আর সীমিত পরিমাণ রপ্তানির মাধ্যমে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কেরও উন্নতি হবে। কিন্তু সমালোচকেরা বলেছিলেন, এতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হবে। পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দেশের মোট উৎপাদনের খুব সামান্য অংশ রপ্তানি হলেও বাজারে এর প্রভাব যথেষ্ট। কারণ, উৎপাদন ক্রমেই কমছে। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২–২৩ অর্থবছরে যেখানে ৫ লাখ ৭১ হাজার টন ইলিশ ধরা হয়েছিল, সেখানে ২০২৩–২৪ অর্থবছরে কমে দাঁড়ায় ৫ লাখ ২৯ হাজার টনে। ধারাবাহিকভাবে দুই বছর ধরে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় বাজারে সরবরাহ কমে গেছে। এর মধ্যে আবার রপ্তানি চাপ তৈরি করছে।
একজন অর্থনীতিবিদের ভাষায়, “সরকার ইলিশকে শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের খাত হিসেবে দেখছে, কিন্তু সামাজিক প্রভাবের দিকটা উপেক্ষা করছে।” আসলে ইলিশ শুধু একটি মাছ নয়; এটি জাতীয় পরিচয়ের অংশ। ফলে যখন দেশের মানুষ ইলিশ কিনতে পারছে না, অথচ সেটি রপ্তানি হচ্ছে, তখন ক্ষোভ জমাট বাঁধে। এর সঙ্গে যখন অনিয়ম, হুন্ডি ও রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ যুক্ত হয়, তখন সরকারের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে।
তবে সমর্থকেরা বলেন, রপ্তানির পরিমাণ এত কম যে এর প্রভাব তেমন বড় নয়। গত বছর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩৯৫০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিলেও বাস্তবে গেছে মাত্র ৮০২ টন। দেশের মোট উৎপাদনের তুলনায় এই পরিমাণ শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশেরও কম। ফলে বাস্তব সংকট অন্য জায়গায়—উৎপাদন কমে যাওয়া, পরিবহন ও সংরক্ষণে দুর্বলতা, আর বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা। তারা মনে করেন, রপ্তানি বন্ধ করলেও দাম কমবে না।
কিন্তু সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। তারা দেখছেন, ভরা মৌসুমেও ইলিশের দাম এত বেশি যে এটি আর দৈনন্দিন খাবারের অংশ নয়, বরং উৎসব বা বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য সীমিত বিলাসিতা। বহু পরিবার এখন ইলিশ খাওয়াকে এড়িয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব সংস্কৃতিতেও পড়বে বলে আশঙ্কা রয়েছে।
সব মিলিয়ে ইলিশ রপ্তানি নিয়ে বিতর্ক কেবল অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকও। একদিকে রয়েছে রাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বার্থ, অন্যদিকে জনগণের প্রাপ্যতা ও বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। এ দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করা সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ। যদি অনিয়ম, সিন্ডিকেট ও অর্থপাচারের অভিযোগ সত্য হয়, তবে এর দায়ভার কেবল ব্যবসায়ীদের নয়, নীতিনির্ধারকদেরও নিতে হবে। কারণ, রাজনৈতিক প্রভাবশালী মহলের স্বার্থ রক্ষার জন্য যদি সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করা হয়, তবে সেটি রাষ্ট্রের ন্যায়বিচারকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে।
আজকের বাংলাদেশে ইলিশ আর কেবল নদীর মাছ নয়, এটি অর্থনীতি, কূটনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির জটিল এক প্রতীক। এই প্রতীকের প্রতি রাষ্ট্র যদি ন্যায্য দায়িত্ব পালন না করে, তবে বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতির গর্ব ধীরে ধীরে কেবল স্মৃতির পাতায় ঠাঁই পাবে।




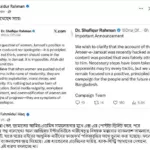

আপনার মতামত জানানঃ