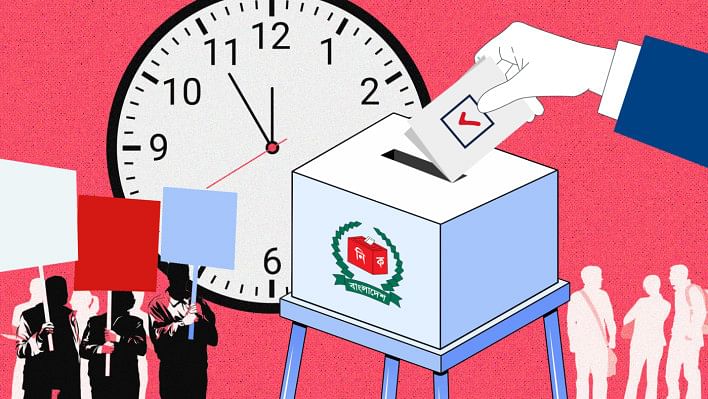
ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আবারও অনিশ্চয়তার মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। প্রধান উপদেষ্টা ৫ আগস্ট জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রোজার আগে নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা দিলেও মাঠের রাজনীতিতে সেই ঘোষণা এখনো দৃঢ় বিশ্বাসের জায়গা তৈরি করতে পারেনি। নির্বাচন কমিশন একদিকে প্রতিদিন বৈঠক করছে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞায় সশস্ত্র বাহিনীকে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে, যাতে তারা নির্বাচনে অন্যান্য বাহিনীর মতো দায়িত্ব পালন করতে পারে। এই উদ্যোগ প্রশাসনিক দিক থেকে নির্বাচনকে শক্তিশালী করার একটি পদক্ষেপ হলেও রাজনৈতিক অঙ্গনে এর প্রতিক্রিয়া মিশ্র।
ঘটনার মোড় ঘুরে যায় যখন প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণার দিনই জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী প্রকাশ্যে বলেন, “ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না।” তিনি যুক্তি দেন, সংবিধান সংস্কার ও বিচারকাজ শেষ না করে নির্বাচনে যাওয়া হলে তা শহীদদের আত্মত্যাগকে অসম্মান করবে। এই বক্তব্য ব্যক্তিগত নাকি দলীয়, তা স্পষ্ট না হলেও এটি রাজনৈতিক জগতে আলোড়ন তোলে। জামায়াতের মতো এনসিপিও আনুপাতিক ভোটের দাবি জানালেও তারা এরই মধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে, যা ইঙ্গিত দিচ্ছে তারা ভোটের প্রস্তুতি নিয়েই এগোচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, এটি এনসিপির কৌশলগত চাল—দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়ানো এবং অন্যান্য দলের সঙ্গে দর–কষাকষিতে সুবিধা নেওয়ার প্রচেষ্টা।
এবারের নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে বিএনপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে জামায়াতকে দেখা হচ্ছে, যেহেতু আওয়ামী লীগ কার্যক্রমে নিষিদ্ধ। জামায়াত ইতিমধ্যে ৩০০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে এবং অন্যান্য ইসলামি দলের সঙ্গে জোট গঠনের সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রশ্ন হলো, এনসিপি এই জোটে যোগ দেবে নাকি একক পথে হাঁটবে। এনসিপি সম্প্রতি আত্মবিশ্বাসের সুরে বলছে, তারা হয় সরকার গঠন করবে, নয়তো প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হবে। এমনকি কিছু নেতা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, বিএনপি ৯০ থেকে ১০০ আসনের বেশি পাবে না।
রাজনৈতিক মাঠের এই উচ্ছ্বাস ও প্রতিযোগিতার মাঝেই ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) পরিচালিত সাম্প্রতিক জরিপের ফলাফল একটি ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে। প্রায় ৪৮.৫% ভোটার এখনো সিদ্ধান্তহীন। মাত্র ১২% বিএনপিকে, ১০.৪% জামায়াতকে এবং ২.৮% এনসিপিকে ভোট দেওয়ার কথা বলেছেন। গত বছরের তুলনায় বিএনপি ও জামায়াতের জনপ্রিয়তা কিছুটা কমেছে, এনসিপির সামান্য বেড়েছে, আর নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সমর্থনও হ্রাস পেয়েছে। এই ভোটার অনিশ্চয়তা নির্বাচনের সঠিক চিত্র এখনো অন্ধকারে রেখেছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে কৌশল পুনর্বিবেচনার সুযোগ দিচ্ছে।
সংবিধান সংস্কার প্রশ্নেও বিভক্তি স্পষ্ট। যদিও প্রাথমিকভাবে সংবিধান পুনর্লিখনের কথা উঠেছিল, এখন আলোচনা সীমিত হয়ে এসেছে বর্তমান সংবিধানের ভিত্তিতেই সংস্কারের দিকে। উচ্চকক্ষে আনুপাতিক ভোটের বিষয়ে মোটামুটি ঐকমত্য হলেও নিম্নকক্ষ নিয়ে কোনো অগ্রগতি নেই। জামায়াত ও এনসিপির দাবি থাকা সত্ত্বেও আগামী নির্বাচনে আনুপাতিক ভোটের বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব, কারণ এর জন্য সংবিধান পরিবর্তন অপরিহার্য।
নির্বাচন কমিশনের প্রধান এ এম এম নাসির উদ্দীন স্বীকার করেছেন, নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে। এই চ্যালেঞ্জ এককভাবে ইসির পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়—প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া তা সম্ভব নয়। অন্যদিকে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের স্পষ্ট করে বলেছেন, যদি নির্বাচন সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক না হয় এবং মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে ভোট দিতে না পারে, তবে এই নির্বাচনও প্রশ্নবিদ্ধ হবে।
সব মিলিয়ে নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ও সংশয় দুটোই সমান্তরালে বাড়ছে। প্রায় সব দলের নেতাই আরেকটি “১/১১” পরিস্থিতির আশঙ্কা করছেন। এর মানে নতুন করে ষড়যন্ত্রের আবির্ভাব এবং ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার সম্ভাবনা। চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানে শত শত প্রাণ হারানোর পরও এই সন্দেহ ও দোষারোপের রাজনীতি গণতন্ত্রের যাত্রাপথকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই মুহূর্তে নির্বাচন আয়োজনের চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো—এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা যেখানে প্রতিটি ভোটার নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন এবং ফলাফল নিয়ে কোনো প্রশ্ন না ওঠে। অন্যথায়, ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের ঘোষণাও হয়তো আরেকটি ব্যর্থ প্রতিশ্রুতিতে পরিণত হবে।






আপনার মতামত জানানঃ