
বাংলাদেশে নির্বাচনী আমেজ এখন তুঙ্গে। জুলাইয়ের অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্ণ হতে না হতেই রাজনীতি পুরোপুরি ঢুকে পড়েছে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে বিতর্ক, জল্পনা ও প্রস্তুতির এক নতুন মোড়ে। এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে বিএনপি—এক সময়ের শাসক দল, বর্তমানে ক্ষমতার বাইরে থাকা বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি, যারা ২০২৫ সালের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বপ্ন দেখছে।
এই নির্বাচনে জয়ের সম্ভাব্য ফল হিসেবে বিএনপি একটি সাংবিধানিক সংস্কার প্যাকেজের দাবি জানাতে পারে। কিন্তু এখানেই তৈরি হচ্ছে রাজনৈতিক কৌশলের এক জটিল দ্বন্দ্ব। কারণ, এই সংস্কার প্রশ্নে বিএনপির বর্তমান অবস্থানই জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি বিতর্কিত দলের জন্য নতুন রাজনৈতিক সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত বিএনপির জন্য নিজেই বুমেরাং হয়ে দাঁড়াতে পারে।
বিএনপি যদি সরাসরি সেই সংস্কার প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করে—যার মধ্যে রয়েছে একটি ক্ষমতাসম্পন্ন নির্বাচিত উচ্চকক্ষ, সংবিধান সংশোধনের যৌক্তিক কাঠামো এবং নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান—তবে তারা নিজেরাই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐকমত্য থেকে। এই অবস্থানে থাকলে অন্যান্য দল, বিশেষ করে এনসিপি, হয়তো এই চার্টার স্বাক্ষর করবে না, এমনকি নির্বাচনে অংশ নাও নিতে পারে।
এখানেই রাজনীতির জমিন জটিল হয়ে উঠছে। কারণ, এনসিপি নিজেরাই সাংগঠনিকভাবে দুর্বল, মাঠের শক্তি সীমিত হলেও তাদের সংস্কারপন্থী অবস্থানই তাদের মূল রাজনৈতিক পরিচয়। এ অবস্থায় যদি জামায়াত এদের সঙ্গে যুক্ত হয়—যা খুবই সম্ভব—তাহলে রাজপথে ‘সংস্কারপন্থী বনাম সংস্কারবিরোধী’ এক নতুন দ্বন্দ্ব শুরু হতে পারে।
জামায়াত যদি এই দ্বন্দ্বে সক্রিয় ভূমিকা নেয়, তবে তারা হয়ে উঠতে পারে ‘রাজনৈতিক মধ্যস্থতাকারী’ বা এমনকি জাতীয় রাজনীতিতে একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার’। এই ভূমিকার মাধ্যমে তাদের অতীতের বিতর্কিত ভাবমূর্তি কিছুটা হলেও বদলাতে পারে। বিশেষ করে যদি তারা একটি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য সংস্কার প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় বা অন্য দলগুলোকে ঐকমত্যে আনতে সহায়ক হয়, তবে তাদের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।
এই পরিস্থিতিতে বিএনপির সামনে তিনটি বড় ধরনের রাজনৈতিক ঝুঁকি দেখা দেয়:
প্রথমত, জামায়াত-নেতৃত্বাধীন সংস্কার আন্দোলন একদিকে নির্বাচন ব্যাহত করতে পারে, অন্যদিকে আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ চলে যেতে পারে বিএনপির বাইরে।
দ্বিতীয়ত, যদি বিএনপি ছাড়া অন্য দলগুলো নির্বাচনে অংশ নেয়, তবে ভোটারদের মধ্যে দ্বিধা, সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন এবং রাজপথে নতুন আন্দোলনের সম্ভাবনা বাড়বে।
তৃতীয়ত, সবচেয়ে সম্ভাব্য এবং বিপজ্জনক পথ হলো—জামায়াত যদি নির্বাচনে অংশ নেয় এবং বিএনপিকে কিছু সংস্কারে রাজি করিয়ে নেয়, অথবা নিজেরাই সংস্কারপন্থী হয়ে ওঠে। এতে বিএনপির অবস্থান দুর্বল হবে এবং ২০৩০-৩১ সালের রাজনীতিতে জামায়াত হয়ে উঠতে পারে বিএনপির আসল প্রতিদ্বন্দ্বী।
এই তিন পথেই বিএনপি রাজপথে ও সংসদে উভয়ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান হারাতে পারে, আর রাজনীতির মঞ্চে নতুন করে জায়গা করে নিতে পারে জামায়াত।
তবে একটি সহজ ও কৌশলগত পথ বিএনপির সামনে এখনো খোলা রয়েছে।
সংবিধান সংশোধনে দ্বৈত সংখ্যাগরিষ্ঠতার শর্ত, স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর রাজনৈতিক প্রভাব দূর করা, এবং নারীদের সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করাকে যদি বিএনপি গ্রহণ করে, তবে তারা ভবিষ্যতের জন্য দ্ব্যর্থহীন বার্তা দিতে পারে—তারা সংস্কারবিরোধী নয়। এতে একদিকে রাজনৈতিক বিরোধীদের মুখ বন্ধ করা যাবে, অন্যদিকে তরুণ ও মধ্যপন্থী ভোটারদের আস্থা ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে।
এই কৌশলের আরেকটি বড় উপকার হবে—তারেক রহমানকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে ‘সংস্কারের পুরুষ’ হিসেবে। তার মা খালেদা জিয়া যেমন সংসদীয় পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়েছিলেন, তার পিতা জিয়াউর রহমান যেমন বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করেছিলেন, তেমনি তারেক রহমান নিজেকে উপস্থাপন করতে পারবেন ‘আধুনিক গণতন্ত্রের রূপকার’ হিসেবে।
বিএনপির জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো—জামায়াতের মতো একটি দল যদি সংস্কার দাবির শূন্যতায় জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে মাথা তোলে, তবে তরুণ ও শিক্ষিত ভোটারদের একটি বড় অংশ বিএনপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। এখনো জামায়াতের প্রতি জনগণের মনোভাব আস্থাশীল নয়, কিন্তু বিএনপির সংস্কারবিরোধিতার ফাঁকে যদি তারা সুযোগ পায়, তবে তা হবে বিএনপির রাজনৈতিক বিপর্যয়ের শুরু।
বাস্তবতা হলো, প্রস্তাবিত অনুপাতভিত্তিক উচ্চকক্ষে বিএনপি চাইলে ভবিষ্যতে বড় দল হিসেবেই রয়ে যাবে। তাই এই ব্যবস্থাকে ভয় পাওয়ার কোনো যুক্তি নেই। বরং সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্যের ক্ষেত্রেও বিএনপির পারফরম্যান্স ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
এখন জনগণের মধ্যে একটি ‘সংবিধান সংস্কার’ চেতনা তৈরি হয়েছে—যা শুধু শহর নয়, গ্রাম পর্যায়েও আলোচিত হচ্ছে। জনগণ চায় রাষ্ট্রক্ষমতার ভারসাম্য, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং নারীদের বাস্তব প্রতিনিধিত্ব। বিএনপি যদি এই স্রোতের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত না করে, তবে তারা ভবিষ্যতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হতে পারে।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক চাপ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, এমনকি এশিয়ার কিছু শক্তিধর দেশ এবার বাংলাদেশের নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সরাসরি পর্যবেক্ষণে রয়েছে। অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবি কেবল কূটনীতিকদের নয়, বরং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অংশীদারদের পক্ষ থেকেও আসছে। বিএনপি যদি নিজের অবস্থানকে ‘সংস্কারবিরোধী একক অবস্থানে’ পরিণত করে, তবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়াও কঠিন হয়ে উঠবে।
তবে বাস্তব চিত্রে একটি বড় অস্পষ্টতা রয়েছে—সামাজিক মাধ্যমে বিএনপিকে ‘সংস্কারবিরোধী’ বলেই তুলে ধরা হলেও, প্রকৃতপক্ষে ৬৯১টি সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র ৭৩টিতে তারা দ্বিমত জানিয়েছে। বাকি ৬০০টির বেশি প্রস্তাবে তারা ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে।
এই কারণে দলের ভেতরের আলোচনা, যুক্তিনির্ভর সংশোধনী প্রস্তাব ও সংস্কার বিষয়ে তাদের অগ্রগতি গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। তারা সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ এবং প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ নিয়ে সংস্কার মানতে রাজি হওয়ায় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আশাবাদী হয়েছেন।
একটি যুগান্তকারী নির্বাচনের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে বিএনপির সামনে এখন সুযোগ—শুধু নেতৃত্ব পাওয়ার নয়, নেতৃত্বের ধরন বদলে দেওয়ারও। প্রশ্ন হলো, তারা কি এই সুযোগকে সম্ভাবনা হিসেবে দেখবে, নাকি আবারও তা হাতছাড়া করবে?



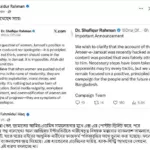


আপনার মতামত জানানঃ