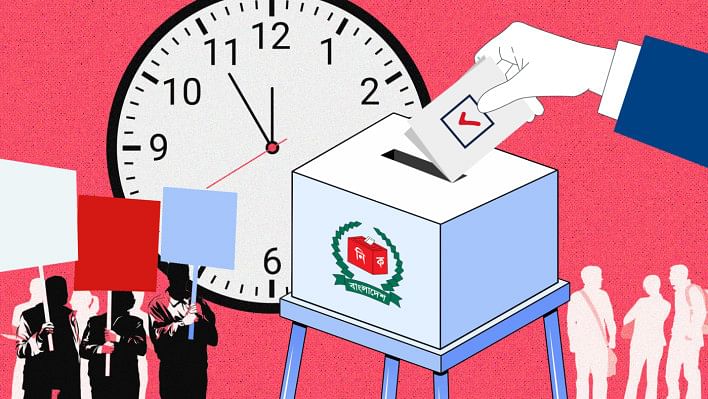 বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নির্বাচনী ব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংস্কারের লক্ষ্যে একাধিক কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই সংস্কারের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত একটি বিষয় হলো ‘আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা’ বা পিআর পদ্ধতি। এটি এমন একটি নির্বাচন পদ্ধতি যেখানে জাতীয় সংসদের আসন বণ্টন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত মোট ভোটের অনুপাতে নির্ধারিত হয়। ফলে যেসব দল হয়তো সীমিত সংখ্যক ভোট পায়, তারাও সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়। বর্তমান ‘একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে আসন নির্ধারণ’ প্রথার তুলনায় এই পদ্ধতি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায্য বলে দাবি করছেন অনেক রাজনৈতিক দল ও বিশ্লেষক।
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নির্বাচনী ব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংস্কারের লক্ষ্যে একাধিক কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই সংস্কারের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত একটি বিষয় হলো ‘আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা’ বা পিআর পদ্ধতি। এটি এমন একটি নির্বাচন পদ্ধতি যেখানে জাতীয় সংসদের আসন বণ্টন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত মোট ভোটের অনুপাতে নির্ধারিত হয়। ফলে যেসব দল হয়তো সীমিত সংখ্যক ভোট পায়, তারাও সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়। বর্তমান ‘একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে আসন নির্ধারণ’ প্রথার তুলনায় এই পদ্ধতি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায্য বলে দাবি করছেন অনেক রাজনৈতিক দল ও বিশ্লেষক।
সম্প্রতি একটি সেমিনারে জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টিসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল পিআর পদ্ধতির পক্ষে জোরালো দাবি তোলে। এদের বক্তব্য, এ পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সংসদে সব দলেরই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে এবং ছোট দলগুলোও জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে। তাদের মতে, বর্তমান ব্যবস্থায় হয়তো একজন প্রার্থী ২৫ শতাংশ ভোট পেয়েও নির্বাচিত হয়ে যান, অথচ বাকি প্রার্থীরা ৭৫ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হন। এতে জনগণের প্রকৃত মতামতের প্রতিফলন ঘটে না।
তবে এই আলোচনায় বড় একটি বিরোধী সুর আসে বিএনপির পক্ষ থেকে। বিএনপি স্পষ্ট করে জানিয়েছে, তারা প্রচলিত সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষেই রয়েছে। তাদের মতে, এই পদ্ধতি বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে চলছে এবং এর মধ্য দিয়েই একটি দল জনসমর্থনের ভিত্তিতে সরকার গঠন করে। তারা পিআর পদ্ধতিকে অকার্যকর ও বিভ্রান্তিকর মনে করে। বিশ্লেষকদের মতে, বিএনপি মনে করছে বর্তমান ব্যবস্থায় তাদের জয়ের সম্ভাবনা বেশি, তাই তারা আনুপাতিক পদ্ধতির বিরোধিতা করছে।
এদিকে নির্বাচন ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা একদিকে যেমন স্বৈরশাসনের পথ রুদ্ধ করতে পারে, অন্যদিকে এটি ভোটারের প্রকৃত মতামতেরও প্রতিফলন ঘটায়। কারণ এই পদ্ধতিতে ভোটের প্রতিটি কণাই মূল্যবান। কেউ যদি ৫ শতাংশ ভোটও পায়, তা হলে সেই ভোটে অন্তত কিছু আসনে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। এটি ছোট দলগুলোর পক্ষে অত্যন্ত ইতিবাচক একটি বিষয়।
নির্বাচন বিশ্লেষক অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদের মতে, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি চালু হলে ভোটারের সকল স্তরের মতামত সংসদে প্রতিফলিত হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। তিনি বলেন, “এই পদ্ধতিতে সংসদে এমন একটি চিত্র তৈরি হবে, যেখানে সকল শ্রেণি ও মতাদর্শের মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।” তিনি আরও বলেন, “বর্তমানে স্থানীয় জনপ্রিয়তা বা ভোট ব্যাংকের জোরে অনেকেই সংসদে আসেন, যা জনমতের পূর্ণ প্রতিফলন নয়।”
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান ব্যবস্থায় একজন প্রার্থী নির্দিষ্ট একটি আসনে জয়ী হন। ধরা যাক, কোনো আসনে চারজন প্রার্থী রয়েছেন এবং তারা যথাক্রমে ২০, ২০, ২০ ও ২৫ শতাংশ ভোট পেলেন। যিনি ২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন, তিনি সংসদে যাবেন, বাকি তিনজন বাদ পড়ে যাবেন। কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে এই ৮৫ শতাংশ ভোটের প্রতিফলন সমানভাবে সংসদে পড়বে, যেহেতু আসন বণ্টন মোট ভোটের ভিত্তিতে হবে। এতে করে ভোটারদের মতামত আরও বেশি ন্যায্যভাবে প্রতিফলিত হবে।
বিশ্বের বহু দেশে এই পদ্ধতি চালু রয়েছে। সাম্প্রতিক এক জরিপ অনুযায়ী, ১৭০টি দেশের মধ্যে অন্তত ৯১টি দেশে এই পদ্ধতিতে নির্বাচন পরিচালিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশ, ইউরোপের বহু উন্নত দেশ এবং লাতিন আমেরিকার কিছু দেশেও এই পদ্ধতির চর্চা রয়েছে। নেপালের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য, যেখানে রাজতন্ত্র পতনের পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
বাংলাদেশেও এই পদ্ধতির পক্ষে সুপারিশ এসেছে গত এক দশকে বারবার। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মতি ছাড়া এই পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়নি। বড় দুই দল—আওয়ামী লীগ ও বিএনপি—এই বিষয়ে কখনও স্পষ্ট সমর্থন জানায়নি। বরং তাদের অবস্থান বরাবরই বিদ্যমান ব্যবস্থার পক্ষে থেকে গেছে। কারণ হিসেবে বিশ্লেষকরা মনে করেন, বড় দলগুলো সাধারণত প্রচলিত পদ্ধতিতে বেশি লাভবান হয়। তারা একক আসনে প্রার্থী দিয়ে নিজের প্রভাব কাজে লাগিয়ে নির্বাচিত হয় এবং বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে।
তবে সমস্যা হলো, এতে করে সংসদে একতরফা মতাদর্শের আধিপত্য তৈরি হয় এবং বহু ভোট, বহু কণ্ঠস্বর সংসদের বাইরে থেকে যায়। এই অপূর্ণতা দূর করতেই আনুপাতিক ব্যবস্থা একটি কার্যকর সমাধান হতে পারে। তবে এই ব্যবস্থারও কিছু ত্রুটি রয়েছে। অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ যেমন বলেছেন, পিআর পদ্ধতিতে সরকার গঠন অনেক সময় অস্থিতিশীল হয়, কারণ কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না। ফলে জোট সরকার গঠন করতে হয়, যার স্থায়িত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, রাজনৈতিক পরিপক্বতা ও আন্তঃদলীয় সমঝোতার মাধ্যমে এই সমস্যা মোকাবিলা সম্ভব।
পিআর পদ্ধতি চালু করতে হলে সংবিধানে কিছু সংশোধনের প্রয়োজন হবে। যদিও বিশ্লেষকদের মতে, এটি খুব কঠিন কোনো বিষয় নয়। প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও জনগণের চাপ। বর্তমানে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নানা বিতর্ক ও অসন্তোষ রয়েছে। বিশেষ করে ভোটারদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। পিআর পদ্ধতি চালু হলে এই আস্থার সংকট অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা।
রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিএনপি যেমন শুরু থেকেই এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করে এসেছে, তেমনি আওয়ামী লীগকে এই আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানোই হয়নি। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, বৃহৎ দলগুলো নিজেদের স্বার্থেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে থাকে। কারণ এতে তারা এককভাবে সরকার গঠনের সুযোগ হারায়। অপরদিকে, ছোট দলগুলো—যারা অনেক সময় ১০-১৫ শতাংশ ভোট পেলেও সংসদে কোনো আসন পায় না—তারা পিআর ব্যবস্থায় অনেক বেশি উপকৃত হবে।
ফলে দেখা যাচ্ছে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হলে সকল পক্ষকে কিছু ছাড় দিতে হবে। ছোট দলগুলো যে অংশগ্রহণের সুযোগ চায়, তা যেমন যৌক্তিক, তেমনি বড় দলগুলোও জাতীয় স্বার্থে একক আধিপত্যের চিন্তা থেকে বের হয়ে এলে পুরো ব্যবস্থাটি আরও গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে। আর জনগণের প্রকৃত মতামতের প্রতিফলন ঘটবে সংসদে।
এই ব্যবস্থার বাস্তবায়ন যে রাতারাতি সম্ভব নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমত এবং একটি শক্তিশালী জনমতের চাপে ধীরে ধীরে বাংলাদেশও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার পথে এগোতে পারে। উন্নত বিশ্বে এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ, স্বৈরতন্ত্র রোধে এর ভূমিকা, এবং নির্বাচনে প্রতিটি ভোটের মূল্য নিশ্চিত করার দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে।


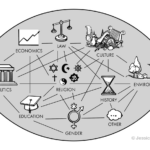



আপনার মতামত জানানঃ