
বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা দীর্ঘদিন ধরেই একটি আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩০ বছর এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটাধারীদের সন্তানদের জন্য তা ৩২ বছর। এই নির্ধারিত সীমার বাইরে গিয়ে হাজার হাজার তরুণ প্রতিবছর সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়ে যান। ফলে বিগত এক দশকে একাধিকবার এ নিয়ে আন্দোলন হয়েছে, কোথাও কোথাও ঘটেছে সংঘর্ষ, হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে। পাশাপাশি এ নিয়মের ইতিহাসও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশ্নবিদ্ধ।
বয়সসীমা নির্ধারণের ইতিহাস
সরকারি চাকরির বয়সসীমা ৩০ বছর নির্ধারণের সূচনা ঘটে আশির দশকে। ১৯৮৬ সালে প্রথমবারের মতো ২৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছর করা হয় চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়স। তখন থেকেই এটি স্থির থেকে গেছে। যদিও শিক্ষা ব্যবস্থায় দেরি, সেশনজট, ও কর্মসংস্থান সংকট দিন দিন বাড়তে থাকে, কিন্তু বয়সসীমার ক্ষেত্রে কোনো সংস্কার হয়নি।
তবে ২০০৭ সালে জরুরি অবস্থা চলাকালীন কিছু পদে বয়সসীমা ৩৫ বছর পর্যন্ত করা হয়েছিল অস্থায়ীভাবে, এবং বিভিন্ন সময়ে বিশেষ নিয়োগে বা কোভিড-পরবর্তী নির্দিষ্ট চাকরিতে বয়সে শিথিলতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা কখনোই স্থায়ী রূপ পায়নি।
উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ও সংঘর্ষ
১. ২০১১ সালের আন্দোলন: চাকরিতে বয়সসীমা বাড়ানোর দাবিতে ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষার্থীরা প্রথমবার সুসংগঠিতভাবে আন্দোলনে নামে। মিছিল ও মানববন্ধনের মাধ্যমে তারা ৩৫ বছর বয়সসীমার দাবি জানায়। যদিও তখন কোনো উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ হয়নি, সরকারও এ বিষয়ে নীরব থেকেছে।
২. ২০১৮ সালের আন্দোলন: এই বছর বেশ বড় পরিসরে আন্দোলন হয়। “৩৫ চাই” নামে একটি সংগঠন রাজধানী ঢাকায় একাধিক মানববন্ধন, অবস্থান কর্মসূচি ও মিছিল করে। বিশেষ করে শাহবাগ ও জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় আন্দোলনকারীরা কয়েকবার পুলিশের বাধার সম্মুখীন হন। সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হন, যাদের মধ্যে কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি হন।
৩. ২০২০–২১ সালের করোনা-পরবর্তী আন্দোলন: করোনাভাইরাস মহামারির সময় চাকরির নিয়োগ প্রায় দুই বছর স্থগিত ছিল। এর ফলে অনেক চাকরিপ্রত্যাশী বয়সসীমা অতিক্রম করে ফেলেন। এই সময় ‘চাকরি প্রত্যাশী সাধারণ ছাত্র পরিষদ’ ও অন্যান্য সংগঠন বিভিন্ন জায়গায় টানা ১০–১৫ দিনের অবস্থান কর্মসূচি, মশাল মিছিল এবং অনশন কর্মসূচি পালন করে।
২০২১ সালের আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহবাগে আন্দোলনের সময় পুলিশের সঙ্গে কয়েক দফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। তখন অন্তত ৩৫ জন আহত হন, যার মধ্যে কয়েকজন ছাত্রনেতার অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। আন্দোলনকারীরা দাবি করেন, রাষ্ট্র যদি সময়মতো নিয়োগ কার্যক্রম চালাত, তবে তারা বয়সসীমার বাইরে চলে যেতেন না।
৪. ২০২৩ সালের আন্দোলন: ২০২৩ সালের শুরুতে আবারও ৩৫ চাই আন্দোলন চাঙ্গা হয়। ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাব, টিএসসি ও রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ। এই সময়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় ৫০ জন আহত হন, এবং প্রায় ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আন্দোলনকারীরা আবারও বলেন, তারা কোনো রাজনৈতিক স্বার্থে আন্দোলনে নেই, শুধু ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছেন।
কেন এই ক্ষোভ?
বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা শেষ করতে সাধারণত ২৪-২৫ বছর সময় লেগে যায়। এরপর প্রতিযোগিতামূলক প্রস্তুতি নিতে গিয়ে অনেকেই ৩০ পার করে ফেলেন। সেশনজট, কোর্সের বিলম্ব, ফল প্রকাশে ধীরগতি ইত্যাদি কারণে শিক্ষার্থীরা কর্মজীবনে প্রবেশ করতে দেরি করেন। অথচ সরকার বয়সসীমা নির্ধারণ করে রেখেছে এমনভাবে, যেন সবাই সঠিক সময়ে পড়াশোনা শেষ করে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে—যা বাস্তবের সঙ্গে খাপ খায় না।
আন্দোলনের পেছনের কারণ
গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সময় ছাত্র ও চাকরিপ্রত্যাশীরা বয়সসীমা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন। তাদের যুক্তি—অনেক সময় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার দীর্ঘসূত্রিতা, সেশনজট, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা ইত্যাদি কারণে সময়মতো ডিগ্রি শেষ করা সম্ভব হয় না। ফলে ৩০ বছর বয়সসীমা পার হয়ে যাওয়ার আগেই তারা সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতার বাইরে চলে যান।
বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির সময় প্রায় দুই বছর ধরে নিয়োগ পরীক্ষাগুলো স্থগিত ছিল। এতে হাজার হাজার চাকরিপ্রত্যাশী বয়স হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তীতে তাদের জন্য বয়সে ছাড়ের দাবি উঠলেও সরকার শুধু নির্দিষ্ট কিছু নিয়োগ পরীক্ষায় সীমিতভাবে ছাড় দিয়েছে। আন্দোলনকারীরা সব ধরনের চাকরিতে বয়সসীমা বাড়িয়ে ৩৫ বছর করার দাবি জানিয়ে আসছে।
এই নিয়ম কি এড়ানো যেত?
প্রশ্ন উঠেছে—এই সংকট কি এড়ানো যেত? বিশ্লেষকদের মতে, রাষ্ট্র যদি সময়মতো শিক্ষা কার্যক্রম ও নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনা করতে পারত, তাহলে অনেকেই বয়সসীমার বাইরে যেতেন না। আবার, বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে যদি কর্মজীবনে প্রবেশের বাস্তবতা বিবেচনায় নেয়া হতো, তাহলে আরও মানবিক ও কার্যকর নীতিমালা তৈরি করা সম্ভব ছিল।
কিছু দেশ যেমন শিক্ষার দৈর্ঘ্য, যুব বেকারত্ব, এবং চাকরির বাজার বিশ্লেষণ করে সরকারি চাকরির বয়সসীমা নির্ধারণ করে, বাংলাদেশেও তেমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল।
অন্যান্য দেশে চাকরির বয়সসীমা
বিভিন্ন দেশে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বয়সসীমা ভিন্ন ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ:
ভারত: কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়স সাধারণত ৩২ বছর, তবে অনগ্রসর শ্রেণি ও তফসিলভুক্ত জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এটি ৩৫ থেকে ৩৭ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে।
পাকিস্তান: অধিকাংশ সরকারি চাকরিতে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বছর হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে ৩৫ বছর পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়।
যুক্তরাজ্য: সাধারণভাবে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের কোনো সর্বোচ্চ বয়সসীমা নেই, তবে নির্দিষ্ট কিছু পদে (যেমন—পুলিশ, সামরিক বাহিনী) ফিটনেস ও দক্ষতার ভিত্তিতে বয়স বিবেচনা করা হয়।
জার্মানি ও কানাডা: এসব দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বয়স সীমা নেই; বরং যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে চাকরির সুযোগ দেওয়া হয়।
বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ৩০ বছর বয়সসীমা অনেকেই অযৌক্তিক মনে করেন। কারণ, এখানে উচ্চশিক্ষা শেষ করতে অনেক সময় ২৪-২৫ বছর পর্যন্ত লেগে যায়। এরপর নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে অনেকেই বয়সের কারণে বাদ পড়ে যান।
অন্যদিকে, ভারতের মতো দেশে যেখানে জনসংখ্যাও বিশাল, সেখানে চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩২ থেকে ৩৭ বছর পর্যন্ত রাখা হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে বয়সের পরিবর্তে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও চাকরির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নেওয়া হয়। ফলে সেখানে অনেকেই পেশা পরিবর্তন বা দেরিতে চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ পান।
সরকারি চাকরির বয়সসীমা নিয়ে আন্দোলন শুধুই একটি চাকরির ইস্যু নয়, এটি তরুণ সমাজের স্বপ্ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, এবং প্রশাসনিক বাস্তবতার প্রতিফলন। ইতিহাস বলছে, ৩০ বছর বয়সসীমা বহুদিন ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে, অথচ সময় বদলেছে, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের পরিস্থিতিও পাল্টেছে।
যদি বাংলাদেশ বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে চায়, তাহলে বয়সসীমার এই গোঁড়ামি থেকে বেরিয়ে এসে আরও বাস্তবধর্মী ও মানবিক নীতিমালার দিকে যেতে হবে। আর সবচেয়ে জরুরি—চাকরি মানেই যেন “সময়মতো সুযোগ”—তা নিশ্চিত করা।

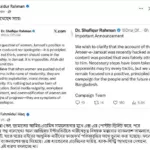




আপনার মতামত জানানঃ