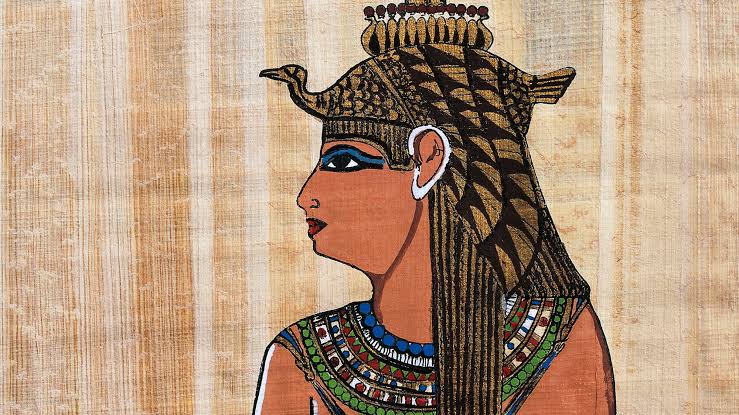 ভোরবেলায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। সে হয়তো অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে যাবে, কিংবা কোনো প্রতিবাদী পোস্টার হাতে নিয়ে রাস্তায় নামার আগে শেষবারের মতো নিজের মুখটা ঠিক করে নিচ্ছে। মুখে তেমন কিছু নেই, ক্লান্তি আর দৈনন্দিন যন্ত্রণা মিলিয়ে একঘেয়েমি জমে আছে। হঠাৎ ছোট্ট একটা স্টিক বের করে সে আলতো করে ঠোঁটে রঙ টেনে দিল। মুহূর্তেই যেন বদলে গেল তার মুখের রেখা, চোখের ভঙ্গি। যেন নিজেকে আরেকটু উঁচু করে দাঁড় করাল সে; ছোট্ট একটা রঙিন দাগ তার ঠোঁটে, অথচ যেন তার ভেতরের কণ্ঠে আরও একটু জোর যোগ করে দিল। এ রঙ শুধু সাজ নয়, এ যেন নীরব ভাষায় বলা—“আমি আছি, আমি চাই, আমি প্রতিবাদ করি, আমি বেছে নিই।”
ভোরবেলায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। সে হয়তো অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে যাবে, কিংবা কোনো প্রতিবাদী পোস্টার হাতে নিয়ে রাস্তায় নামার আগে শেষবারের মতো নিজের মুখটা ঠিক করে নিচ্ছে। মুখে তেমন কিছু নেই, ক্লান্তি আর দৈনন্দিন যন্ত্রণা মিলিয়ে একঘেয়েমি জমে আছে। হঠাৎ ছোট্ট একটা স্টিক বের করে সে আলতো করে ঠোঁটে রঙ টেনে দিল। মুহূর্তেই যেন বদলে গেল তার মুখের রেখা, চোখের ভঙ্গি। যেন নিজেকে আরেকটু উঁচু করে দাঁড় করাল সে; ছোট্ট একটা রঙিন দাগ তার ঠোঁটে, অথচ যেন তার ভেতরের কণ্ঠে আরও একটু জোর যোগ করে দিল। এ রঙ শুধু সাজ নয়, এ যেন নীরব ভাষায় বলা—“আমি আছি, আমি চাই, আমি প্রতিবাদ করি, আমি বেছে নিই।”
লিপস্টিকের গল্প আসলে এমনই এক দীর্ঘ নাটক, যেখানে সৌন্দর্যের পাশাপাশি ভীষণ জড়িয়ে আছে ক্ষমতা, ধর্ম, রাজনীতি, শ্রেণী, বিজ্ঞান আর বিদ্রোহের ইতিহাস। আজ যে লিপস্টিক খুব সাধারণভাবে ব্যাগে রাখা থাকে, সেলফি তোলার আগে যে সামান্য সময় নিয়ে ঠোঁটে টেনে নেওয়া হয়, সেই ছোট্ট বস্তুটির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আড়াই থেকে চার হাজার বছরের ইতিহাস। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার রাজমহল, মিসরের সমাধি, গ্রিক গির্জা, রোমান সভা, মধ্যযুগের ধর্মআদালত, আর আধুনিক রাস্তায় আন্দোলনে দাঁড়িয়ে থাকা নারীদের ঠোঁট—সব মিলিয়ে লিপস্টিকের পথচলা যেন সভ্যতার আড়াল হয়ে থাকা এক রঙিন ডায়েরি।
এ গল্পের শুরু প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের মেসোপটেমিয়ায়। উরের নগরের শক্তিশালী নারী শাসক কুইন পু আবি বা শুবাদ সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিকরা জানাচ্ছেন, তিনি ঠোঁটে লাগাতেন এক বিশেষ রঙ—সাদা সিসা আর গুঁড়া করা লাল পাথরের মিশ্রণে তৈরি প্রাচীন লিপটিন্ট। সেই রঙ ছিল কেবল সাজের জন্য নয়; ক্ষমতা, মর্যাদা ও রাজকীয়তা দৃশ্যমান করার এক প্রতীক। ধনীদের কবর খুঁড়ে দেখা যায়, সামুদ্রিক ঝিনুকের খোলসে ঠোঁটের রঙ সংরক্ষণ করা থাকত—আজকের ভাষায় বলা যায় এটি ছিল এক ধরনের মিনি লিপস্টিক কনটেইনার। মৃত্যু-পরবর্তী জগতেও ঠোঁটের রঙ সঙ্গে নেওয়ার এ আয়োজন প্রমাণ করে, প্রাচীন মানুষের কাছে এ রঙ ছিল দেহের সাজগোজের বাইরে, এক ধরনের সামাজিক অস্তিত্বের পরিচয়।
এর পরে কিছুটা সময় পেরিয়ে মেসোপটেমিয়াতেই দেখা গেল আরেক ধারা। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে সেখানকার নারীরা ঠোঁট সাজাতে শুরু করলেন মূল্যবান পাথর গুঁড়া করে। আগের মতো সাধারণ মাটি বা পাথর নয়, বরং দামি রত্ন গুঁড়া করে ঠোঁটে রঙ লাগানো হলো এক ধরনের উচ্চবর্গীয় পরিচয়ের ঘোষণা। এখানে লিপস্টিক একধরনের বিলাসী পণ্য; যে রঙ ঠোঁটে দেখা গেলে বোঝা যেত, সে ধনবান, প্রভাবশালী আর শ্রেণিগতভাবে ‘উঁচু’।
মেসোপটেমিয়া থেকে এই রঙিন ঠোঁটের সংস্কৃতি চলে যায় নীল নদের পাড়ে, প্রাচীন মিসরে। খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজারের দিকে মিসরে পুরুষ এবং নারী—দুয়েরই দৈনন্দিন জীবনের অংশ ছিল মেকআপ। চোখে কাজল, মুখে পাউডার, আর ঠোঁটে রঙ। তারা ব্যবহার করত লাল অকার নামের এক ধরনের মাটি, যা কখনো কেবল গুঁড়া অবস্থায়, কখনো আবার গাম বা রেজিনের সঙ্গে মিশিয়ে লাগানো হতো, যাতে রঙ ঠোঁটে বেশি সময় ধরে থাকে। লাল তো ছিলই, তার পাশাপাশি কমলা, ম্যাজেন্টা, এমনকি নীল ও কালো ঠোঁটও দেখা যেত। ধনীরা মৃত্যুর পরও সঙ্গে নিয়ে যেতেন এক-দু-টি ঠোঁটের রঙের পাত্র, যেন পরজগতেও মর্যাদার রঙ মুছে না যায়।
কিন্তু সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে তখনও শুরু হয়ে গেছে ঝুঁকির বিজ্ঞান। মিসরের কিছু মিশ্রণে ব্যবহার করা হতো ব্রোমিন ম্যানাইট আর আয়োডাইডের মতো বিষাক্ত রাসায়নিক। এ দিয়ে তৈরি হতো বেগুনি আভাযুক্ত অসাধারণ এক লিপস্টিক, যার নাম হয়ে ওঠে ‘মৃত্যুচুম্বন’। ভীষণ আকর্ষণীয় হলেও নিয়মিত ব্যবহারকারী অনেক নারী অসুস্থ হয়ে পড়তেন, এমনকি কারও কারও মৃত্যু পর্যন্ত ঘটত। সৌন্দর্যের লালচে হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকত অদৃশ্য বিষ।
এ সময় নীল নদের কিংবদন্তি রানী ক্লিওপেট্রা অন্য রাস্তা খুঁজলেন। তিনি বুঝেছিলেন, সাধারণ লাল তার চরিত্রের নাটকীয়তা আর রহস্যকে ধারণ করতে পারছে না। তিনি চাইতেন গভীর, স্থায়ী, আগুনে ঝলমলে এমন রঙ, যা ঠোঁটে আলো হয়ে ঝলসে উঠবে। সমাধান মিলল কারমাইন রঞ্জকে, যা তৈরি হয় এক বিশেষ পোকার থেকে। কখনো তিনি তাতে মাছের আঁশ মেশাতেন, ঠোঁটে ঝিকিমিকি আভা আনতে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আজও আধুনিক অনেক লিপস্টিক আর ব্লাশনে ব্যবহৃত হয় কারমাইন; এমনকি কিছু খাবারের রঙেও তার উপস্থিতি রয়েছে। অর্থাৎ, ক্লিওপেট্রার সৌন্দর্যবোধ এখনো জড়িয়ে আছে আধুনিক প্রসাধন শিল্পের সঙ্গে।
প্রাচীন গ্রিসে এসে ছবিটা উল্টো দিকে মোড় নিল। সেখানে একসময় অতিরিক্ত সাজগোজ, বিশেষ করে ঠোঁট রাঙানো, কৃত্রিমতা আর নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতীক হিসেবে দেখা হতে থাকে। ভদ্রমহিলারা লিপস্টিক থেকে দূরে সরে গেলেন, আর তা ক্রমে যৌনকর্মীদের পরিচয়ের চিহ্নে পরিণত হলো। এমনকি আইন পর্যন্ত করা হলো—যদি কোনো যৌনকর্মী দিনের বেলায় ঠোঁটের রঙ ছাড়া ঘুরে বেড়ায় এবং নিজেকে ভদ্রমহিলা সাজিয়ে ওঠার চেষ্টা করে, তবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। একসময়কার ক্ষমতার প্রতীক রঙিন ঠোঁট সেখানে নেমে গেল সামাজিক তলানিতে, কলঙ্কের প্রতীকে।
রোমান সাম্রাজ্যের সময় আবার পাল্টে গেল দৃশ্যপট। সেখানে পুরুষরা নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বোঝাতে ঠোঁটে রঙ লাগাতেন। ধনী নারীরা ব্যবহার করতেন সৌন্দর্যের জন্য। অর্থাৎ লিপস্টিকের সঙ্গে বারবার পাল্টাচ্ছিল অর্থ—কখনো রাজমর্যাদা, কখনো পাপ, কখনো আবার পুরুষালি ‘বাবুগিরি’। ইউরোপে ৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মানুষের মধ্যে এক ধরনের কৃত্রিমতাবিরোধী ধর্মীয় ঢেউ উঠল; চোখে লাগাম টেনে দেওয়া হলো সৌন্দর্যচর্চায়। কেউ কেউ ইচ্ছে করে কম গোসল করতেন, সাদাসিধে থাকতে চাইতেন ধর্মীয়তার অংশ হিসেবে। লিপস্টিক সেখানে হয়ে উঠল সন্দেহের বস্তু।
মধ্যযুগে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে, ধর্মীয় প্রভাব যখন চরমে, তখন গির্জার অনেক নেতার ধারণা ছিল—ঈশ্বর যেমন করে মুখ বানিয়েছেন, তা পরিবর্তন করা মানেই ঈশ্বরের কাজে হস্তক্ষেপ। কেউ ঠোঁটে রঙ লাগালে তাকে দেখা হতো ‘পাপী’ হিসেবে, কোথাও কোথাও তো ডাইনি বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ক্রুসেডের সময় ইউরোপীয় সৈন্য আর ব্যবসায়ীরা যখন আবার মধ্যপ্রাচ্যে আসা-যাওয়া শুরু করলেন, তখন তাঁদের চোখে পড়ল সেখানে ব্যবহৃত বিলাসী প্রসাধনকর্ম—কাজল, সুগন্ধি, ঠোঁটের রঙ। ইউরোপে তখন লিপস্টিক যেন নিষিদ্ধ আকর্ষণ; ধর্ম যাকে নিষেধ করে, সংস্কৃতি তাকে গোপনে টেনে নেয়।
এই অস্থিরতার মাঝেই ষোলো শতকে মঞ্চে এলেন রানী প্রথম এলিজাবেথ। গালজুড়ে ঘন সাদা পাউডার আর তীব্র লাল ঠোঁট—এই বৈপরীত্যকে তিনি নিজের রাজকীয় স্টাইল বানালেন। কোচিনিল পোকা থেকে পাওয়া কারমাইন, গাম আরবিক, ডিমের সাদা অংশ আর ডুমুরের দুধ—এসব দিয়ে বানানো হতো তাঁর পছন্দের লাল। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই রঙ খারাপ আত্মাকে দূরে রাখে। গির্জা কী বলছে, তা নিয়ে তাঁর তেমন মাথাব্যথা ছিল না; আর রানি হিসেবে তাঁকে কেউ ডাইনি বানিয়ে আগুনে পোড়াবে, এই সাহসও কারও ছিল না। ফলে ধীরে ধীরে লাল ঠোঁট আবার উচ্চবর্গীয়দের আভিজাত্যের প্রতীকে ফিরে আসে। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা কাগজে থাকলেও বাস্তবে গুরুত্ব হারাতে থাকে।
আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে আরেক অদ্ভুত আইন পাস হলো—কোনো নারী যদি পরচুলা, কৃত্রিম দাঁত, উঁচু হিল আর প্রসাধন দিয়ে নিজেকে ‘প্রতারণামূলকভাবে সুন্দর’ বানিয়ে কোনো পুরুষকে বিয়ের ফাঁদে ফেলে, তবে সেই বিয়ে বাতিল করা যাবে, এমনকি তাকে ডাইনি হিসেবে বিচার করা যাবে। পুরুষের সুবিধার কথা ভেবেই বানানো এই আইন অনেক নারীকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, ফলে তারা অনেকেই লিপস্টিক কেনা কমিয়ে দিলেন। তা–ও অদ্ভুতভাবে দেখা গেল, অনেক লিপস্টিকে যেহেতু পারদ মেশানো সিঁদুর বা ভারমিলিয়ন ব্যবহার হতো, যা মারাত্মক বিষাক্ত, আইনটি অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক নারীর প্রাণও বাঁচিয়ে দিল। এ যেন এক অদ্ভুত ‘শাপে বর’।
ইতিমধ্যে আরব-স্পেনের কর্দোভায় বসে এক চিকিৎসক ও শল্যবিদ লিখছিলেন প্রসাধনের নতুন ইতিহাস। আবু আল কাসিম আল জাহরাভি আট থেকে বারো শতকের মধ্যে এমন এক পণ্য বানালেন, যা আধুনিক লিপস্টিকের সঙ্গে সবচেয়ে মিল রাখে। সুগন্ধি মিশ্রণকে তিনি বিশেষ ছাঁচে ঢুকিয়ে শক্ত কাঠির আকার দিলেন—যা আলাদা করে বহন করা যায়, সরাসরি ঠোঁটে ঘষে লাগানো যায়। তরল বা গুঁড়া লিপ কালারের বাইরে এটাই ছিল প্রথম ‘স্টিক’ ধারণা, আধুনিক প্যাকেট লিপস্টিকের এক প্রাচীন পূর্বপুরুষ।
লিপস্টিকের শিল্পগত রূপান্তর শুরু হলো উনিশ শতকের শেষ দিকে। তার আগে পর্যন্ত ঠোঁটের রঙ মানে ছিল গুঁড়া পিগমেন্ট, তেল-মশলার মিশ্রণ, যা ব্রাশ দিয়ে বা আঙুলে মেখে লাগাতে হতো। ১৮৮৪ সালে ফরাসি কোম্পানি গেরল্যাঁ বাজারে আনল এক নতুন ধরনের পণ্য—হরিণের চর্বি, মৌমাছির মোম আর ক্যাস্টর অয়েলের মিশ্রণে তৈরি তুলনামূলক নরম, সমানভাবে লাগানো যায় এমন লিপস্টিক, যা মোড়া থাকত বিশেষ কাগজে। ইতিহাসবিদদের অনেকে এটিকেই প্রথম বাণিজ্যিক আধুনিক লিপস্টিক হিসেবে মনে করেন। এখান থেকে শুরু হলো লিপস্টিকের mass product হয়ে ওঠা, আর একই সঙ্গে এটি যেন লিখতে শুরু করল নতুন রাজনৈতিক গল্প।
বিশ শতকের শুরুতে আমেরিকায় নারী ভোটাধিকার আন্দোলন জোরদার হলো। সেই সময় লাল লিপস্টিক এক নতুন পরিচয় পেল—মুক্তির প্রতীক হিসেবে। ১৯১২ সালে নিউইয়র্কের রাস্তায় মিছিল করা সাফ্রেজেটদের হাতে এলিজাবেথ আরডেন নিজে লিপস্টিকের টিউব তুলে দিলেন। মিছিলের ভিড়ে যখন শত শত নারী লাল ঠোঁট নিয়ে “আমিও ভোট দেব” বলছিলেন, তখন লিপস্টিক একেবারে সরাসরি রাজনৈতিক পাল্টা আওয়াজে পরিণত হয়। অনেক গবেষকের ভাষায়, সে সময়ে লিপস্টিক ছিল নারীর আত্মবিশ্বাসের ব্যাজ, শরীরে নয়, ঠোঁটে লেখা এক ঘোষণাপত্র।
তবে সৌন্দর্য আর রাজনীতির পাশাপাশি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ কাটেনি। কোথাও গুঁড়া পোকা আর তেলের মিশ্রণ কিছু ঘণ্টার মধ্যে দুর্গন্ধ ছড়াত, আবার কোথাও সিসা আর ভারমিলিয়নের মতো বিষাক্ত ধাতু ব্যবহারের ফলে দেখা দিত গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি। ১৯৩৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ফুড, ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট পাস হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে প্রসাধনে বিষাক্ত উপাদান নিষিদ্ধ করা হয়, রাজ্যভিত্তিক আইন আরও কঠোর হয়। ফলে লিপস্টিক ধীরে ধীরে বিষাক্ত ধাতু থেকে সরে এসে তুলনামূলক নিরাপদ পথের দিকে এগোয়।
এদিকে প্যাকেট ডিজাইনের ইতিহাসও এগোচ্ছে নাটকীয়ভাবে। ১৯২৩ সালে মরিস লেভি প্রথম ঘোরানো টিউবের লিপস্টিকের পেটেন্ট নিলেন। আজ যে টুইস্ট করে লিপস্টিক ওপরে উঠিয়ে ব্যবহার করি, সেই ধারণাটাই ছিল তার উদ্ভাবন। এর আগ পর্যন্ত লিপ কালার বহন করা ঝামেলাপূর্ণ ছিল, নতুন টিউবের কারণে লিপস্টিক হয়ে উঠল সত্যিকারের ‘পকেট সাইজ বিপ্লব’। পরে চল্লিশের দশক থেকে ফিফটিজে ফর্মুলা উন্নতির দৌড়ে যোগ দিলেন অনেক রসায়নবিদ; দীর্ঘস্থায়ী অথচ ঠোঁট শুকিয়ে না দেওয়া লিপস্টিক বানানো ছিল বড় লক্ষ্য। অনেক ব্যর্থতার পর হেজেল বিশপ তৈরি করলেন প্রথম বাস্তবসম্মত দীর্ঘস্থায়ী নন-স্মিয়ার লিপস্টিক, যা এক যুগের চেহারাই বদলে দিল।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লিপস্টিক সরাসরি যুদ্ধের প্রতীক হয়ে ওঠে পশ্চিমা জগতে। ফাইটিং রেড, ভিক্টরি রেড—এমন নামের শেড বাজারে এলো। এলিজাবেথ আরডেন বানালেন এমন লিপস্টিক, যার রঙ মহিলা সামরিক বাহিনীর ইউনিফর্মের সঙ্গে মিলে যায়। কারখানার মেয়েদের ড্রেসিংরুমে রাখা থাকত লিপস্টিক, যেন ক্লান্ত শরীরেও তারা ঠোঁটে রঙ টেনে নিজেকে শক্ত অনুভব করতে পারে। কথিত আছে, হিটলার লাল লিপস্টিক অপছন্দ করতেন; ফলে মিত্রশক্তির অনেক নারীর কাছে লাল ঠোঁট ছিল এক ধরনের নীরব প্রতিবাদ, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছোট্ট ব্যক্তিগত যুদ্ধ।
একুশ শতকের কাছাকাছি এসে আবার লিপস্টিক নতুন করে রাজপথে নামে। ২০১৮ সালে নিকারাগুয়ার সয় পিকো রোহো আন্দোলনে নারী-পুরুষ উভয়েই লাল লিপস্টিক লাগিয়ে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ২০১৯ সালে চিলিতে হাজারো নারী লাল ঠোঁট নিয়ে যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। পাঙ্ক সংস্কৃতিতে কালো বা গাঢ় বেগুনি ঠোঁট আবার অন্যরকম বিদ্রোহের ভাষা হয়—প্রথার বাইরে যাওয়ার ঘোষণা।
এর মধ্যে বদলে গেছে ভোক্তার মনও। শুধু সুন্দর দেখানোই নয়, আজকের ক্রেতা চায় ঠোঁট যেন আরাম পায়, শুকিয়ে না যায়, লিপস্টিকের ভেতর থাকুক ময়েশ্চারাইজার, ভিটামিন, প্রাকৃতিক উপাদান। ২০১৫–১৬ সালের দিকে বাজারে এসেছে এমনসব ‘মুড লিপস্টিক’—স্টিকে সবুজ, কিন্তু ঠোঁটে লাগানোর পর শরীরের তাপমাত্রা আর পিএইচ-এর সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে গোলাপি বা লাল হয়ে যায়। অন্যদিকে পশু-নির্যাতনবিরোধী পরীক্ষা, ভেগান ফর্মুলা, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন—এসব নিয়ে চলমান বিতর্ক প্রমাণ করে, লিপস্টিক এখন শুধু প্রসাধন নয়, বরং এক রাজনৈতিক অবস্থানও।
মহামারীর সময় যখন মাস্কের আড়ালে ঠোঁট লুকিয়ে গেল, তখনও অর্থনীতিবিদেরা কথা বললেন ‘লিপস্টিক ইনডেক্স’ নিয়ে—কতবার যে কঠিন সময়ের পর লিপস্টিক বিক্রি হঠাৎ বেড়ে গেছে, তার হিসাব আছে। বড় খরচ কমিয়ে মানুষ ছোট্ট, সস্তা আনন্দের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, যেমন নতুন লিপস্টিক কিনে ফেলা। সব বদল, সব নিষেধ, সব আতঙ্কের মাঝেও কয়েকটি সত্য টিকে থাকে—লিপস্টিক বারবার ফিরে আসে, আর প্রতিবারই তার সঙ্গে ফিরে আসে একটি নতুন অর্থ।
আজ যখন কেউ নিজের পছন্দের শেড বেছে নেয়—গভীর লাল, নরম নিউড, অদ্ভুত সব মভ–টোন, কিংবা দারুণ গাঢ় কালো—তখন তার ঠোঁটে শুধু একটি রঙ বসে না, বসে চার হাজার বছরের স্মৃতি। কখনো রাজমুকুটের গর্ব, কখনো পাপের ছাপ, কখনো ভোটের দাবি, কখনো স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে লাল ঘোষণা। এই ক্ষুদ্র রঙিন স্টিক তাই কেবল সৌন্দর্যের খেলনা নয়; এটি মানুষের স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশ, ধর্ম, নীতিশাস্ত্র আর রাজনীতির ইতিহাসের এক চলমান সাক্ষী। হয়তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি এসব কিছু ভেবে ঠোঁটে রঙ টানে না; তবু তার ছোট্ট সেই টান, অজান্তেই জুড়ে যায় কুইন শুবাদের লাল, ক্লিওপেট্রার কারমাইন, এলিজাবেথের রাজকীয় ঠোঁট আর সাফ্রেজেটদের মিছিলের সঙ্গে—একটানা চলতে থাকা রঙিন বিদ্রোহের সঙ্গে।






আপনার মতামত জানানঃ