 মানিকগঞ্জের ঘিওরের ছোট্ট শহরটার ওপর হঠাৎ যেন ঘনীভূত হয়ে নেমে এসেছে এক অস্বস্তিকর নীরবতা। কয়েক দিন আগেও যেখানে জাবরার “খালা পাগলীর মেলা”র মাঠজুড়ে ছিল বাউল–দরবেশদের বাঁশি, একতারার সুর, তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুলতে থাকা মানুষ, সেখানে এখন আলোচনার কেন্দ্র একটাই নাম—বাউল শিল্পী আবুল সরকার। পালাগানের মঞ্চে উচ্চারিত কয়েকটি বাক্য, মোবাইল ফোনে ধারণ করা কয়েক মিনিটের ভিডিও, আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝড় তোলা কিছু পোস্ট—সব মিলিয়ে লোকগান আর লোকআস্থার এই পুরোনো মেলাটাই রাতারাতি পরিণত হয়েছে “ধর্ম অবমাননার” অভিযোগ আর আইনি তৎপরতার মঞ্চে।
মানিকগঞ্জের ঘিওরের ছোট্ট শহরটার ওপর হঠাৎ যেন ঘনীভূত হয়ে নেমে এসেছে এক অস্বস্তিকর নীরবতা। কয়েক দিন আগেও যেখানে জাবরার “খালা পাগলীর মেলা”র মাঠজুড়ে ছিল বাউল–দরবেশদের বাঁশি, একতারার সুর, তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুলতে থাকা মানুষ, সেখানে এখন আলোচনার কেন্দ্র একটাই নাম—বাউল শিল্পী আবুল সরকার। পালাগানের মঞ্চে উচ্চারিত কয়েকটি বাক্য, মোবাইল ফোনে ধারণ করা কয়েক মিনিটের ভিডিও, আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝড় তোলা কিছু পোস্ট—সব মিলিয়ে লোকগান আর লোকআস্থার এই পুরোনো মেলাটাই রাতারাতি পরিণত হয়েছে “ধর্ম অবমাননার” অভিযোগ আর আইনি তৎপরতার মঞ্চে।
৪ নভেম্বর রাতের সেই পালাগানের আসরে ঠিক কী কী কথা উচ্চারিত হয়েছিল, তা এখন আর শুধু মেলার অতিথিদের স্মৃতির মধ্যে আটকে নেই। ঘিওরের জাবরায় খালা পাগলীর মেলায় পালাগানের আসর বসেছিল, যেখানে আবুল সরকার তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে প্রতিপক্ষ বাউলশিল্পীকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন—মহান আল্লাহ পাকের তিনটি সৃষ্টির মধ্যে কোনটি আগে, কোনটি পরে? প্রশ্নের ভঙ্গি, প্রতিপক্ষের সঙ্গে বৌদ্ধিক লড়াই, মাঝেমধ্যে কৌতুক—বাউল পালাগানের যুগান্তকারী ঐতিহ্যে এসবই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আজকের ডিজিটাল বাস্তবতায় সেই স্বাভাবিকতা খুব সহজেই “প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্ন” হয়ে যায়। কয়েক সেকেন্ডের খণ্ডিত ক্লিপ, কনটেক্সট–বিহীন কিছু সংলাপ আর উত্তেজনাপূর্ণ ক্যাপশন—এই ত্রয়ীই তৈরি করে দেয় নতুন এক জনরোষের আগুন।
ঘিওরের বন্দর মসজিদের ইমাম মুফতি মো. আবদুল্লাহ সেই ভিডিও দেখেই মামলা করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর অভিযোগ—আবুল সরকার জেনে–বুঝে আল্লাহ এবং ইসলামের বিশ্বাস নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন, যা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উসকানি হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। মামলার ভাষায় “ইচ্ছাকৃত অবমাননা”র এই অভিযোগ যখন থানার ডায়েরিতে নথিবদ্ধ হয়, তখন জাতীয়ভাবে পরিচিত এক লোকশিল্পীর নাম দ্রুতই অপরাধ–বিবরণীর আসামি কলামে চলে যায়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আর দেরি করেনি; মাদারীপুরে একটি গানের আসর থেকে তাঁকে আটক করে মানিকগঞ্জে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়, পরদিন হাজির করা হয় সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে, আর আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
এদিকে মানিকগঞ্জ আদালত প্রাঙ্গণে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় আলেম–ওলামা ও তাওহীদি জনতার ব্যানারে সংগঠিত মানুষরা। তারা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করে “ধর্ম অবমাননাকারীর কঠোর শাস্তি”র দাবিতে স্লোগান তোলে। খেলাফত মজলিসসহ বিভিন্ন ইসলামী দলের স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দিতে থাকেন, বাউল গানের নির্দিষ্ট কিছু প্রবণতাকে “আকিদাবিরোধী” এবং “ইসলাম বিদ্বেষী” হিসেবে চিত্রিত করেন। রাস্তার ভাষা আর আদালতের ভাষা এক নয়; কিন্তু একে অন্যকে প্রভাবিত করতে শুরু করলে তাতে যে উত্তেজনা তৈরি হয়, তা সামাল দিতে হয় শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকেই।
অন্যদিকে আবুল সরকারের সহশিল্পীদের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি আঁকে। সহকারী শিল্পী রাজু সরকার অভিযোগ করেন, পালাগানের পূর্ণ বক্তব্য প্রচার না করে একটি গোষ্ঠী কৌশলে ভিডিওর কেবল খণ্ডিত অংশ ছড়িয়ে দিয়েছে। সেই অংশগুলোতে শুধু প্রশ্ন বা চ্যালেঞ্জ শোনা যায়, কিন্তু তার উত্তর, যুক্তি, কিংবা পুরো তর্কের ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় না। তাঁর দাবি, আবুল সরকার আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে কোনো কটূক্তি করেননি; বরং মৌলবাদী ব্যাখ্যার সমালোচনা করেছেন, ধর্মের ভেতরের মানবিকতা তুলে ধরতে চেয়েছেন। বাউল ঐতিহ্যে এমন প্রশ্ন–উত্তর–ভিত্তিক পালা, জবাবি গান, দর্শনভিত্তিক বিতর্ক তো নতুন কিছু না; কিন্তু ডিজিটাল যুগে এই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো খুব সহজে একাকার হয়ে যায় “বিতর্কিত ক্লিপ” নামে।
মানিকগঞ্জের বাউল ঘরানা, খালা পাগলীর মেলা আর সেখানকার পালাগান—এগুলো শুধু বিনোদনের আয়োজন নয়, বরং বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির এক গভীর শিকড়। খালা পাগলীর মেলাকে ঘিরে প্রতিবছরই ঘিওর এলাকায় বাউল–ফকির, সাধক–দরবেশদের মিলনমেলা বসে; দোকানপাট, আলো, হাসি–আনন্দের পাশাপাশি থাকে গভীর রাতে তত্ত্বের পালা, ভক্তিমূলক গান, আধ্যাত্মিক তর্কবিতর্ক। এই পরিবেশে ধর্ম, ঈশ্বর, সৃষ্টিজগত, আত্মা–পরমাত্মা—এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রশ্ন তোলা, রূপক ব্যবহার করা, এমনকি প্রচলিত ধারার সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করা—এসবই বহুদিনের সাংস্কৃতিক চর্চা। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজ যখন ক্রমশ বেশি সংবেদনশীল এবং বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন এই একই চর্চা একসময় এসে দাঁড়ায় “ধর্ম অবমাননা নাকি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা”র প্রশ্নে।
বাংলাদেশে এ প্রথম নয়, বাউল বা লোকশিল্পীকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে আইনের মুখোমুখি হতে হলো—এর আগে শরিয়ত সরকার, রিতা দেওয়ানসহ আরও কয়েকজন শিল্পী একই ধরনের মামলায় গ্রেপ্তার, হয়রানি, দীর্ঘদিন কারাবাসের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। তাদেরও বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, গানের আসরে প্রশ্ন তুলেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন বা এমন কিছু বলেছেন—যা একটি অংশের দৃষ্টিতে ‘কুফরি’ বা ‘শিরক’ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা এক ধরনের উত্তেজনা এবার এসে পড়ছে আবুল সরকারের কাঁধে। পরিবেশ এমনভাবে বদলে গেছে যে, বাউলদের শত বছরের তপস্যা, সুর আর দর্শনের ভেতরে যতই ভক্তিভাব থাকুক না কেন, ভুল শব্দচয়ন, ভুল সময় আর ভুল ক্লিপ–এডিটিং সেকেন্ডের মধ্যে তাঁদের “অপরাধী”র আসনে বসিয়ে দিতে পারে।
এখানে আইনি প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নও। একদিকে ধর্মীয় অনুভূতি—যা অনেকের কাছে নিজের অস্তিত্বের গভীরে গেঁথে থাকা বিশ্বাসের সমতুল্য; অন্যদিকে শিল্পীর স্বাধীনতা—যেখানে প্রশ্ন তোলার, চ্যালেঞ্জ করার, বিদ্রূপের মাধ্যমেও সত্য অনুসন্ধানের সুযোগ থাকে। সংবিধান মতপ্রকাশ ও শিল্প–সংস্কৃতির স্বাধীনতার কথা বললেও বাস্তবে এই স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করে সমাজের ক্ষমতাবান গোষ্ঠী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আর প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতৃত্ব। এই গোষ্ঠীগুলোর চাপ–প্রতিক্রিয়া একদিকে আদালতে অভিযোগের ভাষা তৈরি করে, অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইক–শেয়ার–কমেন্টের ঢেউয়ের মধ্যে “সঠিক” আর “ভুল”কে তাড়াতাড়ি বিচার করে ফেলে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্ব পাওয়ার মত। আগে যেভাবে বাউল গানের শ্রোতা সীমিত ছিল মেলা, ওরশ বা উৎসবের মাঠে, এখন তা কয়েক মিনিটেই পৌঁছে যায় দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, প্রবাসের ঘরেও। স্মার্টফোনের ক্যামেরা, সস্তা ইন্টারনেট আর অ্যালগরিদম–নির্ভর নিউজফিড এমন এক পরিসর তৈরি করেছে, যেখানে কনটেক্সট হারিয়ে গিয়ে কেবল “উত্তেজনাপূর্ণ অংশ”টাই সামনে আসে। ধর্ম, রাজনীতি আর পরিচয়–রাজনীতির মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে এই খণ্ডিততা এক ধরনের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, যা পরে ঠান্ডা করতে হয় আইন, গুলি, কাঁদানে গ্যাস আর গ্রেপ্তারের মাধ্যমে।
তবে এই ছবি একরঙা নয়। একদল মানুষ যেমন আদালত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কঠোর শাস্তি দাবি করেছে, অন্যদিকে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় বাউল–শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী আর নাগরিক সমাজের একটি অংশ এই ধরনের মামলাকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ হিসেবে দেখছে। অতীতে শরিয়ত সরকারের মুক্তির দাবিতে যেমন বিশিষ্ট নাগরিকেরা বিবৃতি দিয়েছেন, মানববন্ধন করেছেন, তেমনি আবুল সরকারের গ্রেপ্তারের ঘটনাও নতুন করে প্রশ্ন তুলছে—ধর্মীয় অনুভূতি রক্ষার নামে কি শিল্প–সংস্কৃতির ওপর এক ধরনের অঘোষিত সেন্সরশিপ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না?
বাউল ঐতিহ্য নিজেই এসেছে এক ধরনের প্রতিবাদের ধারায়—যেখানে প্রচলিত কুসংস্কার, ভণ্ডামি, বাহ্যিক আড়ম্বরের বিরুদ্ধে কথা বলা হয় গান আর দর্শনের ভেতর দিয়ে। লালন ফকির, হাসন রাজা থেকে শুরু করে অসংখ্য নাম–না–জানা বাউল তাদের গান দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ধর্মের নামে বিভাজন আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে। সেই ধারাবাহিকতায় আজকের অনেক বাউলও মৌলবাদ, কুসংস্কার কিংবা ধর্মের নামে সহিংসতার সমালোচনা করেন। তাদের কেউ কেউ “শরীয়ত–বহির্ভূত”, কেউবা “কাফের” তকমাও জুটিয়ে নেন। যখন এই তর্ক মেলার মাঠের ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তা সহাবস্থানের এক ধরনের অনুশীলন; কিন্তু যখন সেটা মোবাইল ক্লিপ হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পৌঁছে যায়, আর সেখানকার উত্তেজিত জনতা বিষয়টি বিচার করে, তখন একই বাক্যও একেবারে অন্য অর্থ নিয়ে হাজির হয়।
আবুল সরকারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের আরেকটি দিক হলো “সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি”। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে দেখা গেছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোরআন অবমাননার কথিত পোস্ট, কোনো ধর্মীয় প্রতীককে অবমাননার অভিযোগ, বা গানের ভেতর কোনো রহস্যময় রেফারেন্স—এসবকে কেন্দ্র করে দ্রুতই জনতার রোষে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। ফলে প্রশাসন এখন অনেক বেশি আগেই “প্রিভেন্টিভ” অ্যাকশন নিতে চায়; অভিযোগ উঠলেই গ্রেপ্তার, মামলার নথিভুক্তি, আদালতে হাজিরা—এসবের মাধ্যমে তারা হয়তো সাময়িক ক্ষোভ ঠান্ডা করে, কিন্তু সেই সঙ্গে শিল্পীদের মনে তৈরি করে ভয় ও আত্ম–সেন্সরশিপের সংস্কৃতি।
একজন বাউলশিল্পীর গ্রেপ্তার মানে কেবল একজন ব্যক্তির ওপর মামলা নয়, বরং একটি দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ধারার ওপর চাপ সৃষ্টি করা। মানিকগঞ্জ–নরসিংদী–কুষ্টিয়া–ফরিদপুরের বাউল আড্ডাগুলোতে এখন আলোচনা হচ্ছে—কোন কথা বলা যাবে, কোন কথা বলা যাবে না; কোন গানের লাইন বাদ দিতে হবে, কোন অংশ গাইলে ভিডিওতে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। এই ভয় যদি ক্রমশ বাড়তে থাকে, তবে বাউলগানের সেই তাত্ত্বিক ধারাই ক্ষতিগ्रস্ত হবে, যেখানে প্রশ্ন করার, দ্বিমত পোষণের, এমনকি বিতর্কিত উপমা ব্যবহার করে সত্যকে খোঁজার সাহস ছিল।
আদালত এখনো আবুল সরকারের মামলার রায় দেয়নি, প্রমাণ–প্রক্রিয়া, সাক্ষ্যগ্রহণ—সবই বাকি। আইনের বিচারে তাঁকে দোষী বা নির্দোষ প্রমাণ করার দায়িত্ব বিচারব্যবস্থার। কিন্তু সমাজের আদালত অনেক আগেই রায় লিখে ফেলতে চাইছে—কেউ তাঁকে “ইমানের শত্রু”, কেউ তাঁকে “মতপ্রকাশের শহীদ” বানিয়ে ফেলছে। এই দুই মেরুর মাঝখানে যে ঠাণ্ডা মাথার আলোচনার জায়গা থাকা প্রয়োজন, সেটাই যেন সবচেয়ে বেশি অনুপস্থিত।
আজ যখন আমরা আবুল সরকারের নামটি শুনি, তখন একদিকে তাঁকে দেখি পীর–দরবেশ, সুফি ওস্তাদের শিষ্য হিসেবে, যিনি সারা জীবন পালাগান আর লোকগানে ডুবে থেকেছেন; অন্যদিকে দেখি একটি মামলার আসামি হিসেবে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ—তিনি নাকি সেই ঈমানকেই আঘাত করেছেন, যাকে তাঁর গান এতদিন জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। ঠিক এই দ্বৈত চিত্রটাই বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি—যেখানে ধর্ম, সংস্কৃতি, আইন আর রাজনীতি একে অন্যের ওপর উঠে বসে, কখনো আলিঙ্গন করে, কখনো গলা টিপে ধরে।
এখন প্রশ্ন, এই ঘটনায় আমরা কী শিখব? আমরা কি শুধু নতুন আরেকটি “ধর্ম অবমাননা মামলা”র তালিকায় আরেকটি নাম যোগ করে এগিয়ে যাব, নাকি সত্যিকার অর্থে বুঝতে চেষ্টা করব—কোথায় ধর্মীয় অনুভূতির যৌক্তিক সুরক্ষা আর কোথায় মতপ্রকাশের যৌক্তিক স্বাধীনতা? খালা পাগলীর মেলার মাঠ থেকে শুরু হওয়া এই তর্ক এখন কেবল মানিকগঞ্জের নয়; এটি পুরো দেশের, এমনকি আমাদের আগামী প্রজন্মের। বাউলের একতারা আর মসজিদের মাইক—দুয়ের মধ্যে যদি ন্যূনতম সংলাপের সেতু না থাকে, তাহলে যে শূন্যতা তৈরি হবে, সেখানে জায়গা করে নেবে ভয়, ঘৃণা আর সন্দেহ। আর সেই শূন্যতায় হারিয়ে যেতে পারে লোকসঙ্গীতের মায়া–মাখা সেই সুর, যে সুর একসময় ধর্ম, জাত–পাত, শ্রেণি—সব বিভাজন পেরিয়ে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে শিখিয়েছিল।



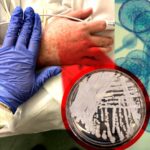


আপনার মতামত জানানঃ