
ভারতের আতিথ্যে থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ এশিয়ার কূটনীতিতে গত এক বছরে যে ধীরে-ধীরে বদল এসেছে, তার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রশ্ন—দিল্লি কি তাকে ক্রমান্বয়ে “আনলক” করছে? প্রশ্নটি নিছক কৌতূহল নয়; এতে জড়িয়ে আছে দিল্লি-ঢাকার টানাপোড়েন, বাংলাদেশের ভেতরকার রাজনৈতিক সমীকরণ, এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সূক্ষ্ম বার্তা-রাজনীতি। গত অগাস্টে ভারতে পা রাখার পর প্রথম কয়েক মাস যে কঠোর নীরবতা ও নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন, তা এখন অনেকটাই বদলে গেছে: অনলাইনে বক্তব্য, বিদেশে দলীয় সমর্থকদের উদ্দেশে লাইভ সংযোগ, এবং সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ—আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ধারাবাহিক লিখিত সাক্ষাৎকার। বিশেষ করে ২৯ অক্টোবর একসঙ্গে রয়টার্স, এএফপি ও দ্য ইন্ডিপেনডেন্টে প্রকাশিত লিখিত প্রশ্নোত্তর—যা ভারতীয় আতিথেয়তার বাস্তবতায় দিল্লির অগোচরে সম্ভব নয়, এমনই মনে করেন পর্যবেক্ষকেরা। এই ধারাবাহিক সাক্ষাৎকারে হাসিনার রাজনৈতিক অবস্থান, নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে সতর্কবার্তা ও ভারতে অবস্থান প্রসঙ্গে স্পষ্ট পয়েন্টগুলো প্রকাশ্যে এসেছে—তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নির্বাচন হলে ব্যাপক ভোটবর্জনের ঝুঁকি থাকবে এবং “ন্যায্য” প্রক্রিয়া ছাড়া তিনি ফিরবেন না।
ঢাকার দৃষ্টিতে এই দৃশ্যপট আরামদায়ক নয়। সরকারিভাবে তারা শুরু থেকেই অভিযোগ করছে, ভারতে অবস্থান করে হাসিনা অনলাইনে বক্তব্য দিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের উসকানি দিচ্ছেন; এমনকি প্রত্যর্পণ চুক্তির প্রসঙ্গ টেনে তাকে ফেরত চাওয়ার আনুষ্ঠানিকতাও ঘটেছে। দিল্লি পাল্টা বলেছে—সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কারও “মুখে লাগাম” দেয়া সম্ভব নয়, আর হাসিনা এখানে কোনো “রাজনৈতিক বন্দী” নন; সে অর্থে তার ফোন, অনলাইন অ্যাক্সেস বা পত্রপত্রিকা পড়ায় বিধিনিষেধ আরোপ করা ভারত সরকারের কাজ নয়। ফলে কাগজে-কলমে ভারত নিরপেক্ষ অবস্থান দেখালেও বাস্তবে যে হাসিনার গণমাধ্যম-অ্যাক্সেস দ্রুত বেড়েছে, তা অস্বীকারের উপায় নেই। এই দুটি বিপরীত সুর—ঢাকার আক্রমণাত্মক আপত্তি ও দিল্লির “হাত গুটিয়ে থাকা”—আসলে একই কূটনৈতিক খেলায় ভিন্ন ভিন্ন চাল। বিবিসি বাংলার বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনগুলোতে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এই তিক্ততার নানাদিক উঠে এসেছে; এবং সেখান থেকেই “আনলকিং” শব্দবন্ধটি আলোচনায় আসে।
কেন এখন? এর উত্তর খুঁজতে গেলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বোর্ডে চোখ রাখতে হয়। ঐকমত্য কমিশন, সনদ-প্রক্রিয়া, এবং দলভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা—সব মিলিয়ে আওয়ামী লীগের “রাজনৈতিক স্পেস” সংকুচিত। ভারতের কৌশলগত স্মৃতিতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে দীর্ঘদিনের কাজের সম্পর্ক রয়েছে; সীমান্ত-ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প—এ সম্পর্ক দিল্লির নিরাপত্তা চিন্তার সঙ্গে জুড়ে আছে। এমন অবস্থায় আওয়ামী লীগের কণ্ঠকে যদি মাঠে শূন্যে নামিয়ে রাখা হয়, দিল্লি অন্তত তাদের “ন্যারেটিভ সারভাইভাল”—বেঁচে থাকা বয়ান—নিশ্চিত করতে চাইতে পারে। এতে দিল্লি প্রকাশ্যে কোনো ভূমিকা না নিয়েও পরোক্ষে “ক্যাডেনস” ঠিক করতে পারে—কখন, কীভাবে, কোন প্ল্যাটফর্মে—আর হাসিনার লিখিত সাক্ষাৎকার বা লাইভ বক্তব্যগুলো সেই পরিকল্পিত ক্যাডেনসের মতোই লাগে। ২৯ অক্টোবরের সমন্বিত প্রকাশ এক্ষেত্রে নজির: একই দিনে তিন আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে বার্তা গেলে ঢাকার প্রতিক্রিয়া “টেস্টিং দ্য ওয়াটার” হিসেবে মাপা যায়, আর আওয়ামী সংগঠনে একযোগে মনোবল বাড়ানোর প্রভাবও পড়তে পারে।
অবশ্য দিল্লির ক্যালকুলাস কেবল প্রতিবেশী-নীতি নয়, নিজের আভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক অবস্থানও জড়িত। উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা সংবেদনশীল প্রেক্ষাপট, বে অব বেঙ্গল অঞ্চলে সমুদ্র-সংযোগ, কানেক্টিভিটি করিডোর—সব কিছুর সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতি সরাসরি সম্পর্কিত। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা–ইসলামাবাদ যোগাযোগের ঘনত্ব বা “সেভেন সিস্টার্স” প্রসঙ্গে বিতর্কিত ভাষ্য দিল্লির চোখে বিশ্রী সিগন্যাল। ফলে হাসিনার মুখ দিয়ে কিছু “কঠোর” কথা বলানো গেলে—যা ভারত সরকার সরাসরি বললে কূটনৈতিক খরচ বেশি—সেটা এক ধরনের নরম শক্তি প্রয়োগও বটে। এই “আউটসোর্সড টাফ-টক” কূটনীতির পাঠ্যবইয়ে নতুন নয়; দক্ষিণ এশিয়ায় বহুবার সরকার–ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক কণ্ঠের মাধ্যমে বার্তা পাঠানো হয়েছে। একে আপনি “পাবলিক ডিপ্লোম্যাসির গ্রে জোন” বলতে পারেন—যেখানে বক্তব্যের মালিকানা ব্যক্তি-নেতার হলেও সংকেত পৌঁছায় রাষ্ট্রীয় ঠিকানায়।
বাংলাদেশের ভেতরের ট্রায়াল-টাইমলাইনের দিকটি সমীকরণকে আরও জটিল করেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) ২০২৫ সালের মাঝামাঝি থেকে মানবতাবিরোধী অপরাধে হাসিনার বিরুদ্ধে অনুপস্থিত অবস্থায় বিচার চলছে; আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এর কাভারেজ বিস্তৃত। কোথাও কোথাও ট্রাইব্যুনালের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে; একইসঙ্গে “দায়মুক্তির সংস্কৃতি” ভাঙার যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে—ফলে প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক ও নৈতিক উভয় মাত্রায় তর্কসাপেক্ষ থেকে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে কয়েক মাস আগে একটি মামলায় হাসিনার বিরুদ্ধে কনটেম্পট রায়—রাজনীতির উত্তাপ আরও বাড়িয়েছে। সব মিলিয়ে বিচারপ্রক্রিয়া যত এগোয়, ততই তার বার্তার রাজনৈতিক ব্যাসার্ধ বাড়ে; দিল্লি এই ব্যাসার্ধকে মাথায় রেখেই “আনলকিং”–এর গতি নির্ধারণ করছে, এমনটাই যুক্তিযুক্ত অনুমান।
যে প্রশ্নটি বারবার ফিরে আসে—এই আনলকিংয়ের শেষ সীমানা কোথায়? আজ লিখিত সাক্ষাৎকার, কাল ভিডিও-ইন্টারভিউ, পরশু কি সামনাসামনি দীর্ঘ আলাপ? সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু প্রতিটি ধাপই শর্তাধীন। প্রথমত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নির্বাচনী ক্যালেন্ডার ও নিরাপত্তা-পরিস্থিতি—উত্তেজনা বাড়লে দিল্লি আবার “টেম্পারেচার কন্ট্রোল” বাড়াতে পারে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক ফোকাস—যে কোনো আইনি পর্যায়ে বড় অগ্রগতি হলে ভারত প্রকাশ্য আহ্বানের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করতে চাইবে। তৃতীয়ত, আঞ্চলিক খেলোয়াড়দের বার্তা—ওয়াশিংটন, ব্রাসেলস বা টোকিওর ইঙ্গিত-অনুস্বারে দিল্লির ট্যাকটিক্সে স্বল্পমেয়াদি সমন্বয় হতে পারে। এই তিন স্তরের যেকোনো একটিতে “রেড লাইন” ছোঁয়া মানেই আনলকিংয়ের গতি নেমে আসা—অথবা সাময়িক “ফ্রিজ”।
এখন প্রশ্ন—ঢাকা এই প্রবণতাকে কীভাবে পড়ছে? তারা একদিকে প্রত্যর্পণ-চুক্তি ও বিচারপ্রক্রিয়ার যুক্তি তুলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি চাইছে; অন্যদিকে “বিদেশে বসে উসকানি”—এই ভাষ্যে অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ডিজিটাল যুগে এক ক্লিকে সীমানা ভেঙে যায়; দিল্লি যদি প্রকাশ্য গাঁটছড়া না বেঁধেও এক ধরনের “নীরব সম্মতি” দেখায়, তাহলে ঢাকার হাতে কড়াকড়ির অস্ত্র কমে যায়। উপরন্তু, আওয়ামী লীগভিত্তিক সংগঠনে “নেতৃত্ব সক্রিয়”—এই সিগন্যাল মাঠপর্যায়ে সংগঠনিক রসদ যোগায়। এর ফলে নির্বাচনের মুখে প্রতীকী সংঘবদ্ধতা তৈরি হয়; প্রার্থিতা না-থাকলেও বার্তা-বিন্যাস ও সমর্থক-মনোবলে প্রভাব পড়তেই পারে।
দিল্লির জন্য ঝুঁকিটাও কম নয়। প্রথমত, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তাপমাত্রা যদি অতিরিক্ত বেড়ে যায়, সীমান্ত-পরিচালনা, বাণিজ্য, পানি-বণ্টন বা কানেক্টিভিটি প্রকল্পের আলোচনায় প্রতিক্রিয়া আসতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভারতের অভ্যন্তরে “আতিথেয়তা বনাম হস্তক্ষেপ”—এই বিতর্ক জেগে উঠতে পারে, বিশেষত যখন কোনো বিদেশি নেতা দিল্লি থেকে নিয়মিত রাজনীতির বার্তা দিচ্ছেন। তৃতীয়ত, আঞ্চলিক পাল্টা-বার্তা—যদি ঢাকা নীতিগতভাবে আরও দূরে সরে যায়, কিংবা ইসলামাবাদের সঙ্গে সমন্বয় ঘনীভূত হয়, তা ভারতের স্ট্র্যাটেজিক কমফোর্ট-জোনে খচখচানি তৈরি করবে। দিল্লি তাই দেখেশুনে, ধাপে ধাপে, “সিগন্যাল-কন্ট্রোল” করে এগোচ্ছে বলে মনে হয়—একবারে নয়, ছোট ছোট উইন্ডো খুলছে; প্রতিটি উইন্ডো খুলে দেখে নিচ্ছে বাতাস কোনদিকে বইছে।
বহুতল এই কূটনীতিতে একটি নীরব বাস্তবতা আছে—হাসিনা ও আওয়ামী লীগের পার্টি-ফিউচারের প্রশ্ন। রয়টার্সকে দেয়া লিখিত সাক্ষাৎকারে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ “তার বা তার পরিবারের ঘিরেই থাকতে হবে এমন নয়”—অর্থাৎ সম্ভাব্য উত্তরাধিকার-রাজনীতির জন্য দরজা খোলা। এটিকে কৌশলগত বার্তা হিসেবে দেখা যায়: একদিকে আন্তর্জাতিক অডিয়েন্সের কাছে “ব্যক্তি-নির্ভরতা কম” দেখানো, অন্যদিকে দলীয় ভেতরে বিকল্প নেতৃত্বের আলোচনাকে বৈধতা দেয়া। ভারত এই বার্তাকে স্বাগত জানাবে—কারণ ব্যক্তি-নির্ভর রাজনীতির ঝুঁকি আঞ্চলিক নীতিতে অনিশ্চয়তা আনে; বিকল্পের আভাস দিলেই ঝুঁকি-বিতরণ সহজ হয়।
তাহলে এই অতিবর্তমানের মধ্যে মিডিয়ার ভূমিকাই বা কী? পরিকল্পিত “ড্রিপ”—একদিন লাইভ, আরেকদিন লেখা সাক্ষাৎকার—এটা রাজনৈতিক মনোবিজ্ঞানের পুরনো ট্রিক। বেশি দিলে প্রতিরোধ জাগে, কম দিলে মনোযোগ সরে যায়। দিল্লির দৃষ্টিতে “ড্রিপ-ফিডিং” কাজে দেয়: আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রে পয়েন্টেড বার্তা গেলে ওয়েস্টার্ন ক্যাপিটালে “সিগন্যাল পিকআপ” হয়; দেশীয় সমর্থকদের জন্য লাইভ বা ইউটিউব যথেষ্ট। ঢাকার কাছে এটি বিরক্তির কারণ—কারণ প্রতিবারই তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে হয়, যা আলোচনাকে প্রশাসনিক এজেন্ডা থেকে টেনে আনে রাজনীতির কেন্দ্রে। মিডিয়া-ম্যানেজমেন্টই তাই এখানে কূটনীতির এক উপাঙ্গ।
আইনের কোর্টরুম এবং রাজনীতির কোর্ট অব পাবলিক ওপিনিয়ন—এই দুই মঞ্চে সমান্তরাল গল্প চলছে। আইসিটির অগ্রগতি, কনটেম্পট রায়, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার প্রশ্ন—সব মিলিয়ে বিচারপদ্ধতি “কঠোর কিন্তু বিতর্কিত” রেখায় হাঁটছে। রাজনৈতিকভাবে এর প্রতিফলন—আওয়ামী লীগের ওপর বেড়ে চলা চাপ, এবং হাসিনার দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে “মনোবল রাখো, আমি আছি”—এই ন্যারেটিভের পুনরাবৃত্তি। দিল্লির “আনলকিং” যদি এমনই নিয়ন্ত্রিত থাকে—তাহলে বছর ঘুরতে ঘুরতে আমরা হয়তো ক্যামেরার সামনে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারও দেখতে পারি; তবে সেটি হবে স্ক্রিপ্টেড ও নিরাপদ পরিবেশে, যেখানে কঠিন প্রশ্নের আগে-থেকেই “গার্ডরেল” বসানো থাকে।
সবশেষে, এই পুরো প্রক্রিয়াকে “কোভিড-লকডাউন”–উত্তর “আনলকিং”–এর সঙ্গে তুলনা করা যায়—শুরুতে সর্বোচ্চ সতর্কতা, পরে ধাপে ধাপে স্বাভাবিকতায় প্রত্যাবর্তন। পার্থক্য শুধু এখানেই যে, জনস্বাস্থ্য সংকটে আনলকিংয়ের মাপকাঠি ছিল সংক্রমণ-হার; আর হাসিনা-আনলকিংয়ে মাপকাঠি হলো কূটনৈতিক ঝুঁকি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও নির্বাচনী ক্যালেন্ডারের “মিশ্র সূচক”। যখন-যখন এই সূচকে ঝুঁকি বাড়বে, গতি কমবে; যখন-যখন ঝুঁকি কমবে, উইন্ডো আরও খুলবে। আপাতত লক্ষণ বলছে—উইন্ডোগুলো একটু একটু করে খোলা হচ্ছে, বার্তাগুলো মাপা গতিতে ছোঁড়া হচ্ছে, আর দিল্লি-ঢাকা দু’পক্ষই নিজেদের সুবিধামতো সেই বার্তাগুলো ব্যাখ্যা করছে। ভারতের কাছে এর মুনাফা—আওয়ামী লীগের “ন্যারেটিভ লাইফলাইন” সচল রাখা এবং উপযুক্ত সময়ে কঠোর সংকেত পাঠানোর “আর্মস-লেন্থ” সুবিধা; ঢাকার কাছে ক্ষতি—বিচার ও নিরাপত্তা-এজেন্ডার আড়ালে রাজনৈতিক ন্যারেটিভের পুনরুত্থান। কিন্তু রাজনীতির দীর্ঘ খেলায় আজকের ক্ষতি-লাভের খাতা শেষ কথা নয়; যে পক্ষ এই “সিগন্যালিং গেম”-এ ধৈর্য ধরে, টাইমিং মেপে, বার্তা নিয়ন্ত্রণ করে—সুযোগ শেষ পর্যন্ত তাদেরই দিকে যায়। এই যেমন এখন যাচ্ছে—ধীরে, শীতল মাথায়, একেকটি জানালা খুলে—আর প্রতিটি জানালা দিয়ে বাইরের বাতাস ঢুকে পড়ছে বাংলাদেশের রাজনীতির ঘরে।


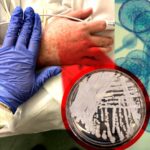


আপনার মতামত জানানঃ