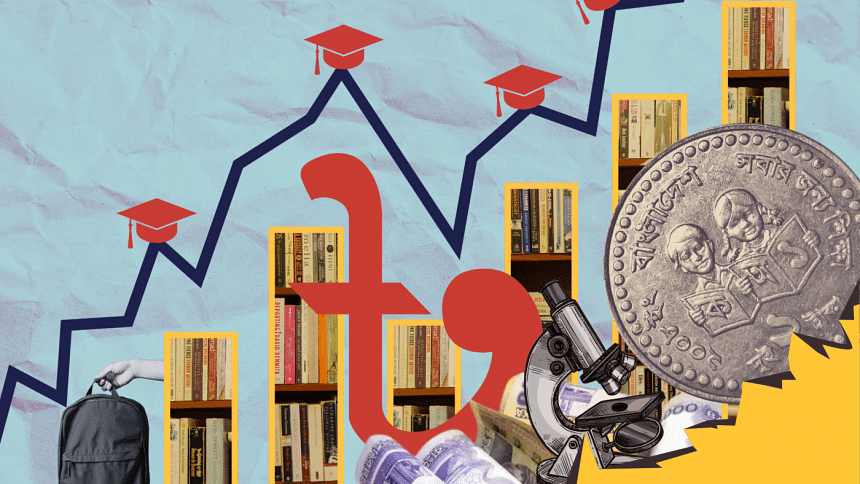 দেশের অর্থনীতি এখন এক ভজঘট অবস্থার মধ্যে পড়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞই বলছেন, বর্তমান পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে প্রতিটি খাতই কিছু না কিছুভাবে চাপের মুখে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, মূল্যস্ফীতি, উচ্চ সুদের হার, জ্বালানির ঘাটতি, এবং বিনিয়োগ স্থবিরতা—সব মিলিয়ে অর্থনীতির চাকা ঘুরছে খুব ধীরে। যে স্থিতিশীলতার আশা কিছুদিন আগেও ছিল, সেটিও এখন ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।
দেশের অর্থনীতি এখন এক ভজঘট অবস্থার মধ্যে পড়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞই বলছেন, বর্তমান পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে প্রতিটি খাতই কিছু না কিছুভাবে চাপের মুখে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, মূল্যস্ফীতি, উচ্চ সুদের হার, জ্বালানির ঘাটতি, এবং বিনিয়োগ স্থবিরতা—সব মিলিয়ে অর্থনীতির চাকা ঘুরছে খুব ধীরে। যে স্থিতিশীলতার আশা কিছুদিন আগেও ছিল, সেটিও এখন ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।
রফতানি খাত, যা এতদিন দেশের অর্থনীতির প্রধান ভরসা হিসেবে কাজ করছিল, সেটিও এখন দুর্বল হতে শুরু করেছে। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, টানা দুই মাস ধরে রফতানি আয় কমছে। আগস্ট মাসে রফতানি আয় প্রায় তিন শতাংশ কমেছে, আর সেপ্টেম্বরে কমেছে আরও ৪.৬১ শতাংশ। যদিও বছরের প্রথম তিন মাসে মোট রফতানি গত বছরের তুলনায় কিছুটা বেশি ছিল, কিন্তু ধারাবাহিক পতনের কারণে ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পাল্টা শুল্ক, ইউরোপে ক্রেতাদের চাহিদা হ্রাস এবং কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়াই এর পেছনের মূল কারণ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রভাব রফতানিতে সরাসরি পড়ছে। অনেক কারখানা নতুন অর্ডার পাচ্ছে না বা উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছে। এতে শুধু রফতানি আয় নয়, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও ধাক্কা লাগছে। পোশাক খাত, কৃষিপণ্য, পাটজাত দ্রব্য, প্লাস্টিক শিল্প—সব খাতেই এর প্রভাব স্পষ্ট। যদিও চামড়া, প্রকৌশল ও হিমায়িত খাদ্য খাতে কিছুটা ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গেছে, তা সামগ্রিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে যথেষ্ট নয়।
বেসরকারি খাতে বিনিয়োগও এখন কার্যত স্থবির। ঋণের উচ্চ সুদ এবং অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে উদ্যোক্তারা নতুন প্রকল্প হাতে নিতে সাহস পাচ্ছেন না। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে—মাত্র ৬.৩৫ শতাংশ। এটি ২০০৩ সালের পর সর্বনিম্ন হার। সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক উভয়ই এখন ঝুঁকি এড়াতে সরকারি বন্ডে বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী। ফলে প্রকৃত উৎপাদন খাতে অর্থের প্রবাহ কমে গেছে।
ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, উচ্চ সুদ এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে ব্যবসায়ীরা এখন বেশ সতর্ক। নির্বাচনের পর যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে, তাহলে বিনিয়োগ আবার বাড়বে বলে তার আশা। তবে এখনই এর কোনো বাস্তব ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না।
এদিকে দেশের মূল্যস্ফীতিও ফের বেড়ে গেছে। আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে সাধারণ মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৩৬ শতাংশে। সবজি, কাঁচামরিচ, চাল, পেঁয়াজসহ নিত্যপণ্যের দাম আকাশছোঁয়া। শহর ও গ্রাম—উভয় ক্ষেত্রেই জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জানায়, খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে ৭.৬৪ শতাংশ, আর খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ৯ শতাংশ।
ভোক্তা সংগঠন ক্যাবের সভাপতি এ এইচ এম সফিকুজ্জামান মনে করেন, বর্ষাকাল, সরবরাহ ঘাটতি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব—সব মিলিয়ে বাজার অস্থির হয়েছে। তিনি বলেন, “যদি কৃষক থেকে সরাসরি ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে দাম কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।”
অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা বলছেন, ব্যাংকের বর্তমান সুদের হার ব্যবসাবান্ধব নয়। এখন অনেক ব্যাংকে ঋণের সুদ ১৪ শতাংশের ওপরে, অথচ বেশিরভাগ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা ১০–১১ শতাংশের বেশি মুনাফা করতে পারেন না। তাই তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে সুদের হার কমিয়ে এক অঙ্কে নামানোর দাবি তুলেছেন। গভর্নর আহসান এইচ মনসুর তাদের আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী মুদ্রানীতিতে সুদের হার ধীরে ধীরে সিঙ্গেল ডিজিটে নামানো হবে।
বৈঠকে ব্যবসায়ীরা আরও প্রস্তাব দেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, কোভিড, এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতায় ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠন কমিটির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানো উচিত। রফতানিমুখী শিল্পে ব্যাংকিং জটিলতা দূর করতে বিশেষ কমিটি গঠনেরও দাবি ওঠে, যা বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে।
তবে এই নৈরাশ্যজনক চিত্রের মাঝেও কিছুটা আশার খবর আছে। শিল্পখাতের সম্প্রসারণ সূচক (PMI) সেপ্টেম্বরে ৫৯.১-এ পৌঁছেছে, যা আগের মাসের চেয়ে কিছুটা বেশি। সূচক ৫০-এর ওপরে থাকলে তা সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দেয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনুকূল আবহাওয়া এবং নতুন বাজেট বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও নির্মাণ খাত সম্প্রসারণে এসেছে। তবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ধীর করে দিচ্ছে।
একই সঙ্গে দেশের বৈদেশিক খাতেও কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) বাংলাদেশের চলতি হিসাবে ৪৮৩ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত রেকর্ড হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। প্রবাসী আয়ে ১৮.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং রফতানির প্রবাহ বৃদ্ধিই এই সাফল্যের মূল কারণ।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, আর্থিক হিসাবেও ঘাটতি অনেকটা কমে এসেছে—আগের বছরের ১.৪ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি নেমে এসেছে মাত্র ৫৩ মিলিয়নে। অর্থাৎ, বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ আগের চেয়ে অনেক স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে টাকার বিনিময় হারও কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে, যা আমদানি ব্যয়ের চাপ কমাতে সাহায্য করছে।
তবুও, সার্বিকভাবে দেখা যায়, অর্থনীতি এখন এক জটিল অবস্থায় রয়েছে। একদিকে মূল্যস্ফীতি, অন্যদিকে বিনিয়োগ স্থবিরতা; একদিকে রফতানিতে ধস, অন্যদিকে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা—সব মিলিয়ে যেন এক ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নির্বাচিত সরকারের অধীনে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে এলে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার সম্ভব। কিন্তু এর জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, সুদের হার নিয়ন্ত্রণ, জ্বালানি সরবরাহ স্থিতিশীল করা এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা।
অর্থনীতির এ ভজঘট অবস্থায় সাধারণ মানুষও কষ্টে আছে। বাজারে গেলেই বোঝা যায়, টাকার ক্রয়ক্ষমতা কতটা কমে গেছে। বেতন যেমন বাড়েনি, খরচ বেড়েছে দ্বিগুণ। যারা ব্যবসা করছেন, তারাও বলছেন, পণ্যের দাম বাড়লে বিক্রি কমে যায়, ফলে লাভের পরিমাণও কমে যায়।
সব মিলিয়ে বলা যায়, দেশের অর্থনীতি এখন এক কঠিন সময় পার করছে। তবু কিছু ইতিবাচক দিক আছে—রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ছে, কৃষি খাত ভালো অবস্থায় আছে, এবং বৈদেশিক লেনদেন কিছুটা ভারসাম্যে এসেছে। যদি এই ইতিবাচক দিকগুলো ধরে রাখা যায়, এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে অর্থনীতি আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন শক্ত নেতৃত্ব, বাস্তবসম্মত নীতি, এবং ব্যবসায়ীদের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা—যা এখন দেশের ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।






আপনার মতামত জানানঃ