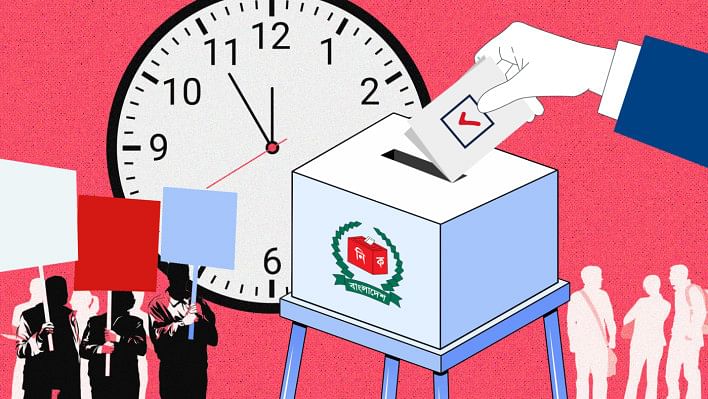 বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সবসময়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগ হয় ভোটের মাধ্যমে। নির্বাচনকাল ঘনিয়ে এলে রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পর্যন্ত সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এ প্রক্রিয়ার দিকে। নির্বাচন শুধু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নয়; এটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক গতিপথ নির্ধারণ করে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যে রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে, তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সবসময়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগ হয় ভোটের মাধ্যমে। নির্বাচনকাল ঘনিয়ে এলে রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পর্যন্ত সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এ প্রক্রিয়ার দিকে। নির্বাচন শুধু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নয়; এটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক গতিপথ নির্ধারণ করে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যে রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে, তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করা হবে এবং ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এই সময়ের মধ্যে কমিশন ২৪টি অগ্রাধিকারমূলক কাজ শেষ করবে। এর মধ্যে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ, হালনাগাদ ভোটার তালিকা চূড়ান্ত, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন, দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধন এবং তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার অন্যতম। মূল লক্ষ্য হলো একটি অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করা, যেখানে সব দল সমান সুযোগ পাবে এবং জনগণ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের উত্তেজনা ও দ্বন্দ্বের নজির আছে। কোনো কোনো নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় জনগণের আস্থায় ভাটা পড়েছে, আবার কিছু নির্বাচন রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও সহিংসতার জন্ম দিয়েছে। ফলে এ বার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিরোধী দলগুলোর আস্থা অর্জন। নির্বাচনকালীন সরকারের কাঠামো, ভোটের পরিবেশ ও প্রশাসনের নিরপেক্ষতা সবসময়ই আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। জনগণের প্রত্যাশা হচ্ছে— একটি নিরপেক্ষ কমিশনের অধীনে নির্বাচন, যেখানে প্রতিযোগিতা থাকবে কিন্তু প্রভাব খাটানো বা ভোটাধিকার হরণ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে না।
নির্বাচনের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বর্তমানে বৈশ্বিক মন্দা, ডলার সংকট, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ বাজারের অস্থিরতা দেশের অর্থনীতিকে চাপে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন আয়োজন মানে বিপুল অর্থ ব্যয়। ভোটকেন্দ্র স্থাপন, নির্বাচনী সামগ্রী সরবরাহ, নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর ভাতা সব মিলিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বাড়তি চাপ সৃষ্টি হবে। একই সময়ে জনগণের প্রত্যাশা থাকে, উন্নয়ন ব্যাহত না করে একটি কার্যকর ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা। তাই অর্থনৈতিক বাস্তবতাও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, সাধারণ মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে চায়। বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের মধ্যে রাজনৈতিক আগ্রহ বাড়ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যাপকতার কারণে রাজনৈতিক সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তরুণ প্রজন্ম উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সুশাসনকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীও ভোটের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখতে চায়। তাই ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণ করা যে কোনো রাজনৈতিক দলের জন্য অপরিহার্য।
প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রসঙ্গও নির্বাচন ঘিরে আলোচনায় রয়েছে। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিতর্ক আছে। একদিকে বলা হচ্ছে, এটি ভোট গণনায় গতি ও স্বচ্ছতা আনবে, অন্যদিকে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে গ্রামীণ এলাকায় যন্ত্র ব্যবহারের দক্ষতা, সচেতনতার অভাব ও প্রযুক্তিগত ত্রুটি নিয়ে। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হবে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও আস্থার পরিবেশ নিশ্চিত করা, যাতে ভোটাররা কোনোভাবেই বঞ্চিত বা বিভ্রান্ত না হন।
বাংলাদেশের নির্বাচন সবসময় আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রতি জোর দিচ্ছে। কারণ নির্বাচনের পর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নির্ভর করে বৈদেশিক বিনিয়োগ, উন্নয়ন সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির ওপর। এ জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ইসির জন্য অত্যন্ত জরুরি। এতে একদিকে যেমন নির্বাচন নিয়ে আস্থা বাড়বে, অন্যদিকে দেশের গণতান্ত্রিক অবস্থান আরও সুসংহত হবে।
নির্বাচনকালীন সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। অতীতে সহিংসতার ঘটনা ভোটারদের মনে ভীতি তৈরি করেছে। তাই নিরাপত্তা বাহিনীকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিতি কমে যেতে পারে, যা নির্বাচনের বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের দায়িত্বশীল আচরণও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
জনগণের প্রত্যাশা স্পষ্ট— তারা চায় এমন একটি নির্বাচন, যেখানে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ থাকবে এবং ভোটের ফলাফল তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটাবে। সাধারণ মানুষ রাজনীতির অচলাবস্থা নয়, বরং স্থিতিশীলতা চায়। নির্বাচনের পর সংসদে বিরোধী দলের কার্যকর ভূমিকা এবং সরকারের জবাবদিহিতা গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবে। তরুণ প্রজন্ম বিশেষভাবে আশাবাদী যে, তারা নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারবে।
সবশেষে বলা যায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। যদি নির্বাচন কমিশন তার ঘোষিত রোডম্যাপ সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে, তবে এটি হবে গণতন্ত্রের ভিত্তি আরও মজবুত করার এক সুবর্ণ সুযোগ। তবে ব্যর্থ হলে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা ও আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে পারে। তাই অংশগ্রহণমূলক, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারবে। এটি শুধু সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নয়; বরং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের নির্ধারক হয়ে উঠবে।






আপনার মতামত জানানঃ