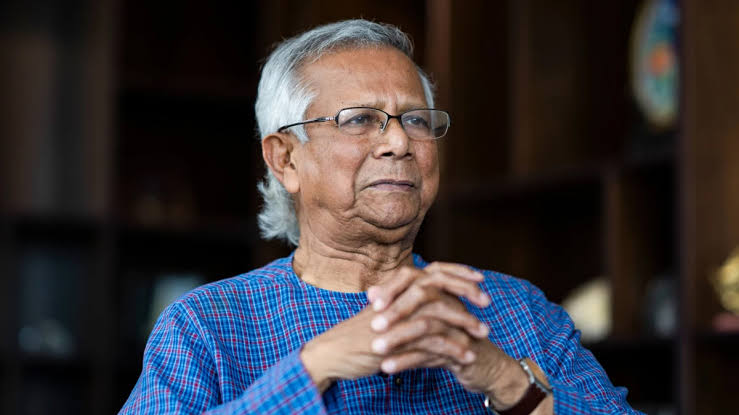 এই শহরে প্রতিদিনই কেউ না কেউ মরে। কখনো ককটেলের আঘাতে, কখনো গণপিটুনিতে, কখনো অবহেলা আর নিষ্ঠুরতার ধাপে ধাপে নির্মমতায়। তবু সব মৃত্যু এক রকম নয়। কোনো কোনো মৃত্যু সংবাদ শিরোনাম হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোকের বন্যা নামে, মোমবাতি জ্বলে, প্রতিবাদ মিছিল হয়। আবার কোনো কোনো মৃত্যু নীরবে পড়ে থাকে ফুটপাতের ধুলোয়, হাসপাতালের করিডরে কিংবা থানার নথির ভেতরে—যেন সেগুলো আসলেই মৃত্যুই নয়, কেবল পরিসংখ্যান।
এই শহরে প্রতিদিনই কেউ না কেউ মরে। কখনো ককটেলের আঘাতে, কখনো গণপিটুনিতে, কখনো অবহেলা আর নিষ্ঠুরতার ধাপে ধাপে নির্মমতায়। তবু সব মৃত্যু এক রকম নয়। কোনো কোনো মৃত্যু সংবাদ শিরোনাম হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোকের বন্যা নামে, মোমবাতি জ্বলে, প্রতিবাদ মিছিল হয়। আবার কোনো কোনো মৃত্যু নীরবে পড়ে থাকে ফুটপাতের ধুলোয়, হাসপাতালের করিডরে কিংবা থানার নথির ভেতরে—যেন সেগুলো আসলেই মৃত্যুই নয়, কেবল পরিসংখ্যান।
সিয়াম মজুমদার নামটি খুব অল্প সময়ের জন্যই আমাদের চোখে পড়েছে। ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় চা আনতে গিয়ে উড়ালসড়কের ওপর থেকে ছোড়া একটি ককটেলের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। একটি তরতাজা তরুণের শরীরের রক্ত-মাংস ছড়িয়ে পড়ে চায়ের দোকানের ওপর। সেই দৃশ্য এতটাই ভয়াবহ যে স্বাভাবিক মানবিক সংবেদনশীলতায় সেটি আমাদের ঘুম হারাম করে দেওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। দু-এক দিন সংবাদ হলো, কিছু ছবি ছাপা হলো, তারপর সিয়াম ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন আমাদের সম্মিলিত স্মৃতি থেকে।
সিয়াম কোনো রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, কোনো পরিচিত মুখ ছিলেন না, কোনো ‘গুরুত্বপূর্ণ’ পরিবারের সন্তানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মগবাজার এলাকার একটি চায়ের দোকানের কর্মচারী। খুলনার গ্রাম থেকে ঋণের বোঝা নিয়ে তাঁর পরিবার ঢাকায় এসেছিল। বাবা রিকশা চালাতেন, মা বাসাবাড়িতে কাজ করতেন। পরিবারের সবাই মিলে চেষ্টা করছিলেন কোনোমতে টিকে থাকার, ঋণ শোধ করার, একটু স্বস্তির জীবনের দিকে এগোনোর। সেই চেষ্টার মাঝখানেই ককটেলের আঘাতে থেমে গেল একটি জীবন। মায়ের মুখ থেকে বেরিয়ে এল সেই আর্ত বাক্য—“আমি আর ঢাকায় থাকমু না। ঢাকায় আইস্যা সব শেষ হইয়্যা গেল।” এই বাক্যের ভেতরে শুধু শোক নয়, আছে এই শহরের প্রতি গভীর এক অভিশাপ।
এই মৃত্যু কি আমাদের নাড়া দিয়েছে? আমরা কি এটিকে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা, সামাজিক নৈরাজ্য কিংবা রাজনৈতিক সহিংসতার ভয়াবহ ফল হিসেবে গভীরভাবে বিবেচনা করেছি? বাস্তবতা হলো, করিনি। কারণ সমাজ নির্দিষ্ট কিছু জীবনকে ‘শোকযোগ্য’ হিসেবে চিহ্নিত করে রাখে, আর বাকিদের ঠেলে দেয় ‘অশোকযোগ্য’ অন্ধকারে। সিয়াম সেই অন্ধকারের মানুষ।
এই তালিকায় সিয়াম একা নন। ওমর ফারুকও আছেন। রাজশাহীর বাগমারার এক ভ্যানচালক, যিনি চুরির অভিযোগে গণপিটুনির শিকার হয়ে এমন এক নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করেছেন, যা পড়লে গা শিউরে ওঠে। তাঁকে লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়েছে, হাত-পায়ে পেরেক ঠুকে দেওয়া হয়েছে, পানির জন্য কাকুতি-মিনতি করলে নদীতে চুবিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে, এমনকি পায়ুপথে শুকনা মরিচের গুঁড়া ঢেলে দেওয়া হয়েছে। এসবের পরও যেন নির্যাতনকারীদের ক্ষুধা মেটেনি। পরে নাটক সাজিয়ে তাঁকে প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত বসে, ১০০ টাকা জরিমানা আর সাত দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর হাসপাতাল, কারাগার, আবার হাসপাতাল—শেষ পর্যন্ত মৃত্যু।
এই মৃত্যু কি আমাদের বিবেককে কাঁপিয়েছে? গণপিটুনি নিয়ে দু-চারটি সাধারণ আলোচনা ছাড়া কি কোনো গভীর আত্মসমালোচনা হয়েছে? হয়নি। কারণ ওমর ফারুকও সেই শ্রেণির মানুষ, যাঁদের মৃত্যু সমাজের চোখে খুব বেশি মূল্য রাখে না। তিনি কোনো প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অংশ নন, তাঁর পেছনে নেই কোনো রাজনৈতিক পতাকা, নেই কোনো সংগঠনের শক্ত কণ্ঠ।
এখানেই প্রশ্নটা আরও গভীর হয়। আমরা কি আদৌ সব মৃত্যুকে সমান চোখে দেখি? ‘সব মানুষের রক্ত লাল’—এই কথাটি আমরা খুব সহজে বলি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, রক্তের রং নয়, মানুষটির সামাজিক অবস্থানই নির্ধারণ করে তাঁর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া। কারও মৃত্যুতে রাষ্ট্র শোক প্রকাশ করে, কারও মৃত্যুতে কেবল একটি মামলা নম্বর খোলা হয়। কারও মৃত্যুর পর টক শো হয়, কলাম লেখা হয়, আবার কারও মৃত্যু কাগজের ভেতরের পাতাতেই চাপা পড়ে যায়।
এই বাস্তবতা নতুন নয়। সমাজতাত্ত্বিকরা বহু আগেই বলেছেন, রাষ্ট্র ও সমাজ নির্দিষ্ট কিছু জীবনকে ‘গ্রিভেবল’ বা শোকযোগ্য হিসেবে নির্মাণ করে। এই নির্মাণের পেছনে কাজ করে শ্রেণি, ক্ষমতা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক অবস্থান। যাঁরা সমাজের সুবিধাভোগী অংশের অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের মৃত্যু মানেই ‘ক্ষতি’। আর যাঁরা শ্রমজীবী, দরিদ্র, প্রান্তিক—তাঁদের মৃত্যু যেন স্বাভাবিক, অনিবার্য, প্রায় অনুমিত।
মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি আরও নির্মমভাবে পরিষ্কার হয়। একটি কারখানার যন্ত্র নষ্ট হলে সমাজ শোক করে না, কেবল হিসাব করে কীভাবে সেটি দ্রুত মেরামত করা যায়। শ্রমিকের মৃত্যু হলেও সমাজের বড় অংশের প্রতিক্রিয়া প্রায় একই রকম। সিয়াম বা ওমর ফারুকদের মৃত্যুতে আমরা শোক না করে কেবল পরের দিনের খবরের দিকে তাকাই। কারণ এই মানুষগুলোকে আমরা অবচেতনে ‘ব্যবস্থার যন্ত্রাংশ’ হিসেবেই দেখে অভ্যস্ত।
এই অপ্রকাশযোগ্য শোক আসলে আমাদের সামষ্টিক ব্যর্থতার দলিল। রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। সরকার ব্যর্থ হয়েছে সহিংসতা ঠেকাতে। নাগরিক সমাজ ব্যর্থ হয়েছে শক্ত প্রতিবাদ গড়ে তুলতে। বুদ্ধিজীবীরা ব্যর্থ হয়েছেন এই মৃত্যুগুলোকে কেন্দ্র করে দীর্ঘস্থায়ী নৈতিক প্রশ্ন তুলতে। মানবাধিকারকর্মীরা ব্যর্থ হয়েছেন ধারাবাহিক চাপ তৈরি করতে। রাজনৈতিক মহল ব্যর্থ হয়েছে কারণ এই মৃত্যুর সঙ্গে তাদের তাৎক্ষণিক স্বার্থ জড়িত নয়।
সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো, আমরা ধীরে ধীরে এসব মৃত্যুতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। গণপিটুনি, ককটেল বিস্ফোরণ, পথচারীর মৃত্যু—এসব যেন দৈনন্দিন জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে উঠছে। এই স্বাভাবিকীকরণই সবচেয়ে বড় বিপদ। কারণ যখন মৃত্যু স্বাভাবিক হয়ে যায়, তখন মানবিকতা ধীরে ধীরে মরতে শুরু করে।
সিয়ামের মা যখন বলেন, “সব শেষ হইয়্যা গেল”, তখন সেটি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত শোকের ভাষা নয়। এটি একটি শ্রেণির মানুষের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ। এই শহর তাঁদের দেয় কেবল শ্রমের সুযোগ, নিরাপত্তা দেয় না। জীবন কেড়ে নিলে শহরের কিছুই যায় আসে না। কারণ তাঁরা বদলযোগ্য, প্রতিস্থাপনযোগ্য।
আমাদের শোকের ব্যাকরণে তাই সিয়াম মজুমদার বা ওমর ফারুকদের জন্য কোনো অধ্যায় নেই। নেই কোনো রাষ্ট্রীয় স্মরণ, নেই কোনো জাতীয় প্রশ্ন। অথচ প্রশ্ন থাকা উচিত—কেন একটি তরুণ চা আনতে গিয়ে ককটেলে মারা যাবে? কেন চুরির অভিযোগে একজন মানুষকে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় হত্যা করা হবে? কেন এসব ঘটনার পরও অপরাধীরা এতটা নিশ্চিন্ত থাকে?
এই প্রশ্নগুলো না তুললে অপ্রকাশযোগ্য শোক আরও দীর্ঘ হবে। আরও অনেক সিয়াম, আরও অনেক ওমর ফারুক আমাদের চোখের সামনে হারিয়ে যাবে। আর আমরা হয়তো আবারও বলব—সব মানুষের রক্ত লাল। কিন্তু সেই লাল রক্ত যে মাটিতে শুকিয়ে যাচ্ছে, তার দায় আমরা নিতে শিখব না।
শেষ পর্যন্ত শোক প্রকাশ করাটাই শুধু আবেগের বিষয় নয়, এটি একটি রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থান। কার জন্য আমরা শোক করি, আর কার জন্য করি না—সেখানেই স্পষ্ট হয়ে যায় আমরা কেমন সমাজে বাস করছি। যদি আমরা সত্যিই মানুষ হিসেবে নিজেদের মূল্যায়ন করতে চাই, তাহলে অপ্রকাশযোগ্য শোকের এই মৃত্যুগুলোকে প্রকাশযোগ্য করে তুলতেই হবে। নইলে ‘সব শেষ হইয়্যা গেল’ শুধু একটি মায়ের কান্না নয়, আমাদের সামষ্টিক ভবিষ্যতের পূর্বাভাস হয়ে থাকবে।






আপনার মতামত জানানঃ