 জেলা প্রশাসনের চোখ–কান যদি সাত থেকে ১৫ দিন দেরিতে কাজ করে, তবে সে জেলার আইন–শৃঙ্খলার আসল চালকের আসনে বসে আছে কে? প্রশ্নটা শুধু আমলাতান্ত্রিক কোনো বিধান নিয়ে নয়; প্রশ্নটা নাগরিক নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং আসন্ন নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। বণিক বার্তার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমন এক বাস্তবতা, যেখানে থানায় নথিভুক্ত মামলার এজাহার ও জিডির তথ্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিদিন যাওয়ার কথা, কিন্তু বাস্তবে তা পৌঁছাতে সময় লাগছে এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহ। এর মধ্যে অনেক অপরাধী গা–ঢাকা দিতে পারছে, অনেক “সাদা পোশাকে তুলে নেওয়া” ঘটনা কোনোদিনই আলোচনার টেবিলে ওঠে না, আর জেলা আইন–শৃঙ্খলা সমন্বয় কমিটি কার্যত অন্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়—যেন পিছনের আয়নায় তাকিয়ে সামনে গাড়ি চালানোর চেষ্টা।
জেলা প্রশাসনের চোখ–কান যদি সাত থেকে ১৫ দিন দেরিতে কাজ করে, তবে সে জেলার আইন–শৃঙ্খলার আসল চালকের আসনে বসে আছে কে? প্রশ্নটা শুধু আমলাতান্ত্রিক কোনো বিধান নিয়ে নয়; প্রশ্নটা নাগরিক নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং আসন্ন নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। বণিক বার্তার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমন এক বাস্তবতা, যেখানে থানায় নথিভুক্ত মামলার এজাহার ও জিডির তথ্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিদিন যাওয়ার কথা, কিন্তু বাস্তবে তা পৌঁছাতে সময় লাগছে এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহ। এর মধ্যে অনেক অপরাধী গা–ঢাকা দিতে পারছে, অনেক “সাদা পোশাকে তুলে নেওয়া” ঘটনা কোনোদিনই আলোচনার টেবিলে ওঠে না, আর জেলা আইন–শৃঙ্খলা সমন্বয় কমিটি কার্যত অন্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়—যেন পিছনের আয়নায় তাকিয়ে সামনে গাড়ি চালানোর চেষ্টা।
পুলিশ প্রবিধান অনুযায়ী সার্কেল সহকারী পুলিশ সুপারকে (এএসপি) এফআইআর ও জিডি থেকে তথ্যানুসারে বিপি ফরম–১৬ পূরণ করে প্রতিদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানোর কথা। এই ফরমের ওপর ভিত্তি করেই জেলার কোথায় কী ধরনের অপরাধ বাড়ছে, কোথায় ধরপাকড়, কোথায় চাঁদাবাজি, কোথায় রাজনৈতিক উত্তেজনা—এসবের দ্রুত চিত্র পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে জেলা প্রশাসকরা বলছেন, ওই ফরম নিয়মিত আসে না; বরং জেলা পুলিশের বিশেষ শাখা আর এসপি অফিস থেকে সপ্তাহে একবার “গোপনীয় প্রতিবেদন” আর পাক্ষিকে একবার সারাংশ পাঠানো হয়। ফলে দিনের অপরাধ সম্পর্কে জেলা প্রশাসনের আনুষ্ঠানিক ধারণা তৈরি হতে হতে অপরাধী অনেক সময় নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যায়।
এখানেই তৈরি হয়েছে একটি মৌলিক সমস্যা। আইনের ভাষায় জেলা আইন–শৃঙ্খলা কমিটি হচ্ছে জেলার সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমন্বয়কারী প্ল্যাটফর্ম—যেখানে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সভাপতি, পুলিশ সুপার (এসপি) সদস্য–সচিবসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি থাকেন। এই কমিটি যদি প্রতিদিনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য না পায়, তবে তাদের সভা পরিণত হয় “খবর পেছনের মাসের, সিদ্ধান্ত আজ” ধরনের আনুষ্ঠানিকতায়। এতে একদিকে নাগরিকের অভিযোগের দ্রুত প্রতিকার হয় না, অন্যদিকে নির্যাতন, অবৈধ আটক বা অর্থ আদায়ের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কৌশলগত হস্তক্ষেপ করার সুযোগও সংকুচিত হয়ে পড়ে।
অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. তৌহিদুল হক খুব স্পষ্ট করে বলছেন—এটা মূলত সমন্বয়ের সংকট, ক্ষমতার নয়। প্রতি বছর ডিসি–এসপি সম্মেলনে বারবার বলা হয়, প্রশাসন ও পুলিশের সমন্বয় ছাড়া জেলার কাঙ্ক্ষিত আইন–শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু মাঠের বাস্তবতা হচ্ছে, অনেক জায়গায় ডিসি অফিস আর এসপি অফিসের মধ্যে এক ধরনের “নীরব যুদ্ধ” চলে, কে আগে, কে বড়—এই ক্ষমতার হিসাব অনেক সময় নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকারের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। ফলাফল, দু’পক্ষের মধ্যে অবিশ্বাস; কেউ কাউকে পুরো চিত্র জানাতে চায় না, কেউ কাউকে “অতিরিক্ত প্রভাবশালী” হতে দিতে চায় না। অথচ নাগরিকের জন্য প্রয়োজন ছিল উল্টোটা—দু’পক্ষ একে অন্যের সহযোগী হয়ে কাজ করবে, তথ্য ভাগাভাগি করবে, দায়িত্বও ভাগ করবে।
জেলা প্রশাসকদের কিছু অভিজ্ঞতা এই সংকটের গভীরতা আরও স্পষ্ট করে। কেউ কেউ বলছেন, অতীতে অনেক জেলায় দেখা গেছে—আইন–শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বৈঠকে এসপিরা ডিসি অফিসের কাউকে রাখতে অনীহা প্রকাশ করেছেন, আবার কখনো এসপি নিজে না গিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে পাঠিয়েছেন; অথচ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ছিল ডিসি ও এসপির উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। আরও আছে ডিসি–এসপির পারস্পরিক অভিযোগের ইতিহাস—কেউ কেউ সদর দপ্তরে গিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। এই দূরত্বের পটভূমিতে যখন জেলা প্রশাসন থানার প্রতিদিনের তথ্য চেয়ে ২০২১ সাল থেকে পাঁচবার চিঠি দিয়েছে, আর পুলিশ সদর দপ্তর কার্যত ‘নীরব প্রতিক্রিয়া’ দেখিয়েছে, তখন বোঝা যায়—সমস্যাটি কাগজের নিয়ম না মানার চেয়েও বড়; এটি আস্থার, সংস্কৃতির, আর ভূমিকা–বোধের সংকট।
পুলিশের এক অংশের যুক্তি—এফআইআর ও জিডির প্রতিদিনের তথ্য জেলা প্রশাসকের জন্য এতটা জরুরি নয়। তাদের মতে, ব্রিটিশ আমলে যখন জেলার সব ক্ষমতা জেলা প্রশাসকের হাতে ছিল, তখন এই ধারাটি যুক্তিসঙ্গত ছিল; এখন পরিস্থিতি বদলেছে, আইন–শৃঙ্খলা কার্যত পুলিশের হাতেই। তাই প্রতি মাসের আইন–শৃঙ্খলা সভার আগেই সামগ্রিক সারাংশ পাঠিয়ে দিলেই যথেষ্ট। একজন এসপি–স্তরের কর্মকর্তা তো পরিষ্কার বলেছেন, “জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পুলিশের তেমন কোনো কাজ নেই, মোবাইল কোর্ট চালালে আমরা সহযোগিতা করি”—অর্থাৎ আইন–শৃঙ্খলা বলতে পুলিশের দৃষ্টিতে মূলত অপরাধী ধরা, মামলা করা, আর জেলা প্রশাসকের কাজ শুধু কিছু ভ্রাম্যমাণ আদালত, কাগুজে প্রতিবেদন ও প্রটোকল সামলানো।
এই দৃষ্টিভঙ্গি তিনটি জায়গায় বিপজ্জনক। প্রথমত, বাংলাদেশের আইন–শৃঙ্খলা ধারণা কখনোই একক প্রতিষ্ঠানের ওপর দাঁড়িয়ে নেই; ম্যাজিস্ট্রেসি, প্রশাসন, পুলিশ, স্থানীয় সরকার—সব মিলে একটি চেইন। এই চেইনের কোনো জায়গায় তথ্য আটকে গেলে সামগ্রিক জবাবদিহি ভেঙে পড়ে। দ্বিতীয়ত, “জেলা প্রশাসনের ভূমিকা কম” ধারণা যত বেশি শক্ত হয়, তত বেশি বাড়ে অনিয়মের সুযোগ—সাদা পোশাকে তুলে নেওয়া, গুমের চেষ্টা, অবৈধ অর্থ আদায়—এসবের বিরুদ্ধে তখন আর কোনো বিকল্প চেক–অ্যান্ড–ব্যালান্স থাকে না। তৃতীয়ত, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে যে ইতিমধ্যেই সংবেদনশীল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, সেখানে প্রতিটি থানার প্রতিটি ছোট–বড় অপরাধের খবর জেলা প্রশাসনের কাছে দ্রুত না পৌঁছালে নির্বাচনী সহিংসতা, রাজনৈতিক প্রতিশোধ কিংবা টার্গেটেড ধরপাকড়—এসব বিষয় নজরের বাইরে থেকে যেতে পারে।
নির্বাচনী সময়ে একটি জেলার চিত্র মুহূর্তে বদলে যেতে পারে। কোনো এলাকায় হঠাৎ করে বিরোধী দলের কর্মীদের ওপর হামলা, অন্য কোথাও প্রার্থী সমর্থকদের ধাওয়া–পাল্টা ধাওয়া, আবার কোথাও “অজ্ঞাত পরিচয়” লোকদের রাতের ঢুকে বাড়ি ভাঙচুর—এসব ঘটনা যদি সঙ্গে সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নজরে না আসে, তাহলে তিনি নির্বাচন কমিশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা কেন্দ্রের সঙ্গে কীভাবে সমন্বয় করবেন? সাত–দশ দিন পর যখন ফাইল–চালাচালি করে “সাপ্তাহিক গোপনীয় প্রতিবেদনে” সেই তথ্য আসে, তখন হয়তো নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণাও শেষ, সংঘটিত ক্ষতির কিছুই আর ঠিক করার থাকে না। আবার মাঠে যারা রয়েছেন, তাদের একাংশ মনে করেন, “সবাই তো জানে, তবু কিছু করা হয়নি”—এই বোধ নির্বাচন নিয়ে মানুষের আস্থা আরও কমিয়ে দেয়।
একই সঙ্গে নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নটাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন, কোনো ব্যক্তি বা রাজনৈতিক কর্মীকে সাদা পোশাকে তুলে নেওয়া হলো। পরিবার–পরিজন থানায় গেলে বলা হলো, “এমন কাউকে তো আমরা আনিনি।” এই অবস্থায় যদি জেলার আইন–শৃঙ্খলা কমিটি প্রতিদিনের তথ্য–প্রবাহের মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তাহলে অন্তত জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকে—কাকে কোথা থেকে, কোন আইনে আটক করা হয়েছে? কিন্তু যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই তথ্যের দিক থেকে অন্ধকারে থাকেন, তখন ভুক্তভোগী পরিবার কার কাছে যাবে? প্রশাসনের এই তথ্য–বঞ্চনা অনিবার্যভাবে বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে আরও পুষ্ট করে।
অবশ্য সব জেলা একই রকমও নয়। সিলেটের জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলমের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, অন্তত কিছু জায়গায় মৌখিক সমন্বয়, উল্লেখযোগ্য অপরাধের খবর ভাগাভাগি, যৌথ অভিযান—এসব হয়েই থাকে। কিন্তু মৌখিক সমন্বয় কখনোই লিখিত, নিয়মিত ও কাঠামোবদ্ধ তথ্যপ্রবাহের বিকল্প হতে পারে না। মৌখিক সমন্বয় নির্ভর করে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর; ডিসি–এসপি বদলালেই সেই সমন্বয় ভেঙে পড়ার ঝুঁকি থাকে। বিপি ফরম–১৬, দৈনন্দিন এফআইআর ও জিডির তথ্য—এসব হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি ও জবাবদিহির ভিত্তি, যা ব্যক্তিনির্ভরতার বাইরে একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে।
এখানে একটি পুরোনো যুক্তি আবার সামনে আসে—“ব্রিটিশ আমলের বিধান, এখন সময় বদলেছে।” সত্যি, ব্রিটিশ শাসনামলে জেলা প্রশাসক ছিলেন ক্রাউন–এর প্রতিনিধি; জেলা পুলিশের ওপর তাঁর কড়া তদারকি ছিল, আর আজকের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, পুলিশ প্রশাসনের প্রফেশনাল স্বাধীনতা—এসব প্রশ্ন আছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা যদি তথ্য–গোপন করে একধরনের “সর্বেসর্বা” মানসিকতায় পরিণত হয়, আর জেলার নির্বাচনী ও নাগরিক নিরাপত্তার মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছেই প্রতিদিনের অপরাধের তথ্য না যায়, তাহলে তা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নীতির সঙ্গেই সাংঘর্ষিক।
বরং প্রয়োজন—পুরোনো বিধানকে সময়োপযোগী করা, নতুন প্রযুক্তি ও ডেটা–ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো। আজ যখন প্রায় সব থানাই অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ক্রাইম ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করছে, তখন জেলা প্রশাসকের কাছে প্রতিদিনের ফিজিক্যাল ফরম পৌঁছে না যাওয়ার যুক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। একটি সুরক্ষিত, অথরাইজড ড্যাশবোর্ডে ডিসি অফিসের নির্দিষ্ট কর্মকর্তারা যদি প্রতিদিনের এফআইআর ও জিডির তালিকা দেখতে পারেন, তাহলে পুলিশের “অতি ব্যস্ততার” যুক্তি মিলিয়ে যায়। একই ড্যাশবোর্ড থেকে আবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা নির্বাচন কমিশনও জেলার লাইভ অপরাধ–চিত্র দেখতে পারে—যা “সাতদিন পরে রিপোর্ট”–এর চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।
অবশ্য প্রযুক্তি দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয় না, যদি মানসিকতার পরিবর্তন না আসে। জেলা প্রশাসন–পুলিশ সম্পর্কের সংকটের পেছনে আছে “কে কাকে নিয়ন্ত্রণ করবে” এই অদৃশ্য প্রশ্ন। সমন্বয়কে কেউ কেউ মনে করেন মর্যাদা কমে যাওয়ার লক্ষণ, যেন একসঙ্গে বসে কাজ করা মানেই ক্ষমতা হারানো। এই মানসিকতার পরিবর্তন না হলে যত নির্দেশনাই আসুক, যত চিঠিই যাক সদর দপ্তরে, মাঠপর্যায়ে খুব বেশি পরিবর্তন আসবে না।
এখানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেরও দায়িত্ব আছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় যদি বারবার এই সমস্যা উঠে আসে, আর তবু কোনো বাস্তবিক পরিবর্তন না হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে—নির্দেশনার কার্যকর মনিটরিং হচ্ছে কি না। একইভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বা নির্বাচন কমিশন—যারা মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন–পুলিশ সমন্বয়ের ওপর অন্তত নীতি–নির্ধারণী প্রভাব রাখে—তাদেরও উদ্যোগী হতে হবে। তারা চাইলে ডিসি–এসপি কনফারেন্সে এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার এজেন্ডা করতে পারে, যৌথ প্রশিক্ষণ, ইনসেনটিভ–স্ট্রাকচার, এমনকি ভালো সমন্বয়ের জন্য পুরস্কার–ব্যবস্থাও রাখতে পারে।
সর্বোপরি, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোকেও এই আলোচনায় যুক্ত হতে হবে। তারা যদি কেবল কোনো ঘটনা ঘটার পর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে থেমে যায়, আর পেছনের কাঠামোগত সমস্যা—তথ্য–প্রবাহে বাধা, সমন্বয়ের সংকট, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব—এসব নিয়ে জোরালোভাবে কথা না বলে, তাহলে সমস্যা বারবার ফিরে আসবে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচনী সহিংসতা প্রতিরোধ, নাগরিক নিরাপত্তা—এসব কেবল পুলিশের একক দায়িত্ব নয়; এগুলো রাষ্ট্রের সামগ্রিক ক্ষমতার পরিমাপ। আর সেই ক্ষমতার গায়ে আজ যে ফাটল দেখা যাচ্ছে, তার নাম—জেলা প্রশাসন ও পুলিশের তথ্য–সমন্বয়ের জটিলতা।
আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে এখন প্রশ্নটা তাই আরও তীক্ষ্ণ—আমরা কি চাই, প্রতিটি জেলা আইন–শৃঙ্খলা কমিটি হাতে রিয়েল–টাইম তথ্য নিয়ে কাজ করুক, নাকি চাই তারা দুই সপ্তাহ আগের কাগজে চোখ রেখে আগামীকালের নিরাপত্তা পরিকল্পনা আঁকুক? উত্তরটা সহজ; কিন্তু বাস্তবে সে উত্তর বাস্তবায়ন করতে হলে ক্ষমতার এই নীরব যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, সমন্বয়কে দুর্বলতা নয়, বরং শক্তি হিসেবে স্বীকার করতে হবে। নাগরিকের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা—এই তিনটির স্বার্থেই এখন সময়, বিপি ফরম–১৬–এর মধ্যে আটকে থাকা তথ্যকে আবারও জেলা প্রশাসনের টেবিলে ফিরিয়ে আনার।


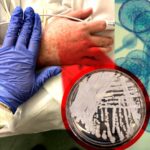



আপনার মতামত জানানঃ