 ঢাকা সেনানিবাসে একটি ভবনকে সাময়িকভাবে কারাগার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ‘MES বিল্ডিং নং-৫৪’, বাসার রোড সংলগ্ন উত্তরের অংশে অবস্থিত, এভাবে ঘোষণা করা হয় সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এটি হবে “সাময়িক কারাগার” এবং সরকারি স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে আইন অনুযায়ী।
ঢাকা সেনানিবাসে একটি ভবনকে সাময়িকভাবে কারাগার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ‘MES বিল্ডিং নং-৫৪’, বাসার রোড সংলগ্ন উত্তরের অংশে অবস্থিত, এভাবে ঘোষণা করা হয় সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এটি হবে “সাময়িক কারাগার” এবং সরকারি স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে আইন অনুযায়ী।
নামমাত্র তথ্য অনুযায়ী কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই — কাদের রাখা হবে এবং কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার হবে, তা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়নি। তবে এই পদক্ষেপ কেন এবং কি প্রেক্ষাপটে করা হলো, তা নিয়ে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিশ্লেষণ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।
এই সিদ্ধান্তের সময় প্রেক্ষাপট নজর এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। গত কয়েকদিনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) থেকে গ্রেপ্তার ও তলব থাকা সেনা কর্মকর্তাদের নামে অভিযোগ ওঠেছে—গণঅভ্যুত্থান, গুম, নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী কাজের মাধ্যমে। সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে জানিয়েছে তারা ১৫ জন অফিসারকে সাময়িকভাবে হেফাজতে নিয়েছে। এই সময়ে একটি সেনানিবাসের ভবনকে চমকে দিয়ে কারাগার হিসেবে ঘোষণা করা হয়—অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ এলাকা।
এই সিদ্ধান্ত থেকে যে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য—“রাষ্ট্র কি ইতিমধ্যে সেনাবাহিনী কর্তৃত্বে চলে?”—তার পেছনে কিছু যুক্তি ও সন্দেহ রয়েছে। প্রথমত, সাধারণভাবে কারাগার স্থাপন ও পরিচালনা করলে তা হয় নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং সুশাসিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু যখন সেই কাজ হয় সেনানিবাসে, যেখানে সাধারণ নাগরিকদের প্রবেশ-নিষিদ্ধ এলাকা, সেখানে স্বাভাবিক বিচারপ্রক্রিয়া ও নজরদারি কম থাকে।
দ্বিতীয়ত, এমন পদক্ষেপ একটি সংকেত পাঠায় — আইন-শৃঙ্খলা কার্যক্রম শুধুই পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনের সীমাবদ্ধতায় নেই, বরং সেনাবাহিনীর অবাধ কার্যক্রম অনুমোদন পাওয়া যেতে পারে। ফলে বিচারপ্রক্রিয়া ও নাগরিক অধিকার প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।
তৃতীয়ত, এটা একটি “ক্ষমতার মুষ্টিবদ্ধকরণ” ইঙ্গিত দিতে পারে — নিরাপত্তা, কারাগার, গ্রেপ্তার ও হেফাজতের ক্ষমতা একক কেন্দ্রীকরণ। সাধারণভাবে সিভিল প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে ভুলিয়ে দেওয়া একটি ফলাফল হতে পারে।
তাছাড়া বিচার ও আইনের মৌলিক নীতি হলো—‘গ্রেপ্তার করার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করা’ এবং প্রসিকিউশন ও প্রতিরক্ষা যুক্তি বিকাশের সুযোগ দেওয়া। বিচারপ্রকৃতি নির্বিশেষে, অভিযুক্ত কারাগার কোথায় রাখা হবে, তা আদালতের নির্দেশ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হওয়া উচিত।
আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রজ্ঞাপন যে ধারা উদ্ধৃত করেছে—ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ধারা ৫৪১(১) এবং প্রিজন অ্যাক্ট, ১৮৯৪-এর ধারা ৩(বি) —সেগুলো “সাব-কারাগার বা অস্থায়ী কারাগার স্থাপন” করার ক্ষমতা প্রতিপাদন করে। তাই আইনগতভাবে এমন ঘোষণা করা যায়। তবে আইন এবং প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধান থাকতে পারে। (একটি আইন থাকলেই সব সুসংগঠিত ও স্বচ্ছভাবে প্রয়োগ হবে, তা ও নয়।)
এই সিদ্ধান্তের ফলে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্বেগ তৈরি হবে, সেটিও অবহেলা করতে হবে না। বিরোধী রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার সংগঠন ও সাধারণ জনগণ প্রশ্ন তুলবেন—এ কারাগারটি কি রাজনৈতিক বন্দীদের নিরাপদ রাখা হবে? কি ভাবে নজরদারি হবে? কারা এবং কী প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব নেবে? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
একই সঙ্গে, এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যদি জনসচেতনতা ও স্বচ্ছতা কার্যকরভাবে না দেখায়, তাহলে জনগণের বিশ্বাস কমে যাবে। বিচার ও প্রশাসনের স্বাধিকার ও সীমাবদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে হবে।
এইভাবে, সেনানিবাসের ভবনকে কারাগার ঘোষণা করা যে একমাত্র ‘প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ’ ছিল, তা বলা কঠিন। কারণ এমন কাজের পেছনে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক কারণ, আইনগত স্পষ্টতা ও জনসম্বেদ থাকা জরুরি—না হলে সেটি ‘দেশটা কি সেনাবাহিনী চালাচ্ছে?’—এই সন্দেহকে আরও গভীর করবে।
অবশ্য, সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে যদি সরকার ভয় করেছে আইনশৃঙ্খলা বেহাল হবে বা কারাগারের স্থান সংকুল হবে—সেক্ষেত্রে বিকল্প লক্ষ্য থাকতে পারে। তবে সেটা নিয়েও খোলামেলা ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত।
সেনানিবাস ভবনকে অস্থায়ী কারাগার ঘোষণা করা শুধু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি একটি রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ইঙ্গিত বহন করে—যে দেশে আইনই সর্বোচ্চ—but সেই আইন প্রয়োগ হয় সেই দেশের জনগণের বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে। এই ধরনের সিদ্ধান্তের পরে সেনাবাহিনী কি নিয়মিত আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে? প্রশ্নটা এখন আর অবধারিত, এবং সমাজ ও সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব হবে সেটা প্রশ্ন করতে।



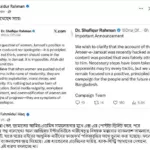


আপনার মতামত জানানঃ