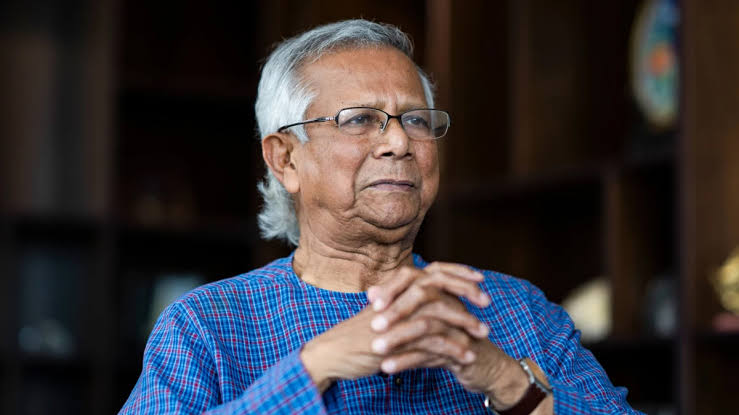
বাংলাদেশে এখন এমন এক সময় চলছে, যখন সরকারকে শুধু সরকার বলে চেনা যাচ্ছে না। রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রশাসনের আড়ালে আরেকটি অদৃশ্য ‘সরকার’ সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে, যার সিদ্ধান্ত এবং কর্মকাণ্ড মাঝে মাঝেই মূল সরকারের নীতিমালার বিপরীতে দাঁড়িয়ে যায়। এই দ্বৈত বাস্তবতা আজ রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে এক ধরনের অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিয়েছে। আর এই ‘ভেতরের সরকার’ এখন শুধু নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণেই নয়, বরং গণতান্ত্রিক সংস্কার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং জনস্বার্থেও বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে।
এমন একটি গভীর পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের কথায়। তিনি বলেছিলেন, সরকার যাদের আমরা দেখি, তাদের বাইরেও আরেকটি সরকার রয়েছে। এই কথাটি শুনতে যতটা সাংঘাতিক মনে হয়, বাস্তবতা তার চেয়েও বেশি। এক বছর আগে গণ–অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে পরিবর্তনের দাবি উঠেছিল, তা এখন তলিয়ে যাচ্ছে একটি অস্পষ্ট, দ্বৈত প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে। শ্বেতপত্র কমিটির কাজই তার একটি বড় উদাহরণ। কমিটি কাজ করলেও তা বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি, কারণ ‘উপদেষ্টা পরিষদের’ ভেতরেই এক ধরনের মতপার্থক্য ও গোপন প্রতিরোধ কাজ করছে।
এই ‘ভেতরের সরকার’-এর সবচেয়ে দৃশ্যমান রূপ আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক পোশাকসংক্রান্ত পরিপত্রে দেখতে পাই। নারী কর্মীদের পোশাক কী হবে, কোনটি ‘শালীন’, আর কোনটি ‘অগ্রহণযোগ্য’—এমন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছিল একেবারে আদেশের ভাষায়, শাস্তির হুমকিসহ। অথচ, ব্যাংকের গভর্নর নিজেই ছিলেন দেশের বাইরে এবং এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে সেটি প্রত্যাহার করেন। প্রশ্ন হলো, গভর্নর যখন জানেন না, তখন কে এই নির্দেশ দিল? কে এই ‘অভ্যন্তরীণ সরকার’, যিনি-বা যারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চায় গভর্নরের অনুপস্থিতিতে?
এই ঘটনাটি নিছক পোশাকবিধির বিতর্ক নয়। এটি আসলে ক্ষমতার গোপন উৎস কোথায়, সেই প্রশ্ন তোলে। এমন সিদ্ধান্ত কোনো একজন বা দুইজন কর্মকর্তা নিজের ইচ্ছায় দিতে পারেন না—এই ধরনের সিদ্ধান্ত কোনো গোপন কেন্দ্র থেকে আসে। এমনই আরেকটি ঘটনা দেখা গেল যখন পাঠ্যবই পর্যালোচনার জন্য গঠিত কমিটির বিরুদ্ধে ধর্মীয় উগ্রতাবাদী গোষ্ঠীর আপত্তিতে সরকার পিছু হটে। অর্থাৎ, একটি বৈধ, প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপকে কিছু প্রভাবশালী ‘মহল’-এর চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে হয়। এমনকি পাঠ্যবই থেকে ‘আদিবাসী’ শব্দ পর্যন্ত বাদ দিয়ে দিতে হয়, যাতে উগ্র জাতীয়তাবাদের মুখ রক্ষা করা যায়।
একই ধরনের দৃশ্যপট আমরা দেখি নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের ক্ষেত্রেও। একটি মহল শুধু সুপারিশের বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা গোটা কমিশন বাতিলের দাবি জানিয়েছে। ফলাফল? সেই কমিশনের কার্যক্রম আর এগোয়নি, প্রতিবেদন ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে। সরকারের পক্ষ থেকে কেউ আর কথা বলছে না, যেন এটি ঘটেইনি। এই সব ঘটনাই ইঙ্গিত দেয়, সরকারের ভেতরে কেউ বা কারা এমনভাবে কাজ করছে, যা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক নীতি ও সংস্কারকে স্তব্ধ করে দেয়।
এদিকে যারা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, সেই শ্রমজীবী মানুষেরা আজ উপেক্ষিত। চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানে দিনমজুর, রিকশাচালক, ভ্যানচালক, গার্মেন্টস শ্রমিক ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রথম সারিতে ছিলেন। তাঁদের রক্তে অর্জিত এই পরিবর্তনের পরে সরকারের উচিত ছিল শ্রমজীবীদের কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বহু কারখানা বন্ধ হয়েছে, হাজার হাজার মানুষ কাজ হারিয়েছে, খাদ্য ও নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে, এবং গত এক বছরে ২৬ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে।
এমন সংকটময় সময়ে সরকার যা করেছে, তা হলো—১৫ লাখ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য নতুন বেতন কাঠামো গঠনের ঘোষণা। মূল্যস্ফীতির দোহাই দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও বাকি কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রা যে আরও কঠিন হয়ে উঠবে, সেটা সরকার কি ভেবেছে? এই বেতন কমিশনের সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন জনপ্রশাসনের ভেতরকার সুবিধাভোগীদের আরও সুবিধা দেয়, অন্যদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে সংকট বাড়ায়।
বিশ্বব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন যেমন প্রশ্ন তুলেছেন, এখনকার এই অর্থনৈতিক বাস্তবতায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর কী যৌক্তিকতা আছে? আমাদেরও সেই প্রশ্ন। অতীতে রাজনৈতিক সরকারগুলো দলীয় স্বার্থে প্রণোদনা দিয়েছে, সেটার একটা ব্যাখ্যা ছিল। কিন্তু বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার তো দলীয় নয়, তাহলে তেল মাথায় তেল দেওয়ার রাজনীতি তারা করছে কেন?
সব মিলিয়ে চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থান যে মূলত বৈষম্য আর অবিচারের বিরুদ্ধে ছিল, সেই আহ্বানের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধা আছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা খুবই স্বাভাবিক। কারণ এখনো সেই বৈষম্য টিকে আছে, বরং তা নতুন রূপে, নতুন কাঠামোয় হাজির হচ্ছে। সরকারের ভেতরে থাকা এই গোপন ‘সরকার’ কেবল সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণই করে না, বরং পুরো রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সম্ভাবনাকে গিলে ফেলার ঝুঁকি তৈরি করছে।
এই অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক কাঠামো, যেখানে ‘সরকারের ভেতরে সরকার’ নয়, বরং জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী একটি কার্যকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকবে। গণ–অভ্যুত্থানের আত্মত্যাগ যেন একটি অদৃশ্য প্রশাসনিক ছায়া সরকারের ছায়ায় হারিয়ে না যায়, সেটাই এখন জাতির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।






আপনার মতামত জানানঃ