
চীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র—এটা শুধু একটি বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং বৈশ্বিক রাজনীতির কৌশলগত পরিবর্তনের স্পষ্ট প্রমাণ। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশনের (USITC) প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, ২০২৫ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র চীন থেকে মাত্র ৫৫৬ মিলিয়ন ডলারের পোশাক আমদানি করেছে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। অথচ এপ্রিল মাসেই এই পরিমাণ ছিল ৭৯৬ মিলিয়ন ডলার। চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্রমাগত অবনতির প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে কঠোর বাণিজ্যনীতির কারণে এই পতন ঘটেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
২০২৫ সালের এপ্রিলে ট্রাম্প প্রশাসন চীনা পোশাকের ওপর সর্বোচ্চ ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করে, যার ফলে মার্কিন খুচরা বিক্রেতারা নতুন উৎস খোঁজে নিতে বাধ্য হন। তারা এখন ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ভারত ও মেক্সিকোর মতো দেশগুলোর দিকে ঝুঁকছে। এই পরিস্থিতিকে অর্থনীতিবিদরা বলছেন ‘একটা কৌশলগত বাস্তবতা’, যা রাজনীতি ও অর্থনীতি—দুই কৌশলেই যুক্তরাষ্ট্রকে চীন থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। ইউনিভার্সিটি অব ডেলাওয়ারের অধ্যাপক শেং লু একে স্বাভাবিক বাজারচক্র নয়, বরং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
বছরের শুরুতে, জানুয়ারিতে চীন থেকে আমদানি ছিল ১.৬৯ বিলিয়ন ডলার—যা আগের বছরের জানুয়ারির তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি। এতে বোঝা যায়, অনেক প্রতিষ্ঠান তখনই শুল্ক বাড়ার আশঙ্কায় আগেভাগে পণ্য আমদানি করে রেখেছিল। কিন্তু যখন কঠোর শুল্ক কার্যকর হলো, তখন তারা বিকল্প দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দিল। এই কৌশলগত পরিবর্তনেই নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য।
বিশ্ববাজারের এই পালাবদলে সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। আন্তর্জাতিক অডিট ফার্ম কিউআইএমএ (QIMA) তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানায়, ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে চীনে মার্কিন সোর্সিং কমেছে ২৫ শতাংশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বেড়েছে ২৯ শতাংশ। এই প্রবণতা শুধু পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি বাস্তব অর্ডার ও সরবরাহ ব্যবস্থায়ও প্রতিফলিত হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত এতে সরাসরি লাভবান হওয়ার অবস্থানে রয়েছে।
বাংলাদেশের মতো শ্রমনির্ভর উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য এটি এক সুবর্ণ সুযোগ। যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহৎ বাজারে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া মানে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি এবং বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বাড়ার সম্ভাবনা। একইসাথে এই প্রবণতা শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করতে পারে। তবে এর জন্য দরকার হবে সরকারি নীতিগত সহায়তা, অবকাঠামো উন্নয়ন, বন্দর ব্যবস্থার দক্ষতা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা।
মেক্সিকোও এই পালাবদলে জায়গা করে নিয়েছে। মে মাসে দেশটি ২৫৯ মিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি। তবে মেক্সিকোর ভৌগোলিক অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি হওয়ায় তাদের কিছুটা স্বতঃসিদ্ধ সুবিধা থাকলেও, দক্ষ শ্রমশক্তি ও খরচ সাশ্রয়ী উৎপাদনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম অনেকটা এগিয়ে রয়েছে।
এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ যদি দূরদর্শিতা ও দক্ষতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে চীন থেকে সরে যাওয়া মার্কিন বাজারের এক বড় অংশই আমরা নিজেদের পক্ষে আনতে পারি। এখন সময় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার। শিল্প উদ্যোক্তাদের দক্ষতা, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, নতুন কারখানায় বিনিয়োগ এবং বৈশ্বিক মান বজায় রেখে উৎপাদন করাই হতে পারে আমাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের চাবিকাঠি।
বিশ্ব রাজনীতির টানাপোড়েনে অনেক সময় এক দেশের পতনই হয় আরেক দেশের সম্ভাবনার শুরু। চীনের জায়গা ফাঁকা হওয়ায় বাংলাদেশের সামনে এখন যে দরজা খুলেছে, সেটি কেবল রপ্তানির নয়, বরং অর্থনৈতিক কৌশলের এক নতুন পর্ব। প্রশ্ন হলো—আমরা কি প্রস্তুত এই সুযোগটা কাজে লাগাতে? সময় কিন্তু খুব বেশি নেই।



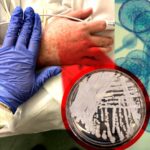


আপনার মতামত জানানঃ