
আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক শাখার পেছনে একাধিক প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর অবদান রয়েছে। তেমনই একজন ছিলেন ডাচ বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনস। তিনি শুধু আলোর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেই থামেননি, বরং তাঁর উন্নত টেলিস্কোপ ব্যবহার করে দূরের গ্রহ-নক্ষত্রের রহস্য উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।
১৬২৯ সাল। নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন হাইগেনস। ছোটবেলা থেকেই গণিত ও বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর। এটা অবশ্য পরিবারের জন্যই হয়েছিল। প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াশোনা আর পারিবারিক পরিচয়ের সুবাদে দার্শনিক রেনে দেকার্তের মতো মানুষদের সংস্পর্শে আসতে পারেন খুব সহজেই। সব মিলিয়ে জ্ঞানচর্চার একটা দুর্দান্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠেন তিনি। ইউনিভার্সিটি অব লেইডেন ও পরে ব্রেডার কলেজে আইন ও গণিত নিয়ে পড়েন।
মেকানিক্স বা বলবিদ্যায়ও হাইগেনসের অবদান কম নয়। তিনি দেখান, বস্তুর সংঘর্ষে পুরো সিস্টেমের ভরবেগ (Momentum) কমেও না, বাড়েও না। এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। এই ধারণাই পরে বলবিদ্যার ভিত্তি গঠনে সাহায্য করে।
তৎকালীন সময়ে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে রয়্যাল সোসাইটি। ১৬৬৩ সালে হাইগেনস এই নতুন গঠিত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হন। সেখানে তিনি পরিচিত হন সমসাময়িক আরেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের সঙ্গে। যদিও বহু বিষয়ে হাইগেন্স ও নিউটনের মতের বিরোধ ছিল, কিন্তু একে অপরের কাজের প্রতি সম্মান করতেন।
প্রথম দিকে হাইগেনস গণিত বিষয়েই লেখালেখি করতেন। তবে ১৬৫৪ সাল নাগাদ তিনি টেলিস্কোপের দিকে মনোযোগ দেন। তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে মিলে লেন্স পালিশের উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এর সাহায্যে আরও পরিষ্কার ছবি দেখা যেত। এই উন্নত টেলিস্কোপ তিনি শনি গ্রহের দিকে তাক করেন। তখন পর্যন্ত এই গ্রহকে কেউই স্পষ্টভাবে দেখতে পারেননি। গ্যালিলিও নিজেও টেলিস্কোপে শনি গ্রহ দেখে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। গ্যালিলিওর কাছে মনে হয়েছিল, শনি গ্রহের পাশে কী যেন কান বা দুলের মতো ঝুলে আছে। হাইগেনস সেই রহস্যভেদ করলেন। তিনি জানালেন, গ্যালিলিওর দেখা কান বা দুল হলো শনির রিং। প্রথমে তাঁর এই আবিষ্কার অনেকেই বিশ্বাস করতে চাননি। কিন্তু পরে আরও পর্যবেক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেছে, হাইগেনস ঠিকই বলেছেন।
শুধু তা-ই নয়, তিনি ১৬৫৫ সালে শনির সবচেয়ে বড় চাঁদ আবিষ্কার করেন। পরে ১৮৪৭ সালে আরেক জ্যোতির্বিদ জন হার্শেল এর নাম রাখেন টাইটান। যখন ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা এই চাঁদে একটি মহাকাশযান পাঠায়, তখন তার নাম রাখা হয় হাইগেনস। শনির এই উপগ্রহটিই বর্তমানে আমাদের সৌরজগতে প্রাণ খোঁজার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় স্থান। হাইগেন্স নিজেও ভিনগ্রহী প্রাণীদের নিয়ে ভাবতেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত একটি লেখা থেকে জানা যায়, তিনি কতটা যুক্তিসম্মতভাবে পৃথিবীর বাইরেও প্রাণ থাকার সম্ভাবনা দেখিয়েছেন।
তবে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ হলো আলোর প্রকৃতি নিয়ে। তিনি বললেন, আলো এক ধরনের তরঙ্গ, যা ইথার নামে এক সূক্ষ্ম মাধ্যমে চলাফেরা করে। সে সময়ের বিজ্ঞানীরা এই ইথারকেই আলোর বাহক হিসেবে ভাবতেন। পরে অবশ্য প্রমাণিত হয়, এমন কোনো ইথার আসলে নেই। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে হাইগেনস আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের নিয়ম হিসাব করেন। যদিও তাঁর হিসাবগুলো সঠিক ছিল, কিন্তু সেই ইথার বলে আসলে কিছু নেই। তাঁর এই তত্ত্ব আইজ্যাক নিউটন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নিউটন প্রস্তাব করেছিলেন, আলো ছোট ছোট কণার সমষ্টি যা দ্রুত গতিতে চলে। বর্তমানে আমরা জানি, আলো একই সঙ্গে তরঙ্গ ও কণাতত্ত্ব মেনে চলে।
মেকানিক্স বা বলবিদ্যায়ও হাইগেনসের অবদান কম নয়। তিনি দেখান, বস্তুর সংঘর্ষে পুরো সিস্টেমের ভরবেগ (Momentum) কমেও না, বাড়েও না। এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। এই ধারণাই পরে বলবিদ্যার ভিত্তি গঠনে সাহায্য করে।
তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হলো দোলনঘড়ি বা পেন্ডুলাম ক্লক। সেই সময়ের ঘড়িগুলোতে প্রায়ই সময় ভুল দেখাত। হাইগেনস তখন একটি দোলনঘড়ি তৈরি করেন। সেই ঘড়িতে সময়ের ভুল ছিল দিনে এক মিনিটের কম। পরে সেটি আরও উন্নত করে দিনে মাত্র ১০ সেকেন্ডের ভুলে নামিয়ে আনেন। গ্যালিলিও তাঁর জীবনের শেষদিকে এমন ঘড়ির নকশা করেছিলেন, কিন্তু তা তিনি তৈরি করে যেতে পারেননি। হাইগেনস সেটি বাস্তবে তৈরি করতে পেরেছিলেন। তিনি হাতঘড়ির ভেতরের নকশাতেও পরিবর্তন করেছিলেন। ফলে সেগুলো আরও ছোট, হালকা ও অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য ওঠে।
প্রথম দিকে হাইগেনস গণিত বিষয়েই লেখালেখি করতেন। তবে ১৬৫৪ সাল নাগাদ তিনি টেলিস্কোপের দিকে মনোযোগ দেন। তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে মিলে লেন্স পালিশের উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এর সাহায্যে আরও পরিষ্কার ছবি দেখা যেত।
হাইগেনস গানপাউডার চালিত ইঞ্জিনের ডিজাইনও করেছিলেন। যদিও তিনি তা কখনো বাস্তবে তৈরি করেননি। এছাড়া একাধিক লেন্স ব্যবহার করে টেলিস্কোপের জন্য প্রথম যৌগিক আইপিস তৈরি করেন। এটি বহু বছর ধরে বড় টেলিস্কোপে ব্যবহৃত হয়েছে। ১২৩ ফুট, ১৮০ ফুট এবং ২১০ ফুট ফোকাল দৈর্ঘ্যের তিনটি বিশাল টেলিস্কোপ তৈরি করে তা রয়্যাল সোসাইটিকে উপহার দিয়েছিলেন হাইগেনস।
তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব যেমন বিস্ময় জাগায়, তেমনি বিস্ময় জাগায় তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি। আধুনিক বিজ্ঞানের যে ভিত্তি আজ আমরা দেখি, তাতে হাইগেনসের অবদান নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। তিনি যেন এক হাতে অতীতকে দেখেছেন টেলিস্কোপে চোখ রেখে, আর অন্য হাতে চিন্তার বীজ বপন করেছেন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে।



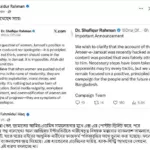


আপনার মতামত জানানঃ